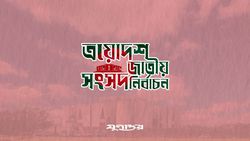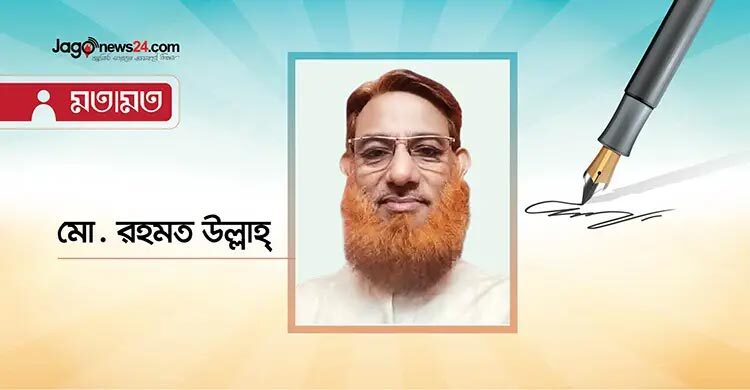আইএমএফের ঋণে বেকারত্ব কেন বাড়ে
ইউরোপিয়ান জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমিতে প্রকাশিত গ্রিক অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্লেটসস ও আন্দ্রেয়াস সিন্টোসের লেখা ‘দ্য ইফেক্টস অব আইএমএফ কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম অন দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট’ শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায় ‘আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলোয় বেকারত্ব বেড়েছে, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে এবং শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা গভীরতর হয়েছে’ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১-২০১৪ মধ্যবর্তী সময়ে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলোর ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত এ প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং তথ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সেই গবেষণা মতে, আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো বাজেট ঘাটতি কমানো, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ, শ্রমবাজার উদারীকরণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সেখানকার লাখ লাখ মানুষকে বেকারত্বের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থাও দুর্বল থেকে ক্রমেই অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়েছে। লক্ষ করা যাচ্ছে যে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মোকাবিলার জন্য সদস্যদেশসমূহকে ঋণ দিয়ে ইতিবাচকভাবে সাহায্য করা যেখানে আইএমএফের গঠনতান্ত্রিক দায়িত্ব, সেখানে ওই দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ঋণগ্রহীতা দেশের সঙ্গে অন্যায় ও অমর্যাদাকর খবরদারিমূলক আচরণ করে যাচ্ছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশের দাদনদার এবং কোনো কোনো এনজিও ঋণের অনেক মিল রয়েছে। এ দেশের অসহায় দরিদ্র কৃষক বা বর্গাচাষি যেমন নিরুপায় হয়ে ঋণের জন্য দাদনদার বা এনজিওর শরণাপন্ন হন, আর সেই সুযোগে দাদনদার ও এনজিও তাঁদের ওপর উচ্চসুদ ও অন্যান্য অন্যায্য শর্ত চাপিয়ে দেয়, আইএমএফের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা সে রকমই। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ রপ্তানি ঘাটতিতে থাকা দেশগুলো যখন বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে অত্যাবশ্যকীয় আমদানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে অপারগ হয়ে ওঠে, তখনই তারা নিরুপায় হয়ে আইএমএফের শরণাপন্ন হয়। আর এই সুযোগে এ প্রতিষ্ঠানটিও ঋণপ্রার্থী দেশের ওপর এমন সব শর্ত চাপিয়ে দেয়, যেগুলো পূরণ করে ঋণ নেওয়ার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের ঋণচাহিদা পূরণ হয় বটে, কিন্তু বেকারত্ব, ছাঁটাই বা কর্মচ্যুতি ও নানা অমানবিক অনুষঙ্গ দেশগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। আর সে চেপে ধরা পরিস্থিতিরই বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।
বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কৃষিপ্রধান এলাকাগুলোতে এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটে থাক। ফসল ওঠার এক-দুই মাস আগে অভাবী কৃষক তাঁর মাঠের ফসল অতি কম মূল্যে দাদনদারের কাছে অগ্রিম বিক্রি করে দেন অথবা এই শর্তে অতি উচ্চ সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। শর্ত থাকে যে ফসল ওঠার পর ওই দাদনদারের কাছেই তা বিক্রি করতে হবে। সমুদ্র বা নদীর ইলিশ শিকারি জেলে কিংবা আখচাষিদের ক্ষেত্রেও ঘটনাগুলো মোটামুটি একই রকম। আর সেসব ঘটনারই মোটামুটি ধাঁচের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে আইএমএফও। পার্থক্য শুধু এটুকু যে দাদনদার উচ্চহারে সুদ কষছে আর আইএমএফ উচ্চমাত্রার কঠিন সব শর্ত আরোপ করছে। কিন্তু ফলাফল সেই একই রকম। দাদনদারের শর্তে অসহায় কৃষক দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র ও অধিকতর নিঃস্ব হচ্ছে এবং তাঁর কষ্ট ও ভোগান্তি উভয় মাত্রা আরও বাড়ছে। অন্যদিকে আইএমএফের ঋণে বাড়ছে ছাঁটাই, বেকারত্ব, সামাজিক অনিরাপত্তা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের ভোগান্তি। ফলে পশ্চিমা পুঁজির প্রতিনিধি আইএমএফ ও বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পুঁজির প্রতিনিধি দাদনদার ও মহাজন বস্তুত সেই একই আদর্শেরই প্রতিনিধি।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আইএমএফের এরূপ নীরব পীড়ন ও শোষণ থেকে বাঁচা যাবে কেমন করে? তাৎক্ষণিক জবাব হচ্ছে, উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হবে, যাতে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আইএমএফের কাছে ঘন ঘন হাত পাততে না হয়। আর এর টেকসই সমাধান হচ্ছে, উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়ানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের ব্যয় খাতকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এর পরিচালন ব্যয়, বিশেষত জনপ্রশাসনের বিলাসী ব্যয় কমিয়ে উন্নয়ন বা মূলধন ব্যয় বাড়াতে হবে। কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ে আইএমএফের পক্ষ থেকে পরামর্শ, পথ্য বা তাগাদা বলতে গেলে প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ, আইএমএফের পরামর্শদাতারাও জানেন, ঋণগ্রহীতা দেশের জনগণের উপকারের নামে আইএমএফের কাছ থেকে দাদন গ্রহণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মর্মের সুপারিশটি জনপ্রশাসনের ওই চতুর সদস্যরাই চূড়ান্ত করে থাকেন। ফলে আইএমএফের নিজের স্বার্থেই তাঁরা কারখানা থেকে লোকবল ছাঁটাই ও কল্যাণমূলক ব্যয় কমানোর কথা বললেও জনপ্রশাসনের ব্যয় কমানোর সুপারিশ তাঁরা কখনোই করে থাকে না। আলোচ্য গবেষণার ফলাফল থেকে বস্তুত সেটাই বেরিয়ে এসেছে।
আইএমএফ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও ভর্তুকি প্রত্যাহারের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে সে ভর্তুকি তারা মূলত কৃষি ও নিম্নবিত্তের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত খাতগুলোতে কমানোর জন্যই অধিক চাপ দেয়। বিত্তবান উদ্যোক্তাদের জন্য যেসব নগদ প্রণোদনা ও অন্যান্য ভর্তুকি চালু আছে, সেগুলো কমানোর কথা বললেও সেটি তারা বলে খুবই মৃদু কণ্ঠে। কারণ, এসব খাতে ভর্তুকি বহাল থাকলে পশ্চিমের ক্রেতারা তা থেকে লাভবান হতে পারেন। একইভাবে আইএমএফ জ্বালানি তেলের ওপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারের কথা বলে। আর এ ক্ষেত্রে ডিজেলের চাহিদা সর্বাধিক বিধায় এর ওপরই খড়্গটি সবচেয়ে আগে কার্যকর করা হয়—বিত্তবানের ব্যবহার্য পেট্রল ও অকটেন সেখানে থাকে অনেকটাই পরের সারিতে। কিন্তু একবারও ভাবা হয় না যে এই জিজেলের ভোক্তা আসলে কৃষক ও অন্যান্য খাতের নিম্ন আয়ের মানুষ। রাষ্ট্রের লোকসান কমাতে আইএমএফ জ্বালানি তেলের ওপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারের কথা বললেও জ্বালানি (গ্যাস ও অন্যান্য) অনুসন্ধানের জন্য ঘুণাক্ষরেও তাগাদা দেয় না। কারণ, বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর দেশগুলোর নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তাব্যবস্থা না গড়ে উঠলে তাতে পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণাধীন মধ্যপ্রাচ্যীয় জ্বালানিব্যবস্থার চাবিকাঠি পশ্চিমেই রাখা যাবে বৈকি।
আইএমএফ তার ঋণের বিপরীতে সুদ নিলেও এটি কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়। ফলে সদস্যদের চাঁদা, অনুদান ও অন্যবিধ সহযোগিতায় গড়ে ওঠা আইএমএফের তহবিল ব্যবহার অন্য সদস্যরাষ্ট্রের ওপর খবরদারি করার গঠনতান্ত্রিক কোনো অধিকার সেটার একেবারেই নেই। তা সত্ত্বেও আইএমএফ যা করছে, তা আসলে ঋণগ্রহীতা সদস্যদেশগুলোর জন্য পরিপূর্ণভাবে অনৈতিক ও চরম অমর্যাদাকর। কিন্তু এরপরও ঋণগ্রহীতা সরকারগুলো এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করে না। এর মূল কারণ হলো, এ সরকারগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্বের নাম করে ক্ষমতায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এরা কখনোই সাধারণ জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। ভেতরে-ভেতরে এরা (রাজনীতিক ও আমলা উভয়ই) বরং আইএমএফের শর্ত মানতে পারলেই অধিক খুশি। কারণ, এতে একদিকে তাদের শ্রেণিস্বার্থ যেমন রক্ষা পায়, অন্যদিকে তেমনি এ সম্পর্কের ফাঁকফোকর গলিয়ে নানা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা জোটানোও সহজ হয়। তদুপরি আইএমএফের যারা নেপথ্যনিয়ন্তা, আইএমএফের পরামর্শ মেনে চলার সুবাদে ক্ষমতায় থাকার জন্য সেই নিয়ন্তাদের আশীর্বাদ পাওয়ার বিষয়টিও অনেকটা সহজ হয়ে আসে।