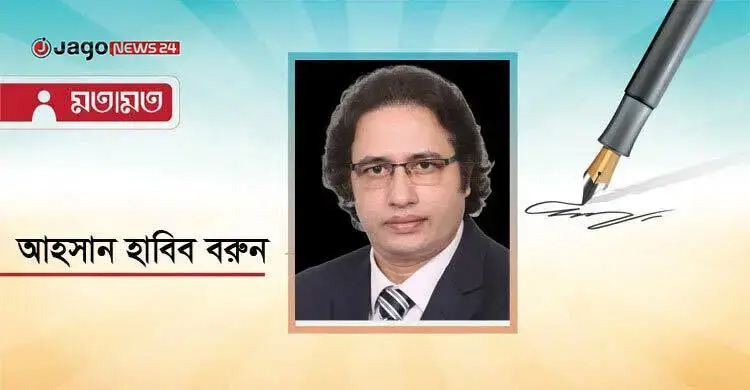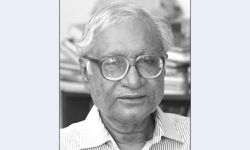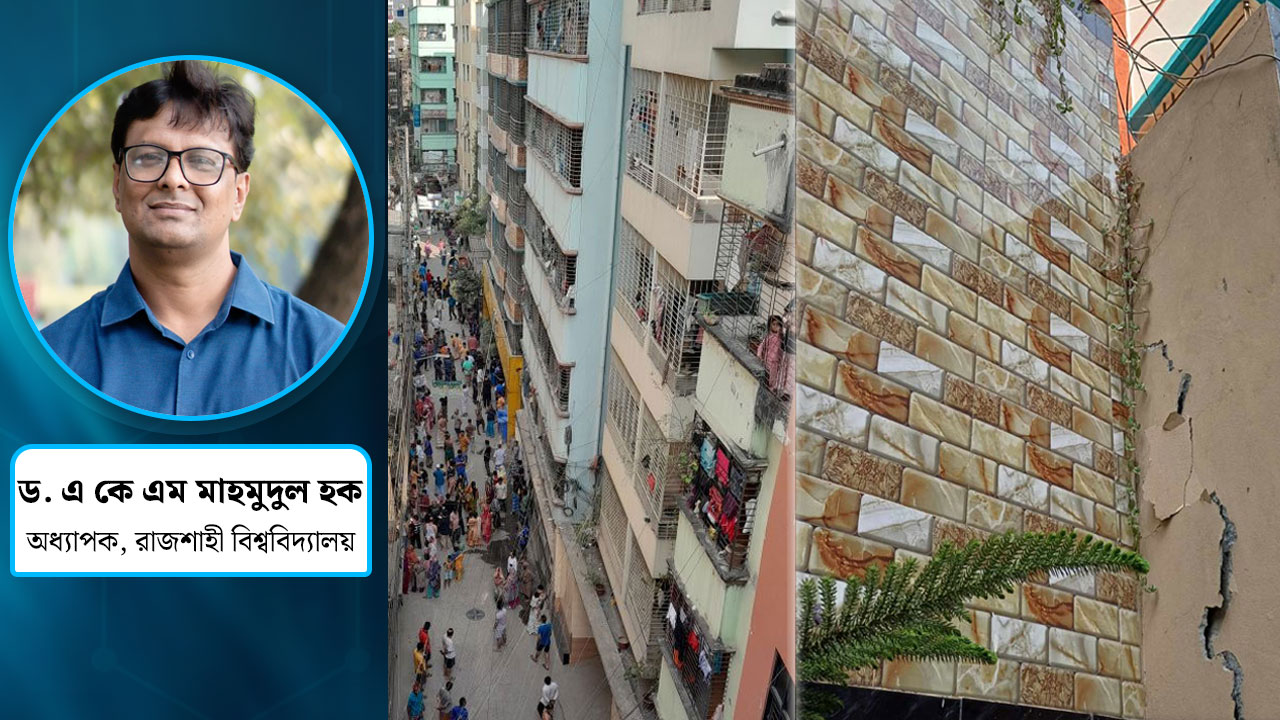
ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল কোনগুলো, তাদের নিরাপত্তা প্রস্তুতি কেমন?
ভূমিকম্প কী?
ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের হঠাৎ কেঁপে ওঠা বা ঝাঁকুনি। আমাদের পৃথিবী কয়েকটি বিশাল টুকরা বা টেকটোনিক প্লেট দিয়ে গঠিত, যা সবসময় খুব ধীরে ধীরে নড়ে। এই প্লেটগুলোর সীমানায় যখন দুটি প্লেট একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় বা ঘষা লাগে, তখন সেখানে প্রচণ্ড শক্তি জমা হতে থাকে—অনেকটা রাবার ব্যান্ড টানার মতো।
চাপ অত্যধিক বেড়ে গেলে প্লেটগুলো হঠাৎ করে সরে যায়, আর তখন জমে থাকা সেই শক্তি হঠাৎ মুক্তি পায়। মুক্ত শক্তি তরঙ্গ আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমরা ভূপৃষ্ঠে সেই কম্পন অনুভব করি। যেখান থেকে কম্পন শুরু হয়, তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলা হয়। এই প্রাকৃতিক ঘটনাই হলো ভূমিকম্প, যা অল্প সময়েই প্রচুর ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।
ভূমিকম্পের কারণ
আসলে ভূমিকম্পকে একটি ট্র্যাজেডি বলা যেতে পারে। ভূমিকম্পের মতো বিশাল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মানুষ সরাসরি দায়ী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বড় ও ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের মূল কারণ হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যা কোটি কোটি বছর ধরে চলমান। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ভূতাত্ত্বিক এবং পৃথিবীর গভীর তাপ ও চাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা মানুষের কোনো কার্যকলাপ—বাড়ি নির্মাণ বা শিল্প উৎপাদন—দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে, ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পকে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবেই গণ্য করা হয়।
তবে একথা মানতে হবে যে মানুষের কিছু নির্দিষ্ট কার্যকলাপ খুব সীমিত ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র কম্পন সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, গভীর খনি খনন, তেল বা গ্যাস উত্তোলনের পর বর্জ্য তরল উচ্চ চাপে ভূগর্ভে প্রবেশ করানো, কিংবা বিশাল জলাধার বা বাঁধ নির্মাণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হওয়া।
এই ধরনের মানবসৃষ্ট কম্পনগুলো মূলত দুর্বল প্রকৃতির এবং সাধারণত টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়াজনিত প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের মতো বড় বা ধ্বংসাত্মক হয় না। যদিও মানুষ ক্ষুদ্র কম্পনের কারণ হতে পারে, বিশ্বজুড়ে যে বড় ভূমিকম্পগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়, তার জন্য মানুষ দায়ী নয়; সেগুলোর কারণ সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক।
ভয়াবহ ভূমিকম্প
মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পগুলোকে দুটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়। মাত্রার দিক থেকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ভূমিকম্পটি ছিল ১৯৬০ সালের চিলির ভালদিভিয়া ভূমিকম্প, যার মাত্রা ছিল ৯.৫ রিখটার স্কেল। এই প্রলয়ঙ্করী কম্পনের কারণে চিলিতে প্রায় ১,৬৫৫ জন মানুষ নিহত হয় এবং বিশাল এলাকা জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। তবে এর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব ছিল প্রশান্ত মহাসাগরজুড়ে সৃষ্টি হওয়া সুনামি, যা সুদূর জাপান ও ফিলিপাইন পর্যন্ত পৌঁছেছিল।
অন্যদিকে, মানব ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্পটি ছিল ১৫৫৬ সালের চীনের শানসি ভূমিকম্প, যার মাত্রা ছিল আনুমানিক ৮.০ রিখটার স্কেল। এই ভূমিকম্পে প্রায় ৮ লাখ ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। দুর্বল অবকাঠামো ও ঘনবসতির কারণে তুলনামূলকভাবে কম মাত্রার হলেও এটি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানি ঘটায়।
এছাড়া আধুনিক ইতিহাসের আরেকটি ভয়াবহ দুর্যোগ হলো ২০০৪ সালের সুমাত্রা ভূমিকম্প (৯.১ রিখটার স্কেল) এবং এর ফলে সৃষ্ট সুনামি, যেখানে ১৪টি দেশে প্রায় ২ লাখ ২৭ হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল।
এই তিনটি ভূমিকম্পই এমন ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলে ঘটেছে, যা আগেই ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে পরিচিত ছিল। তাই এগুলো সম্পূর্ণ আকস্মিক বলা যায় না বরং এগুলো পৃথিবীর স্বাভাবিক ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ারই অংশ।
১৯৬০ সালের চিলির ভালদিভিয়া ভূমিকম্প (৯.৫ রিখটার) এবং ২০০৪ সালের সুমাত্রা ভূমিকম্প (৯.১ রিখটার) উভয়ই পৃথিবীর প্রধান ভূমিকম্প বলয়—যথাক্রমে ‘রিং অব ফায়ার’ এবং ‘আলপাইড বলয়’—এর সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সীমানায় ঘটেছে, যা মূলত দুটি প্লেটের তীব্র সংঘর্ষের অঞ্চল। এসব এলাকায় শক্তি সঞ্চয় ও মুক্তি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।
অন্যদিকে, ১৫৫৬ সালের চীনের শানসি ভূমিকম্প (৮.০ রিখটার) প্লেটের সরাসরি সীমানায় না হলেও, এটি ইউরেশীয় প্লেটের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাচীন চ্যুতি রেখা বরাবর অভ্যন্তরীণ চাপমুক্তির ফলাফল ছিল। যদিও ভূমিকম্পের সঠিক সময় আগাম বলা অসম্ভব, ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলগুলোয় বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত ছিল এবং এসব ঘটনা সেই পূর্ব-বিদ্যমান প্রবণতারই প্রতিফলন।