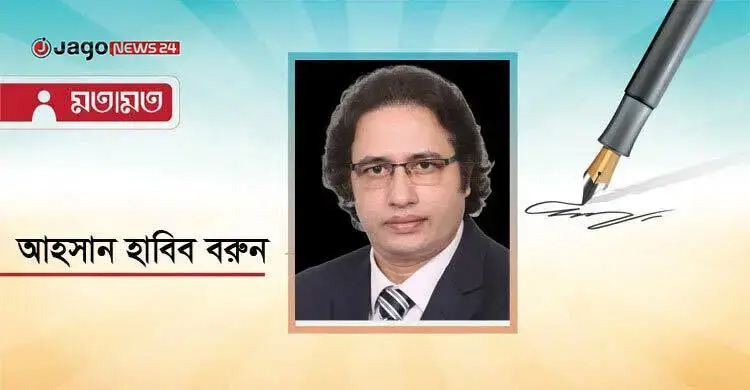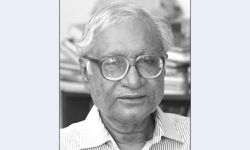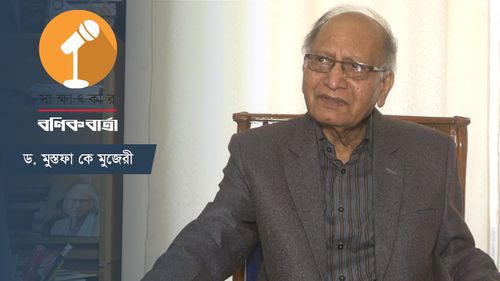
গ্রাহক বা আমানতকারীদের স্বার্থ বিবেচনা না করা হলে ব্যাংক খাত পুরোটাই ধসে পড়বে
ড. মুস্তফা কে মুজেরী, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ও সিরডাপের গবেষণা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের সার্বিক অর্থনীতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সরকারের ঋণনির্ভরতা ও ব্যাংক খাতসহ অর্থনীতির নানা ইস্যুতে সম্প্রতি কথা বলেছেন বণিক বার্তায়।
এগারো মাস পার হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের। এ সময়ে বিগত সরকারের খাদের কিনারায় রেখে যাওয়া অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে বর্তমান সরকার?
ড. মুস্তফা কে মুজেরী: বিগত সরকারের উন্নয়নের চিত্রটা একটা মেকি চিত্র। আমাদের উন্নয়নের সফলতাগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়ে একটা কল্পিত উন্নয়নচিত্র তৈরি করা হয়েছিল। অর্থাৎ বলা চলে অর্থনীতির যে বিভিন্ন পরিসংখ্যান, তথ্য-উপাত্ত সবই ছিল বানোয়াট। একটা অবাস্তব পরিকল্পিত চিত্র দেখানোর জন্য বাস্তবতাকে এড়িয়ে উন্নয়নের জোয়ারের একটা চিত্র তৈরি করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের এক বছরের কাছাকাছি হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সরকার যখন ক্ষমতাগ্রহণ করে তখন ছিল প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা অর্থনীতি। আর্থিক খাত অনেকটাই খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। প্রকৃত খাতে বা রিয়েল সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি, অপশাসন—সবকিছু মিলিয়ে নাজুক অবস্থা ছিল। অর্থাৎ আমাদের উন্নয়নকে একটা অবাস্তব চিত্রের মাধ্যমে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। এখন এই যে চ্যালেঞ্জগুলো ছিল সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে গত ১১ মাসের চিত্রটা যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানে সফলতা বেশকিছুটা কমই দেখা যায়। এ সরকার বিগত সরকারের উচ্চ মূল্যস্ফীতি ইনহেরিট করে। কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি দুই-তিন বছর ধরেই বিরাজ করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাগ্রহণ করার পর বিভিন্ন নীতি নেয়ার গ্রহণের ফলেও কিন্তু এখনো আমাদের মূল্যস্ফীতি কমেনি, যা এখনো ৯-১০ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। এটাকে কমানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনো সফলতা অর্জিত হয়নি।
দেশের ব্যাংক খাতের অবস্থা এখনো বেশ নাজুক। খেলাপি ঋণ, দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রণের কারণে এ খাতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়ে এ খাতকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তাদের পদক্ষেপ কতটুকু ফল বয়ে আনতে পেরেছে বলে মনে করেন?
ড. মুস্তফা কে মুজেরী: আর্থিক খাত মোটামুটি ব্যাংকনির্ভর খাত বলা চলে। শেয়ারবাজার ও ব্যাংক খাত দুটোই চরম দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। তা এখনো কিন্তু দুর্দশাগ্রস্তই রয়ে গেছে। এখন ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। যদিও বলা হচ্ছে, বিগত সময়গুলোয় ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো হয়েছে। এখন খেলাপি ঋণের সঠিক চিত্র বেরিয়ে আসছে। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণ উদ্ধারে আমরা কতটুকু সফলতা অর্জন করেছি সেটাও কিন্তু দৃশ্যমান নয়। অতএব ব্যাংকগুলো তাদের ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে—তেমন কোনো কাঙ্ক্ষিত চিত্র দৃশ্যমান হয়নি।
সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে নেয়া অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মসূচিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
ড. মুস্তফা কে মুজেরী: শুধু ব্যাংক নয়, অন্যান্য খাতের দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখা যায়। যেমন প্রবৃদ্ধির দিকে তাকালে দেখা যাবে, সরকারি হিসাবে বিগত বছরে প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশের নিচে। একমাত্র কভিডের সময় এক বছর ছাড়া গত দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি। এ প্রবৃদ্ধির ধারা ঊর্ধ্বগতি হওয়ার কিন্তু তেমন কোনো প্রবণতা এখনো চোখে পড়ে না। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশী বা দেশীয় বিনিয়োগের কোনো বান্ধব পরিবেশ পাচ্ছে না বলে বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন। ফলে তারা কিন্তু নতুন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। মূলধনি পণ্য আমদানির চিত্রটা দেখলে বুঝা যাবে সেটাও ইতিবাচক নয়। কাজেই সব কিছু মিলিয়ে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সফলতা অর্জিত হয়নি। এখন বিনিয়োগ যদি না হয় তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মৌলিক চাবিকাঠিটি হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগ। বিনিয়োগ না বাড়ার কারণে আমাদের কর্মসংস্থানও বাড়ছে না। বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত এবং যুব বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের বাজার সংকুচিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে প্রায় ৩০ লাখ লোক নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে যাবে।

এদিকে কৃষির ক্ষেত্রে প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ কৃষক কৃষিকাজ করে উৎপাদন খরচ তুলতে পারছেন না। অর্থাৎ লোকসানে বিনিয়োগ করছেন। কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে গত এক বছরে খুব একটা দৃশ্যমান কোনো সফলতা দেখা যায়নি। সংস্কারের ক্ষেত্রেও তেমন কোনো বাস্তব এবং অগ্রাধিকার মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি।
আর্থিক খাত সংস্কারে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমে অগ্রগতি কেমন?
ড. মুস্তফা কে মুজেরী: অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে গতি নেই বললেই চলে বা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার এখন পর্যন্ত সরকার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। এখন সার্বিকভাবে বলা যায়, বর্তমান সরকার গত এক বছরে অর্থনীতির প্রাপ্ত যে একটা ভগ্নদশা বিগত সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, সেই চিত্রটা পরিবর্তন করার জন্য প্রচেষ্টা এবং সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছে।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়িয়েছিল সরকার। সুদের হার বাড়ালেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। তাহলে মূল্যস্ফীতির জন্য কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে মনে করছেন?
ড. মুস্তফা কে মুজেরী: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজই হচ্ছে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাড়াতে সহায়তা করা। তবে যেকোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করেছে। এর মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে চাহিদাকে সংকুচিত করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। বাস্তবতা হচ্ছে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাদেশের মতো দেশে শুধু চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। নীতি সুদহার বেড়েছে কিন্তু মূল্যস্ফীতিকে ৯-১০ শতাংশের নিচে নামানো যায়নি। বেশির ভাগ সময়ই আমাদের মতো দেশে নীতি সুদহার বাড়িয়ে চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব হয় না। শুধু চাহিদাকে সংকুচিত করলে হবে না, একই সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থায় যে বাধাবিঘ্ন আছে সেগুলোকে দূর করা প্রয়োজন যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে। সরবরাহের কারণে যাতে মূল্যস্ফীতিতে কোনো প্রভাব না পড়ে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।
মূল্যস্ফীতির চালিকাশক্তি দুইভাবে সৃষ্টি হতে পারে—অতিরিক্ত চাহিদা চালিত (ডিমান্ড-পুল) এবং ব্যয়-বৃদ্ধি (কস্ট-পুশ) চালিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত মূল্যস্ফীতি এ দুটি কারণের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। যখন মূল্যস্ফীতি অতিরিক্ত চাহিদাজনিত কারণে হয়ে থাকে তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদহার বৃদ্ধি অধিকতর কার্যকর হয়। কিন্তু যখন মূল্যস্ফীতির মূল কারণ দ্বিতীয়টি, তখন কিন্তু শুধু নীতি সুদহার বৃদ্ধি খুব একটা সুফল বয়ে আনে না। আমাদের বর্তমান সময়ের যে মূল্যস্ফীতি তা কিন্তু অনেকটাই সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন বাজার ব্যবস্থায় দুর্বলতা, সংঘবদ্ধ চক্র যাকে আমরা সিন্ডিকেট বলে থাকি, মূল্য-চক্র (ভ্যালু-চেইন), অসাধু মুনাফাখোরদের চক্রান্ত ইত্যাদি নানা কারণ।
এখন চালের ভরা মৌসুম। এবার বোরো ধানের উৎপাদন ভালো হয়েছে। তার পরও সরকার কিছু পরিমাণ চাল আমদানিও করেছে, বেসরকারি খাতেও কিছু চাল আমদানি হয়েছে। এর পরও চালের বাজার অস্থির। চালের দাম গত দুই-তিন সপ্তাহে কেজিপ্রতি ৮-১০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। এর বড় কারণ হচ্ছে বাজার অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা। আমদানীকৃত পণ্য ও দেশীয় উৎপাদনকৃত পণ্য—বেশির ভাগ পণ্যের ক্ষেত্রেই সরবরাহকে একটি ইন্টারেস্ট গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করে। পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তারা বাজারের সরবরাহে সংকট সৃষ্টি করে। যেহেতু আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক নয়। অদক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত মুনাফা পেতে সক্ষম হয়। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শুধু চাহিদাকে সংকুচিত করলেই হবে না, বাজার ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সমন্বিত একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব নীতি বা অন্যান্য যে নীতি আছে তা একই লাইনে নিয়ে আসা এবং সমন্বিতভাবে এ ব্যবস্থাগুলোকে কার্যকর করা দরকার যাতে আমরা মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। এটা নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না, ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার বাড়িয়ে রেখেছে বিগত মাসগুলোয়। এর প্রত্যাশিত ফলাফল তেমন একটা চোখে পড়ে না। বাস্তবতা বলছে, আমাদের কেবল নীতি সুদহারের ওপর নির্ভর করলে হবে না। অন্য নীতিগুলোকেও একই তালে আনতে হবে, যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- বাংলাদেশের অর্থনীতি
- ব্যাংক খাত