
সমান অধিকারের দাবি কতটা বাস্তব
নারী পুরুষের সমান—এই বাক্যটি আমরা বহুবার শুনেছি। সংবিধানে, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায়, এমনকি সামাজিক প্রচারণাতেও এই কথার উচ্চারণ ঘন ঘন হয়। কিন্তু এই বক্তব্যটি বাস্তব জীবনে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, সে প্রশ্ন আজও বড় হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে আসা বাংলাদেশে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছেন ঠিকই, কিন্তু এটি কি সমান সুযোগের বাস্তবতা, নাকি এক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সংগ্রামের ফসল?
বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য করবে না। নারী অধিকার রক্ষায় আইনও তৈরি হয়েছে—যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, আইন থাকা সত্ত্বেও নারীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, হয়রানির শিকার হন এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। বহু সময় দেখা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিচারব্যবস্থাও ভুক্তভোগীর পক্ষে না দাঁড়িয়ে অপরাধীকে রক্ষা করে।
শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি দৃশ্যমান হলেও এর ভেতরে অনেক আপস রয়েছে। মেয়েরা এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ছেলেদের চেয়ে ভালো ফল করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হারও বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষাজীবনের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করলেই শুরু হয় বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হওয়া। নারীদের একই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কম বেতন দেওয়া হয়, পদোন্নতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়, মাতৃত্বকালীন ছুটিকে ‘ঝামেলা’ হিসেবে দেখা হয়। অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সহ্য করতে না পেরে প্রতিভাবান নারী নিজের চাকরি ছেড়ে দেন, যা সমাজের জন্য এক বড় ক্ষতি।

আমাদের দেশে নারীদের নীতিনির্ধারণী স্তরে অংশগ্রহণ বাড়ছে বলেই আমরা গর্ব করি। সংসদে নারী সদস্য, মন্ত্রিসভায় নারী মন্ত্রী, স্থানীয় সরকারে নারী জনপ্রতিনিধি—এই দৃশ্যগুলো যেমন আশাব্যঞ্জক, তেমনি এদের পেছনে অনেক সময় রয়েছে পুরুষের ছায়া নিয়ন্ত্রণ। সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের অনেকেই সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত নন, দলীয় মনোনয়নে এসেছেন। ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারেন না, পুরুষ নেতৃত্বের ছায়ায় থাকতে হয়। বাস্তবে তাই নারীর নেতৃত্ব নয়, পুরুষ কর্তৃত্বের সম্প্রসারণই ঘটে অনেক সময়।
নারীর প্রতিদিনের জীবনে সামাজিক কাঠামোর এক অদৃশ্য দেয়াল সব সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়—‘তুমি মেয়ে, সাবধানে কথা বলো’, ‘রাতের পর বাইরে যেয়ো না’, ‘ছেলেদের সঙ্গে মিশো না বেশি’ ইত্যাদি। এই ধরনের শিক্ষায় মেয়েরা নিজেরা নিজেদের সীমাবদ্ধ করে তোলে। কর্মজীবী নারী হলেও তাঁকে বাড়ির সব দায়িত্ব নিতে হয়—সন্তান লালনপালন, রান্না, ঘরদোর সবই তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। একজন পুরুষ যতই কর্মজীবী হন না কেন, তাঁর থেকে এই দায়িত্ব কেউ আশা করে না।
সবচেয়ে ভয়ংকর চিত্র হলো, নারীর প্রতি হেনস্তা ও সহিংসতা আজও ভয়াবহ রূপে সমাজে বিরাজ করছে। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা—এই ঘটনাগুলো যেন আমাদের নিত্যদিনের সংবাদ হয়ে উঠেছে। কেবল গা শিউরে ওঠার মতো অপরাধই নয়, নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করেও আজ সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। নিকট অতীতে দেখা গেছে, একজন নারী কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন তুললেই—যথার্থ হোক বা বিতর্কিত—তাঁকে কেবল মতবিরোধের কারণে অপমানজনক শব্দে ভূষিত করা হয়েছে। কখনো তাঁকে ‘বেশ্যা’ বলা হয়, কখনো ‘পণ্য’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এসব অপমানের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সমাজের অজুহাত—নারীর কণ্ঠস্বরকে দমন করার, তাঁকে নিরুৎসাহিত করার এক সূক্ষ্ম কিন্তু নিষ্ঠুর চক্রান্ত।
- ট্যাগ:
- মতামত
- লিঙ্গ বৈষম্য



-698a648f3096f.jpg)
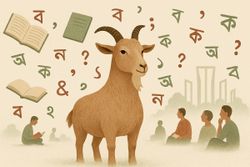

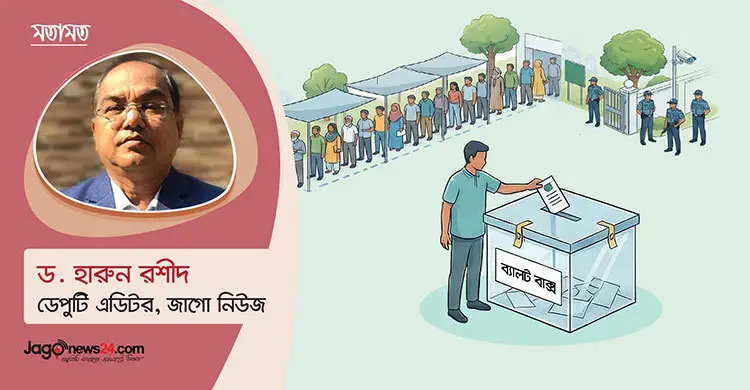

-698a65a64ca3e.jpg)
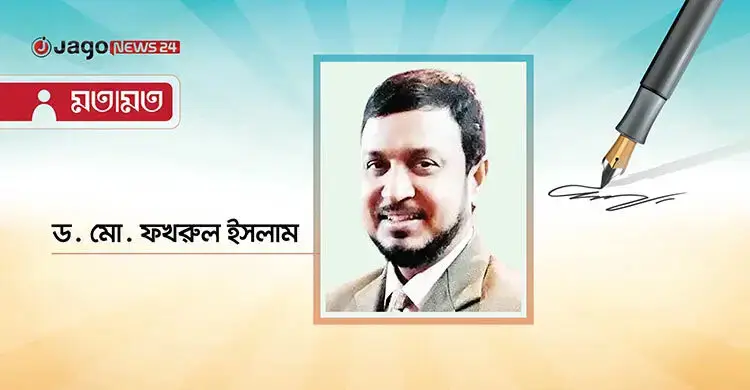
-698a65090f021.jpg)