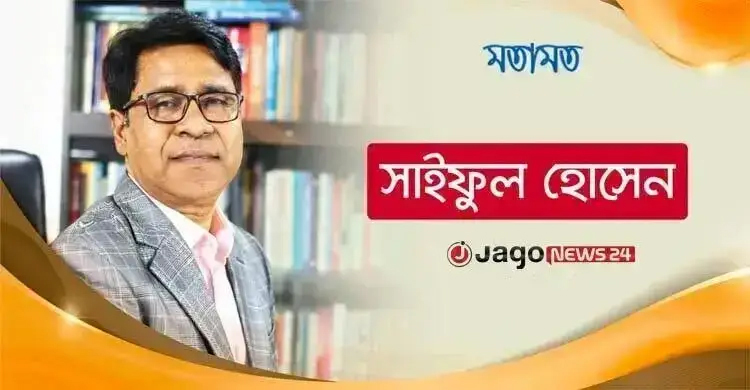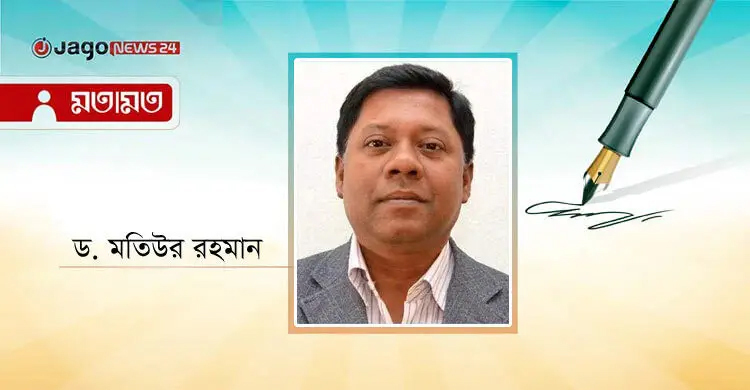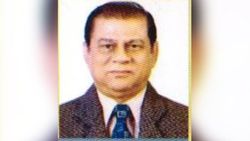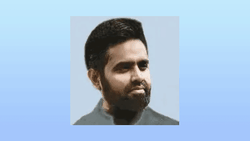যুদ্ধের আফিম থেকে মুক্তির যুদ্ধ
বর্তমান পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে, যাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থাও বলা যায়। সত্যি যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়, তা অতীতের যে কোনো যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কের, অনেক ভয়াবহ পরিণতির কারণ হবে। কেননা, এতে আছে পারমাণবিক যুদ্ধে রূপান্তরের বৈশ্বিক ভয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, তা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণের জন্য নয়, কেবলমাত্র তাদের নতুন মারণাস্ত্রটি পরীক্ষা করার জন্য। এক্ষেত্রে জাপানের শহর দুটি হামলাকারী শক্তির কাছে নয়া মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাগার ছিল মাত্র!
কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের একপক্ষীয় ব্যবহারের আশঙ্কা ক্ষীণ। আর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার মানে হবে বিশ্বজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ যা কারো জন্যই বিজয়সূচক হবে না। এ যুদ্ধে বিজয় হবে পরাজয়ের গ্লানির চেয়েও গ্লানিময়। তৃতীয় যুদ্ধ যে এতকাল না ঘটে ঠান্ডা যুদ্ধের বাক্সে আটকা পড়েছিল তার একটা কারণও এই পারস্পরিক ধ্বংসসাধনের ভয়। কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের যুগ শেষ হওয়ার পরপরই পৃথিবী এককেন্দ্রিক ও তাই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, যার ফলে যুদ্ধের নামে যুক্তরাষ্ট্র-পরিচালিত হামলা ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে।
আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন হয়ে মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ হামলা এখন ইরানকে ছুঁইছুঁই করছে। অন্যদিকে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কও যুদ্ধাবস্থার রূপ নেয়। এশিয়ায় চীনের উত্থান রুখতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত নানা ধরনের বাণিজ্যিক ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যা বিরাট যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। ইউক্রেইনে রুশ হামলা চলমান। অন্যদিকে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার পর বর্তমানে ফিলিস্তিনে চলছে ইসরায়েল পরিচালিত ইতিহাসের সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রকাশ্য গণহত্যা। আরও বহু স্থানে যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে বিরতিহীন। অতীত কালের পৃথিবীতে সংঘটিত যুদ্ধের সঙ্গে এটি এক মৌলিক পার্থক্য। এই পার্থক্যের নাম যুদ্ধ অর্থনীতি।

মানুষ কর্তৃক মানুষের হত্যা ইতিহাসে সুপ্রাচীন। কিন্তু সেটি একটি ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্পে রূপ নিতে দীর্ঘ সময় লেগেছে– এটি পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কার্ল মার্কস একে বলেছেন ‘হিউম্যান স্লটার ইন্ডাস্ট্রি’ বা মানুষ হত্যার শিল্প। ১৯৪০-এর দশকে যুদ্ধ অর্থনীতির প্রসঙ্গটি প্রথম উত্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারে কর্মরত মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড সার্ড। ১৯৪৪-এ ওয়ালটার জে. ওকস ছদ্মনামে তিনি প্রকাশ করেন তার প্রবন্ধ: টুওয়ার্ডস এ পারমানেন্ট ওয়ার ইকোনোমি।
যদিও যুদ্ধকে বৈশি^ক পর্যায়ে মানুষ দেখতে পায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এর গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এ সময় ১৯৩৯ ও ১৯৪৪-এর মাঝে অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় জার্মানিতে ৫ গুণ, জাপানে ১০ গুণ, ব্রিটেনে ২৫ গুণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ গুণ। (পারসপেকটিভস অব দ্য পারমানেন্ট ওয়ার ইকোনোমি, টনি ক্লিফ, মে ১৯৫৭, অনলাইন) এভাবে এটি রূপান্তরিত হয়ে যায় সার্ড-কথিত পারমানেন্ট ওয়ার ইকোনোমি বা স্থায়ী যুদ্ধ অর্থনীতিতে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ অর্থনীতিতে উত্তরণের কথা বলেছিলেন দেশটির ৩৪তম প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার ১৯৬১ সালে তার বিদায়ী ভাষণে। এই ভাষণে তিনিই প্রথম ‘সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স’ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন এবং তার উৎপত্তিকাল ও বিপজ্জনক ভূমিকারও ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেছিলেন, “সাম্প্রতিক কালের বৈশি^ক সংঘর্ষের পূর্ব পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র কারখানা ছিল না। আমেরিকার লাঙ্গল প্রস্তুতকারকরাই প্রয়োজনের সময় তরবারি তৈরি করত। কিন্তু এখন আর আমরা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই জরুরি সমাধানের ওপর নির্ভর করতে পারি না। আমরা বাধ্য হয়েছি বিশাল আকৃতির অস্ত্রের কারখানা তৈরি করতে। এর সঙ্গে ৩৫ লাখ মানুষ এখন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োজিত রয়েছে। বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সব শিল্পকারখানা থেকে যা আয় হয় আমরা তারচেয়ে বেশি ব্যয় করি নিরাপত্তা খাতে।”
- ট্যাগ:
- মতামত
- যুদ্ধ ও সংঘাত
- পারমাণবিক অস্ত্র