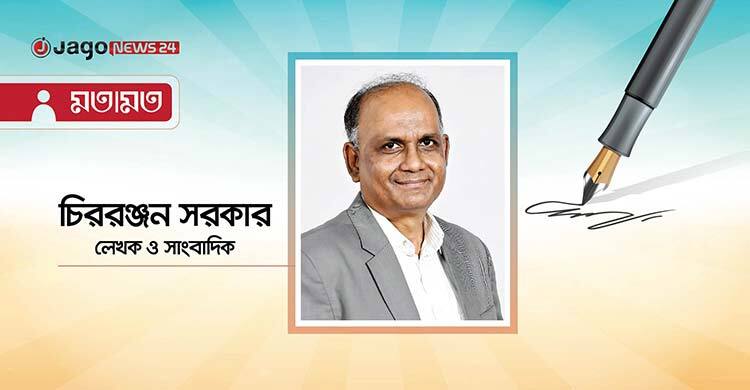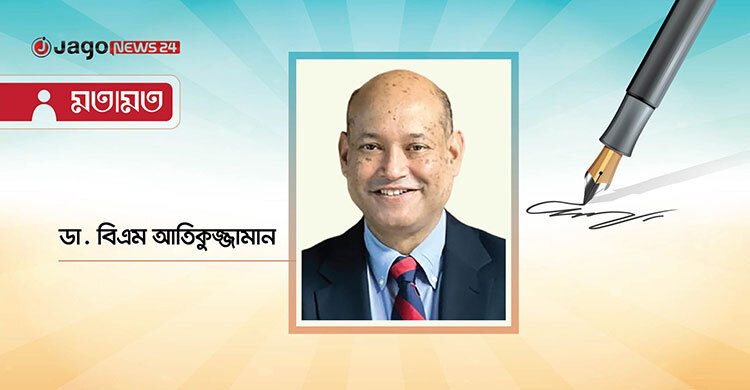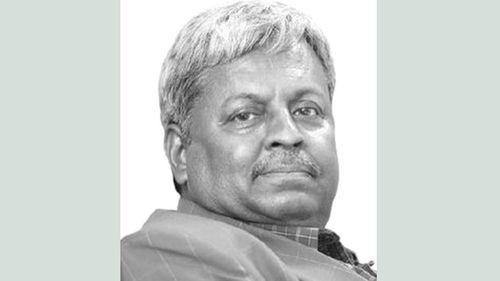
কোথায় সেই শান্তি, মৈত্রী ও অহিংস ধর্মের নীতি?
যারা আমার লেখালেখির সঙ্গে এক-আধটু পরিচিত, তারা সবাই জানেন, নরেন্দ্র মোদি সরকারের নীতি নিয়ে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি রয়েছে। তার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাব না। মাননীয় মোদিজির দল বিজেপি ও তাদের থিংকট্যাংক আরএসএসের রাজনীতির এমন অনেক দিক আছে, যা ভারতের বহুত্ববাদী রাষ্ট্রকাঠামো-বিরোধী। ইদানীং বিজেপির ‘হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি’ ও ‘গোদী মিডিয়া’ মিলে যে ন্যারেটিভ জনমনে চারিয়ে দিয়েছে-নরেন্দ্র মোদির নীতির সমালোচনা মানেই দেশবিরোধিতা-এ ধারণা সর্বৈব ভুল। গণতন্ত্র বহু মতের মিলনক্ষেত্র। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বয়ং তৎকালীন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা রাম মনোহর লোহিয়াকে মন্ত্রী থেকে অনুরোধ জানালে লোহিয়া বলেছিলেন, ‘গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠস্বর খুবই জরুরি। না হলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। ফলে আমি বিরোধী চেয়ারেই থাকব।’
নরেন্দ্র মোদির সরকার ভিন্ন স্বরকে খুব একটা স্বাগত জানান, এরকম দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে না। অথচ মোদিজির পূর্বসূরি অটল বিহারী বাজপেয়ী নীতির প্রশ্নে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপস না করলেও ব্যক্তিগত স্তরে সবার সঙ্গেই ছিল তার সৌজন্যের সম্পর্ক। রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একবার অটলজি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শোনা যায় তার কিডনিতে সমস্যা হয়েছে। খবর পেয়েই রাজিব গান্ধী জানতে চান, অটলজি বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করবেন কিনা! অটলজি স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলে দেন, ‘আমার অত পয়সা নেই।’ রাজিব গান্ধী কিছুদিন বাদেই লন্ডনের এক রাজনৈতিক ডেলিগেশনের সঙ্গে অটলজিকে পাঠান; যাতে সেখানে তিনি চিকিৎসাও করেন, সে ব্যবস্থাও করে দেন। অটলজি সুস্থ হন। এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তে অটলবিহারী বাজপেয়ী নিজেই লিখে গেছেন।
সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও আর নেই। এখন রাজনীতিকদের ভাষা, আচরণ অনেক বদলে গেছে। গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদের ভেতরেও অনেকেই এমন সব ভাষা ব্যবহার করেন, যা শিষ্টাচারবহির্ভূত। দ্রুত বদলে যাচ্ছে দুনিয়া। কেউ যুক্তি দেবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কোনোকিছুই তো অচল-অনড় নয়। সভ্যতার ধর্মই পরিবর্তন। কলকাতাও চোখের সামনে কেমন দ্রুত বদলে গেল। উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রাপার, বিশাল শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্স, ঝাঁ চকচকে এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি বদলে যাওয়ার ইনডেক্স। তবে এসব তো বহিরঙ্গের বদল। প্রাণের শহর কি ভেতরে ভেতরেও বদলে যায়নি! বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, অন্তত একবার কলকাতা না দেখলে বিশ্ব পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস বারেবারে ছুটে আসতেন এ শহরের উত্তাপ পেতে। এ শহর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। জীবনানন্দ দাশের। এবং কাজী নজরুল ইসলামের। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার এক মেসে বসে লিখেছিলেন ‘আরণ্যক’। চোখ বন্ধ করে সময়টাকে যেন দেখতে পাই। দেখি, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসছেন জীবনানন্দ। জন্ম নিচ্ছে কৃত্তিবাস পত্রিকা। কফি হাউজ আলো করে বসে আছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, আরও অনেকে।

উত্তর কলকাতার অলিগলিতে রাত গভীর হয়। ঠুংঠুাং শব্দ করতে করতে শেষ ট্রাম চলে যায়। সারা দিনের ক্লান্তি মেখে রিকশা গ্যারেজ করে শোওয়ার তোড়জোড় করতে থাকেন বৃদ্ধ রাজকুমার পাসোয়ান। সুদূর বিহারের আরা জেলার নারহি গ্রাম থেকে এসে তিনিও পাকাপাকিভাবে আজ কলকাতার বাসিন্দা। এসব নানা দৃশ্যকল্প তো আমার দেখা। দেখা সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ শহরকে। এরও আগের কলকাতাকে কল্পনা করুন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রেসিডেন্ট কলেজের গেটে ঢুকছেন প্রিয় অধ্যাপক রিচার্ডসনের ক্লাস করতে। সঙ্গে বন্ধু গৌরদাস বসাক ও অন্য অনেক যুবক। কিংবা মনে করুন যুক্তিবাদী হেনরি ডিরোজিওকে বহিষ্কার করছেন রক্ষণশীল কলেজ কর্তৃপক্ষ। চল্লিশের দশকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে অথবা গাড়িতে চলেছেন সোহরাওয়ার্দী। রিপন স্ট্রিটের বাসায় মহাব্যস্ত মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেম। কত কত চরিত্র-আকরাম খান, মুজফ্ফর আহমদ। তো কলকাতা তখন যতটা হিন্দুর, ততটাই মুসলমানের। কলকাতার মূল সুর ছিল সর্বধর্ম, সর্বমতের মিলনস্থল।
কলকাতার অন্তর বলতে কেন জানি না, আমার মৃণাল সেনের বলা গল্পটা মনে পড়ে। মৃণাল দা লিখেছিলেন ঘটনাটা। তখন সত্তর দশকের আগুনঝরা কলকাতা। সেই সময়কে সেলুলয়েডে ক্যামেরা বন্দি করতে ফ্রান্স থেকে ছুটে এলেন, বিশ্ববন্দিত বুদ্ধিজীবী লুই মাল। তিনি এসেই মৃণাল সেনকে বগলদাবা করে সটান কার্জন পার্কের কাছে। সেদিন ওখানে বামপন্থি ছাত্রদের কোনো বিক্ষোভ কর্মসূচি বোধহয় ছিল। মিছিল আসছে। গরম গরম স্লোগান। পুলিশের বিরাট বাহিনীর বিপুল তৎপরতা। মৃণাল সেন ঈষৎ চিন্তিত বন্ধুর নিরাপত্তা নিয়ে। আচমকা এক পুলিশ অফিসার মৃণাল সেনের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলেন, ক্যামেরা হাতে ভদ্রলোক কি লুই মাল! একটু আলাপ করিয়ে দেবেন। আমি ওঁর খুব ভক্ত। মৃণাল দা আলাপ করিয়ে দিলেন। লুই মাল তো হতবাক। ওই পুলিশ অফিসার, যে হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করবে, সে কিনা তার অনুরাগী! এই অদ্ভুত বৈপরীত্য একমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়। বিষণ্ন হৃদয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেই কলকাতা বদলে গেছে। এ শহরে এখন ফিলিস্তিন প্রশ্নে মুখ খোলাও বিপজ্জনক। গাজা মাটির সঙ্গে মিশে গেলে এখানে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসির ইমোজি দেখি। আর এখন তো এ শহরে যুদ্ধ পরিস্থিতি। মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা এখন মিনি যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ। মিগ, রাফাল, মিরাজ-কে কতদূর থেকে শত্রু বিনাশ করতে পারে, তাই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লিখেছিলেন মন্বন্তর। যা নিয়ে আজ ঘরে ঘরে চাঞ্চল্য, এয়ার স্ট্রাইক, মক প্রস্তুতি, নিরাপদ জোন, তা বহুকাল আগেই লিখেছিলেন মহতী এই কথাকার। কাগমারী সম্মেলনে এ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেই হাঁটতে হাঁটতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, দেখবেন অখণ্ড পাকিস্তান টিকবে না। দশ-বারো বছরের মধ্যেই পূর্ববাংলা আলাদা হয়ে যাবে। তা-ই তো হলো। বরেন বসুর রংরুট পড়লেও যুদ্ধপ্রেমী বঙ্গসন্তানদের সংবিৎ ফিরতে পারে যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক