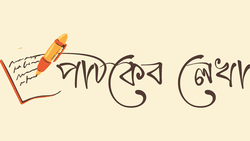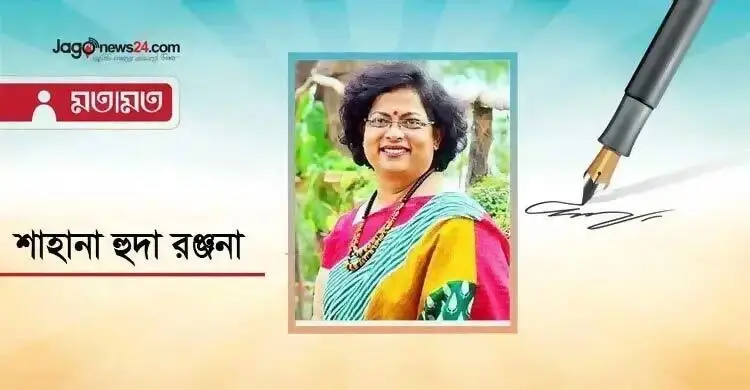৫৪ বছরেও যা নির্মূল করা যায়নি
একাত্তরের যুদ্ধকালের মতো সমষ্টিগত দুঃসময় আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। যুদ্ধটা ছিল রাজনৈতিক এবং তাতে জাতীয়তাবাদ নানাভাবে ও বিভিন্ন দিক দিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তি সে সময়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, তার দুর্বলতাও যে ধরা পড়েনি এমন নয়। বাঙালির জাতীয়তাবাদের শক্তি ছিল ঐক্যে, দুর্বলতা ছিল নেতৃত্বের পেটি বুর্জোয়া চরিত্রে।
বিপরীত পক্ষে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদও পরীক্ষা দিয়েছিল। তার দুর্বলতা ছিল অনৈতিকতায় ও অনৈকের। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের কৃত্রিমতা তখন উন্মোচিত হয়ে যায়। ছাপ্পান্ন জনের ওপর চুয়াল্লিশ জন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; আক্রমণের চরিত্রটা ছিল গণহত্যার। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের রক্ষকেরা পরিণত হয়েছিল হানাদার ঘাতক ও দস্যুতে; তাদের অন্য কোনো জোর ছিল না অস্ত্রের জোর ছাড়া। নৈতিক জোর তো নয়ই। ওই যুদ্ধে ভারত যুক্ত হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই, তাদের তাগিদটাও জাতীয়তাবাদেরই ছিল। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া এদের সংযোগটাও যে জাতীয় স্বার্থের বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।
আসলে বাংলাদেশের মানুষ তো একসময় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকেই নিজেদের মধ্যে ধারণ করত। এমনকি একাত্তরের প্রথম দিকেও। পয়লা মার্চ ঢাকার স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চলছিল পাকিস্তানি টিমের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এমসিসি টিমের; পরিবেশটা ছিল রীতিমতো উৎসবমুখর। স্টেডিয়াম ভর্তি বাঙালি দর্শকেরা সবাই প্রবলভাবে পাকিস্তানি দলকে সমর্থন করছিল; কিন্তু ভরদুপুরে যে মুহূর্তে শোনা গেল গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে, অমনি দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেল।

স্টেডিয়াম মুখরিত হলো ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিতে। আসন তছনছ করা, আগুন জ্বালানো, সবকিছু ঘটল। পাকিস্তানি খেলোয়াড়েরা আক্রান্ত হলো, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাহারায় তাদের জান বাঁচিয়ে আশ্রয় নিতে হলো এমপি হোস্টেলে, মাস ঘুরতে না ঘুরতেই যে আবাসটি পরিণত হয়েছিল বাঙালি নির্যাতনের কেন্দ্রে। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিছুটা পরিবর্তিত জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল এবং আক্রমণের মুখে তা প্রতিরোধে পরিণত হয়েছিল। আক্রমণটা পাকিস্তানিরাই করেছে এবং কাজটা শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই সাতচল্লিশ সালেই। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই।
কিন্তু তবু সত্য তো এটাও যে একদা বাঙালি মুসলমানই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তারা একই সঙ্গে বাঙালি ও মুসলমান ছিল। বাঙালিত্বটাই ছিল প্রধান, সেটিই ছিল স্বাভাবিক, তবে তারা নিজেদের মুসলমান পরিচয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছিল রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আশাতে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তাদের স্বপ্ন আক্রান্ত হয়েছে। ওই আক্রমণের মুখেই তারা তাদের বাঙালি পরিচয়ের কাছে ফিরে গেছে, ওই পরিচয়টিকেই প্রধান করে তুলেছে। আক্রমণটি চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল ২৫ মার্চের মধ্যরাতে। অখণ্ড পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার কাজটা বাঙালিদের হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করেনি, পাকিস্তানি হানাদারেরাই সেটা শুরু ও শেষ করেছে।
সত্য এই যে, জাতীয় মুক্তির জরুরি প্রশ্নটিকে সবাই সমান গুরুত্ব দিতে পারেননি। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রভাব ছিল; ছিল আচরণগত অভ্যাস, এমনকি ওই জাতীয়তাবাদে আস্থা যে ছিল না, তা-ও নয়। যে জন্য দেখা যায় একাত্তরের আগে তো বটেই, পরেও স্থানে স্থানে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের চিহ্ন রয়ে গেছে, বন্যার স্রোত নেমে গেলেও যেমন পানি আটকে থাকে এখানে-সেখানে। যেকোনো বিশ্বাসের পক্ষেই মানসিক সম্পত্তি ও আশ্রয়ে পরিণত হওয়াটা কোনো অসম্ভব ঘটনা নয়। দক্ষিণপন্থীরা পাকিস্তানি ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন, বামপন্থীদের একটি অংশকেও দেখা গেছে শ্রেণি প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে জাতি প্রশ্নকে পেছনে ঠেলে দিয়েছেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের যেভাবে অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত ছিল, সেভাবে তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সেই সঙ্গে এটাও তো জানি আমরা যে মার্চ মাসের শেষ দিনগুলোতে বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তানিদের হর্তাকর্তা ইয়াহিয়া খান যে দরকষাকষি করছিলেন, সেটা পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য ছিল না, ছিল তাকে বাঁচানোর জন্যই। সবকিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বলয় থেকে বাঙালির পক্ষে বের হয়ে যাওয়াটা সহজ ছিল না; মতাদর্শিক নিষেধটা নষ্ট হয়ে যায়নি, তার চেয়েও প্রবল ছিল রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা। মুজিবের পেছনে ছিল জনমতের অকুণ্ঠ সমর্থন, ইয়াহিয়ার হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। জনমতের জন্য জায়গা করে দেওয়াটা হতো ন্যায়সংগত, সেটা ঘটেনি; অস্ত্র দমন করতে চেয়েছে জনমতকে। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি; জনমতেরই জয় হয়েছে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীরা হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের যে মহোৎসব বসিয়েছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।