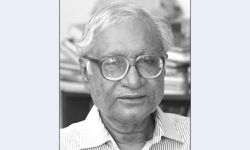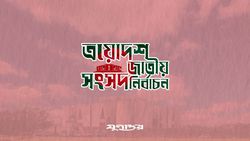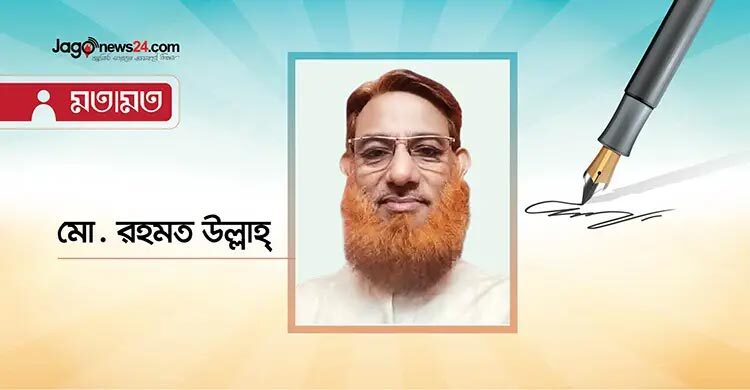বাজার কেন বেসামাল
২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পেশ হবে আগামী ৬ জুন। এই মুহূর্তে ব্যবসায়ীদের অভাব-অভিযোগ ও দাবির কোনো শেষ নেই। আবার ‘মিডিয়া রিপোর্ট’ অনুযায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো শেষ নেই। এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা যে সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরছেন, তার মধ্যে আছে ডলারের দাম, ডলারের অভাব, আমদানি সংকোচন নীতি, ঋণের অভাব, বৃহত্তম ঋণের ঊর্ধ্বসীমা, উৎসে কর ধার্য, সুদ ভর্তুকি প্রত্যাহার, ভর্তুকি হ্রাসের ঝুঁকি, করপোরেট কর হ্রাস, ঋণের ওপর উচ্চ সুদ ইত্যাদি। এর বাইরেও অনেক দায়-দাবি আছে।
ওদিকে যাচ্ছি না। তবে ঠিক এই মুহূর্তে বেশি শোরগোল হচ্ছে ঋণের ওপর উচ্চহারের সুদ নিয়ে। তাঁরা বলছেন, ঋণের ওপর সুদের হার মারাত্মক পর্যায়ে উঠেছে। এটা সহ্যসীমার বাইরে। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বাজারে টেকা যাচ্ছে না। উচ্চ উৎপাদন খরচে বিক্রয়মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। এই মূল্যে ক্রেতা নেই—দেশে অথবা বিদেশে। সুদব্যয় (ইন্টারেস্ট এক্সপেন্ডিচার) এত বেড়েছে যে ব্যাংকে ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে। ঋণের কিস্তি অনেক বেড়েছে, যা পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এদিকে ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মালের আমদানি খরচ বেড়েছে, এর ওপর শুল্ক-কর বৃদ্ধি পেয়েছে, ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই ১০০ টাকা ঋণে যে কাজ হতো, এখন তাতে লাগছে ১৫০ টাকা। অথচ ঋণের পরিমাণ বাড়াতে ব্যাংক রাজি নয়। বড় বড় ঋণগ্রহীতাকে বলা হয়েছে আর কোনো নতুন ঋণ দেওয়া হবে না। যতটুকু পরিশোধ হবে, ততটুকুই আবার পাওয়া যাবে, এর বেশি নয়। এতে বড় বড় গ্রাহক আছেন বিপদে।
এসব সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা ছুটছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে, ছুটছেন মন্ত্রীর কাছে। বসছেন নিজেরা—পথ কী তাহলে? গ্যাসসংকট, বিদ্যুৎসংকট ও মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের অভাব, ঋণের অভাব, সুদের হার বৃদ্ধি—তাহলে কি ব্যবসা বন্ধ করতে হবে? বড় কঠিন প্রশ্নই বটে। সমাধান কী, তা কেউ জানে না—সবাই প্রত্যাশা করে আছে একটা ‘মুস্তফা কামাল মার্কা’ বাজেট নয়, একটা বাস্তববাদী বাজেটের জন্য। এটা কি হবে? ঐতিহাসিক ৭ জুন সামনে রেখে এই প্রশ্ন। আসি তাহলে ঋণের ওপর সুদের হারের ইস্যুতে।
আমাদের সবারই হয়তো মনে আছে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমানত ও ঋণের ওপর সুদের হার নির্ধারণ করত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই হার ব্যাংকভেদে। এতে প্রতিযোগিতা বিঘ্নিত হতো। বাজার অর্থনীতির নীতি লঙ্ঘিত হতো—এ কথা বলে ১৯৯০-৯৫-এর দিকে সুদের হার নির্ধারণের কাজ ছেড়ে দেওয়া হয় নিজ নিজ ব্যাংকের বোর্ডের কাছে। ঋণ শ্রেণিবদ্ধকরণ (ক্ল্যাসিফিকেশন) ইত্যাদি ইস্যুও ছেড়ে দেওয়া হয় ব্যাংকের কাছে। ফল যে খুব বেশি ভালো হয়, তা বলা যাবে না। তবু মোটামুটি চলছিল। হঠাৎ এলেন এক অ্যাকাউন্ট্যান্ট অর্থমন্ত্রী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি অনেক কথা বলে এক হোটেলে বসে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ঠিক করে দিলেন সুদের হার। আমানতের ওপর ৬ শতাংশ সুদ হবে সর্বোচ্চ। ঋণের ওপর হবে ৯ শতাংশ; যা পরিচিতি পেল ‘নয়-ছয়’ সুদনীতি হিসেবে। ‘নয়-ছয়’ কী, তা সবারই জানা। বলা হলো, ব্যবসায় খরচ কমবে, প্রতিযোগিতা ভালো হবে। বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান হবে। পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরে আসবে। সরকারের রাজস্ব বাড়বে। কিন্তু এতে যে বাজার অর্থনীতি বিসর্জিত হলো, তা মুস্তফা কামালের বিবেচনায় ছিল না। শুধু তা-ই নয়, তিনি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ জাতীয় সব নীতিতে ঘন ঘন পরিবর্তন এনে ঋণশৃঙ্খলায় আনেন এক বিপর্যয়। আমানতকারীরা নিরুৎসাহিত। সঞ্চয়পত্র বন্ধ হয় হয়। দেশে সঞ্চয় হয় নিরুৎসাহিত। নীতি হয়ে যায় যেন ‘ঋণ করেই খাও সবাই’। হঠাৎ চলে এল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)—আমাদের উদ্ধারকর্তা।