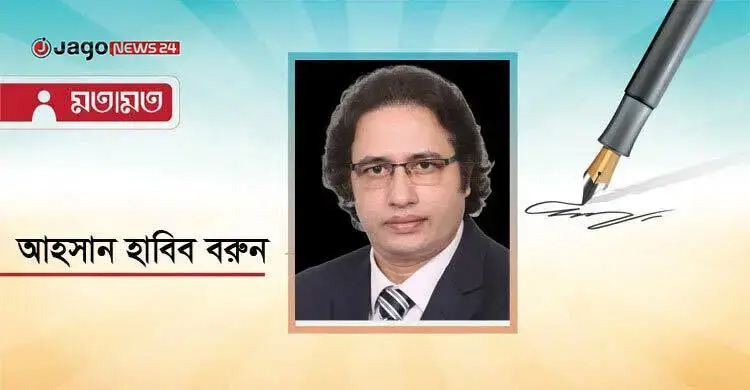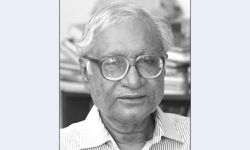যে কারণে পরিবেশ পুলিশ প্রয়োজন
তাংগুক নদীর পলির আর্সেনিক, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, কপার, মারকারি ও লেডের মাত্রা ৯টি স্থান থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বিশ্লেষিত ফলাফলে দেখা যায়, আর্সেনিক দূষকের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে কোনো কোনো স্থানে তিনগুণেরও বেশি। বিশ্লেষিত পলির নমুনায় কোবাল্ট দূষকের পরিমাণ প্রায় ৭০ গুণ বেশি পাওয়া যায়। মারকারি দূষকের পরিমাণ ৩১.৯ গুণ এবং লেড দূষকের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ১৬ গুণ বেশি পাওয়া যায়। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদের পলিতে ক্রোমিয়ামের মাত্রা বেশি। আবার বুড়িগঙ্গার পলিতে লেড ও ক্যাডমিয়ামের মাত্রা অনুমোদিত মাত্রা থেকে বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া আর্সেনিক, জিংক ও কপারের পরিমাণও বেশি পাওয়া যায়। সেজন্য আমাদের দেশের পলির নমুনা পরীক্ষা করে দূষণের মাত্রা জানা প্রয়োজন। কারণ জলজপ্রাণীর মাধ্যমে এসব হেভি মেটাল (আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি) ‘ফুড চেইনে’ চলে আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশের নদী বা অন্যান্য পলি নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। কোনো বই বা প্রকাশিত জার্নাল পেপারও এ বিষয়ে পাওয়া যায়নি। সেজন্য এ বিষয়ে অনেক গবেষণা এবং কাজ করার সুযোগ আছে। সংশ্লিষ্ট সবার সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। উপরন্তু, পলি দূষণের উৎসগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
মৃত্তিকা দূষণ ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের উপায় : ইটভাটায় মৃত্তিকার পরিবর্তে ব্লক দিয়ে বা বিকল্প উপায়ে ইট তৈরি করা যেতে পারে। কৃষি ও অকৃষি জমির মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা করতে হবে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে পরিমাণমতো সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। শস্যাবর্তন (Crop Rotation) ও শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification) করা যেতে পারে। সর্বোপরি মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে একটি প্রতিষ্ঠান এর সমন্বয় করতে পারে; তারা কমিউনিটিকে এবং সব অংশীজনকে প্রেরণা দিতে পারে।
জলাশয়, হাওড়-বাঁওড়, নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি দূষণমুক্ত রাখা : দেশের সমুদ্র, নদ-নদী, পুকুর, হাওড়-বাঁওড়, বিল ও অন্যান্য জলাশয় প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রথমত দূষণের উৎসগুলো খুঁজে বের করতে হবে। কল-কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্যগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে হবে। অর্থাৎ শক্ত বস্তুকে এক ক্যাটাগরিতে, রিসাইক্লিংযোগ্য বস্তুকে অন্য ক্যাটাগরিতে এবং পচনশীল ও দূষকমুক্ত বর্জ্যগুলো আলাদা করে অন্য ভাগে ভাগ করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া বর্জ্য পানি ট্রিটমেন্ট করে জলাশয়ে ছাড়তে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, সুপারভিশন ও প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্যরে রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থাকরণ : যে কোনো বর্জ্যই রিসাইক্লিং করা যায়। প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্যরে রিসাইক্লিং অতি প্রয়োজন। পলিথিন, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য এবং এফলুয়েন্ট বা বর্জ্য পানিকে রিসাইক্লিং বা ট্রিটমেন্ট করে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেজন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন-যার ফলে মৃত্তিকা, পলি, জলাশয়, নদী, সমুদ্র দূষণমুক্ত থাকতে পারে এবং মাছসহ বিভিন্ন জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা পাবে।
পাহাড়ে পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ ও নেট দিয়ে পাহাড় সংরক্ষণ : দেশের পাহাড়গুলো চাষাবাদের জন্য অবস্থাভেদে জিরো-টিলেজ ও নো-টিলেজ (খুবই কম মৃত্তিকা খনন বা কোনো খনন ছাড়াই চাষ করা), টেরাসিং (পাহাড়ে একটু পরপর বেড বা খাঁজ তৈরি করা), মালচিং (গাছের পাতা বা অন্যান্য অংশ দ্বারা ঢেকে চাষ করা; যেমন, পাহাড়ে আনারস যেভাবে চাষ করা হয়) করে চাষ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে চীনের ইউনানসহ বিভিন্ন প্রদেশে লোহার জাল দিয়ে ভঙ্গুর ও ধসে যাওয়ার সম্ভাবনাময় পাহাড়গুলো ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পাহাড়গুলোর ধস বা ক্ষয়ে যাওয়া রোধ হচ্ছে এবং সেগুলো সবুজ লতা-পাতা ও বৃক্ষরাজিতে ভরে গেছে। চীনের ওইসব মরুময় পাহাড়ি এলাকায় এখন প্রাণ ফিরে এসেছে এবং সবুজ ও সুশোভিত হয়ে উঠেছে। দেশের যেসব পাহাড়ে এখনো গাছপালা জন্মেনি অথবা কম গাছপালা অথবা পাহাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ওইসব পাহাড়ে চীনের ইউনান প্রদেশের মতো লোহার জাল ব্যবহার করে সুরক্ষা দেওয়া যেতে পারে।
পাহাড়ে বৃক্ষরোপণ ও পাহাড় সংরক্ষণ : এদেশে পাহাড় থেকে কাঠ, ফল, পাথর, কয়লা, ধান, কলা, কচু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আসছে। তাই সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। উঁচু পাহাড়ি এলাকায় গর্জন, গামারি, কাঁঠাল, চাপালিশ, বহেড়া, মেহগনি, সেগুন, লেবু ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ করা যেতে পারে। এছাড়া নিচু পাহাড়ি এলাকায় গর্জন, গামারি, কাঁঠাল, আম, লিচু, লেবু, রাবার, জলপাই, আমলকী, পেয়ারা, হরীতকী, বহেড়া, সেগুন, মেহগনি, কদম চাপালিশ ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ করে পাহাড় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
সুন্দরবন ও অন্যান্য লবণাক্ত ও উপকূলীয় এলাকা সংরক্ষণ : সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিভিন্নভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে রক্ষা করে চলেছে-কাঠ, বাঁশ, বেত গোলপাতা, মধু, মোম, মাছ ইত্যাদি সরবরাহ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস থেকে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও বৃহত্তর বরিশালের একটা অংশকে রক্ষা করছে। সুন্দরবন ও অন্যান্য উপকূলীয় লোনামাটি অঞ্চলে নারিকেল, সুপারি, তাল, তেঁতুল, খেজুর, আমড়া, শিরিষ, বাবলা, কাঠবাদাম, জলপাই ইত্যাদি বৃক্ষ প্লানটেশন করতে হবে এবং একটি গ্রিন বেল্ট তৈরি করতে হবে। তাছাড়া অধিক লবণাক্ত মৃত্তিকায় সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বাইন, ধুন্দল, গরান, গোলপাতা গাছ জন্মে এবং এগুলো প্লানটেশন করে সুন্দরবন, অন্যান্য লবণাক্ত ও উপকূলীয় এলাকা সংরক্ষণ করা যেতে পারে।