
রোহিঙ্গা সমস্যা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন
কেউ জানে না, বাংলাদেশের আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের সামনে অপেক্ষা করছে কেমন ভবিষ্যতের হাতছানি। কত দিন তারা মানবেতর জীবনের জ্বালা সহ্য করবে ক্যাম্পের ঘেরাটোপে? কবে তারা ফিরে যেতে পারছে তাদের স্বদেশ, জন্মভূমির সুমৃত্তিকায়? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা খুবই জরুরি।
প্রায় আট বছর পেরিয়ে গেছে, যখন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতনের মুখে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আজ তাদের সংখ্যা কক্সবাজারের কুতুপালংসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে ১৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির স্থাপনকারী দেশে। গত ৮ বছরে প্রায় ৪ লাখ জনসংখ্যা বেড়েছে ক্যাম্পগুলোতে। ক্যাম্পগুলোতে ২৪ ঘণ্টায় ১৩০-১৩৫ জন অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ছয়টি শিশুর জন্ম হচ্ছে, যা বছরে প্রায় ৫০ হাজার। ফলে প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।
এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য কূটনৈতিক বৈঠক, চুক্তি এবং আলোচনার পরও প্রত্যাবাসনের কোনো বাস্তব অগ্রগতি হয়নি। কেন? কারণ, কাগজে-কলমে যে ‘সমাধান’-এর কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই-এটাই তুলে ধরেছে সাম্প্রতিক বাস্তবতা।
একদিকে মিয়ানমার বলছে, তারা ‘বিতাড়িত জনগণ’কে ফেরত নিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে, বাংলাদেশ চায় এ দীর্ঘস্থায়ী বোঝা হালকা হোক। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পক্ষ রোহিঙ্গারা-তারা নিজেরাই এ প্রত্যাবাসনে অরাজি। তাদের সরল বক্তব্য: ‘আমরা অধিকার ছাড়া, নিরাপত্তা ছাড়া, নাগরিকত্ব ছাড়া ফিরব না।’
নির্যাতনের স্মৃতি নিয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা তাদের বাস্তবতার দিক থেকে হয়তো ঠিকই বলছে। কারণ, যে প্রত্যাবাসন পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, তার ভিত্তি হলো ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড (এনভিসি)-এমন এক পরিচয়পত্র, যা রোহিঙ্গাদের ‘বিদেশি’ হিসাবে চিহ্নিত করে। এ কার্ড তাদের মিয়ানমারের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। বরং এটিই তাদের বৈধভাবে বঞ্চিত করার এক আইনগত উপায়। তদুপরি, আরও রয়েছে ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন-যা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে।
নাগরিক অধিকার ছাড়াও নিরাপত্তার প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুতর। রাখাইন রাজ্যে এখনো যুদ্ধ চলছে। ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে সেখানে বিদ্রোহী আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বেড়েছে। বহু গ্রাম জনশূন্য, অনেক অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর আগের গণহত্যা ও নির্যাতনের বিচার, এ অবস্থায় এখনো দূরঅস্ত।

এ পরিস্থিতিতে ‘স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন’-এ শব্দগুলো বাস্তবে কতটা অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য? প্রসঙ্গত, যেসব ‘পাইলট প্রকল্প’ বা ‘মানবিক করিডোর’-এর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো অধিকাংশ সময়ই প্রতীকী উদ্যোগ। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর অনেকটাই রাজনৈতিক প্রদর্শনী। নাগরিকত্ব, জমির অধিকার, নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা ছাড়া এসব শুধুই একরকম মরীচিকা।
সামগ্রিক বিবেচনায়, রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি ও চ্যালেঞ্জিং ইস্যু। আন্তর্জাতিক সহায়তা হ্রাসের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে এত বড় শরণার্থী জনগোষ্ঠীকে বহন করা বাস্তবসম্মত নয়। অপরদিকে, মিয়ানমারের সরকার আন্তর্জাতিক চাপে নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে চায়। কিন্তু এ সংকট সমাধানে আঞ্চলিক জোট যেমন আসিয়ান বা বিমসটেক-তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না।
মূল সমস্যা হচ্ছে, শুধু চুক্তি বা বক্তৃতা দিয়ে এ সংকটের সমাধান হবে না। একটি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে, তাদের পরিচয় অস্বীকার করে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত না করে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া যাবে কিনা, এসব প্রশ্নেরও সুরাহা করতে হবে। ফলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচারের বিষয়টিও যুক্ত হওয়া আবশ্যক। রোহিঙ্গাদের তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় অংশ নিতে দিতে হবে। নাগরিকত্ব আইন সংস্কার, আন্তর্জাতিক তদারকি এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন পরিকল্পনা ছাড়া এ সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের সম্ভাবনা নেই।
রোহিঙ্গাদের নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় যা করছে তাতে সুফল মিলছে না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের একার পক্ষে এ জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। মিয়ানমারের সরকার সমস্যার সৃষ্টিকারী। মুখে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও রোহিঙ্গার জন্য তারা কিছুই করবে না, এটা স্পষ্ট। এদিকে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল আরাকান বা রাখাইন রাজ্যে চলছে তুমুল সংঘাত। সেখানে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে বিদ্রোহী আরাকান আর্মি। অতএব, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান ও প্রত্যাবাসনের বিষয়টি এক পক্ষের হাতে নেই। বরং মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও রাষ্ট্রীয় অস্পষ্টতার কারণে প্রত্যাবাসন মরীচিকা হয়ে যেতে পারে।
একইভাবে পাশের বড় দেশ চীন ও ভারতের ভূমিকা রয়েছে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে। প্রয়োজন আছে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ, নাগরিকত্ব, সম্পত্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণেরও। পাশাপাশি, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি অব্যাহত চাপ এবং আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার দাবি করাও আবশ্যক। সার্বিকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এককভাবে কারও পক্ষে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা এবং তাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য।
-698a65a64ca3e.jpg)
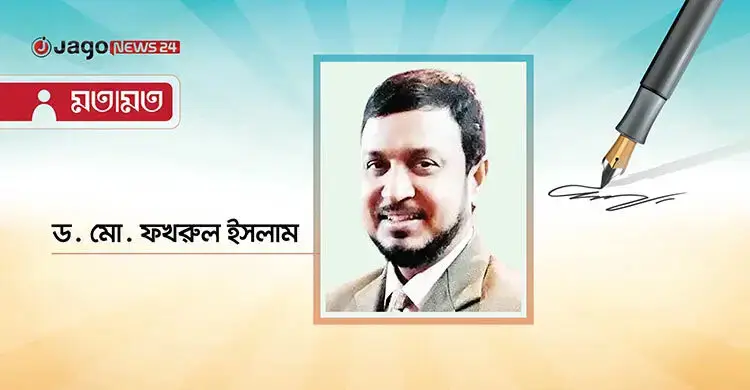
-698a65090f021.jpg)