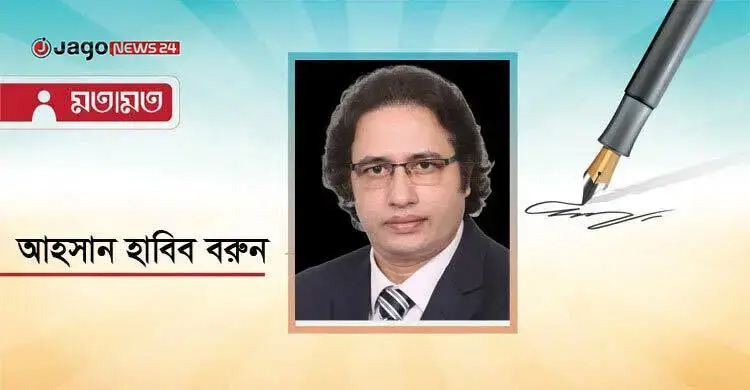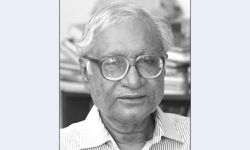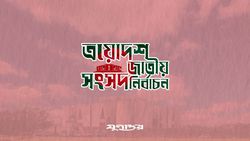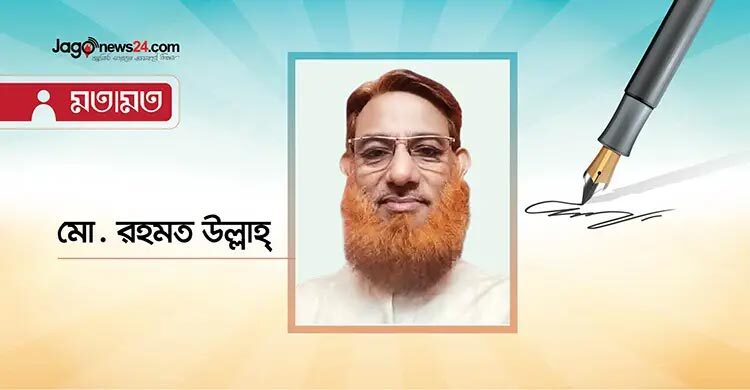বিদেশি ঋণ ‘সহায়তা’, নাকি ব্যবসা সম্প্রসারণের কৌশল
বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর একটি বড় অংশই বিদেশি ঋণনির্ভর। আমাদের দেশে এসব প্রকল্পে ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে ‘দাতা সংস্থা’ এবং প্রদত্ত ঋণকে ‘সহায়তা’ হিসেবে উল্লেখ করার একটি চল রয়েছে। তবে বাস্তবে এসব ঋণের উদ্দেশ্য কতটা গ্রাহক-দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা, আর কতটা ঋণদাতা দেশের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
বিশ্বব্যাংক ও এডিবির মতো বহুপক্ষীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বহুজাতিক করপোরেশনের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যটি সহজে বোঝা যায় না। তবে দ্বিপক্ষীয় ঋণের ক্ষেত্রে কেনাকাটা, পরামর্শক ও ঠিকাদার নিয়োগে বিভিন্ন শর্তের মধ্য দিয়ে মূল উদ্দেশ্যটি আড়ালে থাকে না।
জিন সাতো ও ইয়াশিতামি শিমোমুরা সম্পাদিত দ্য রাইজ অব এশিয়ান ডোনারস (রাউটলেজ, ২০১৩) বই থেকে দেখা যায়, জাপানের বিদেশি ঋণ ও অর্থনৈতিক সহায়তার মূল লক্ষ্য শুরু থেকেই ছিল বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও কাঁচামালের নিরাপদ জোগান নিশ্চিত করা।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায়ও জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তিসহায়তা, ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটা একদিকে জাপানি পণ্যের রপ্তানি বাজার তৈরি করে, অন্যদিকে সস্তা ও নির্ভরযোগ্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করে। এ সহায়তার মাধ্যমে জাপানি কোম্পানিগুলো সরাসরি লাভবান হয়।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাণিজ্যিক স্বার্থ ছাড়াও ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, বিশেষ করে শীতল যুদ্ধের পটভূমিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে। এর অর্থ হলো, অন্য আরও অনেক দেশের মতো জাপানের বিদেশি ঋণনীতি মূলত বাণিজ্য, সম্পদের নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সমন্বিত কৌশল।
দ্য রাইজ অব এশিয়ান ডোনারস বই থেকে দেখা যায়, চীনের বৈদেশিক ঋণ ও সহায়তা শুরুতে আদর্শিক ও ভূরাজনৈতিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ১৯৮০ সালের পর সংস্কারের পর অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিতে মনোযোগী হয়ে ওঠে। অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণের বদলে বেশি গুরুত্ব পায় ‘কনসেশনাল’ লোন, যা সরাসরি চীনা পণ্য ও সেবার সঙ্গে যুক্ত থাকে।
১৯৯৪ সালে এক্সিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই নীতি আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং ‘গোয়িং গ্লোবাল’ কৌশলের অংশ হিসেবে চীনা কোম্পানিগুলোর বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ফলে চীনের বৈদেশিক ঋণনীতি ক্রমে বাণিজ্যিক লাভ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে যায়।
- স্বার্থের সংঘাত ও প্রতিযোগিতাহীনতার ঘটনা শুধু জাপানি ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রেই নয়; চীন, ভারত, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।
- অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত ছিল বিগত সরকারের আমলে নেওয়া বিদেশি ঋণনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পুনর্মূল্যায়ন করা ও সেই সঙ্গে নতুন প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণদাতা সংস্থা নয়, দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া।
প্রশ্ন উঠতে পারে, ঋণদাতা দেশের উদ্বৃত্ত পুঁজি নিজ দেশের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যদি অন্য দেশে নিয়োজিত হয়, তাহলে সমস্যা কোথায়? সাধারণভাবে কোনো দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি অন্য দেশ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়, বরং উভয়ের জন্যই লাভজনক হওয়ার কথা।
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ঋণদাতা দেশের ব্যবসা সম্প্রসারণ অধিক গুরুত্ব পাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণে ঋণগ্রহীতা দেশের স্বার্থের চেয়ে ঋণদাতা দেশের স্বার্থ প্রাধান্য পায়। ঋণের সুদ বেশি হয়, ঋণ পরিশোধের সময়ও কম পাওয়া যায়।
আরও দেখা যায়, যে দেশ ঋণ দিচ্ছে, সেই দেশের সংস্থাই প্রকল্পের পরিকল্পনা করছে, সম্ভাব্যতা যাচাই করছে, পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে, আবার ঠিকাদার হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নও করছে। প্রকল্পের বেশির ভাগ কেনাকাটাও হচ্ছে ঋণদাতা দেশ থেকে। এর ফলে প্রকল্পের লাভ–লোকসান যাচাই যেমন নিরপেক্ষভাবে হয় না, তেমনি প্রকল্পের খরচ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এতে ঋণদাতা দেশের করপোরেশনগুলো লাভবান হলেও প্রকল্পের উচ্চ ব্যয় ও যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই না করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঋণগ্রহীতা দেশের জনগণ।
উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। মেট্রোরেল নির্মাণ করা হচ্ছে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (জাইকা) ঋণে। নির্মাণকাজের দরপত্র দলিল তৈরি ও মূল্যায়নে মূল ভূমিকা পালন করছে জাপানি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিপ্পন কোই। ঋণ ও দরপত্রের শর্ত এমনভাবে দেওয়া হয়, যাতে জাপানি কোম্পানির জন্য কাজ পাওয়া সহজ হয়, যেন অন্য কোনো দেশের কোম্পানি প্রতিযোগিতাই করতে না পারে।