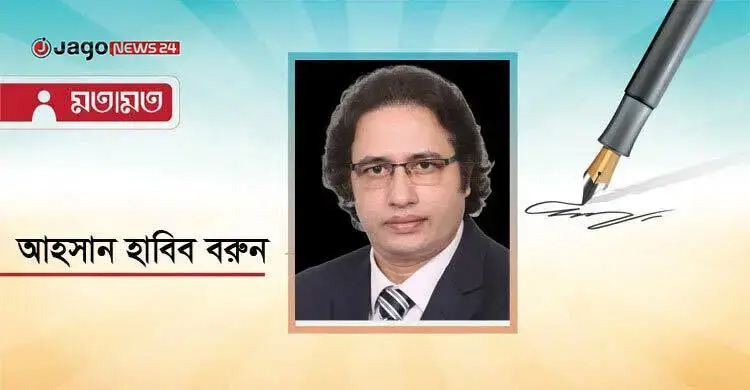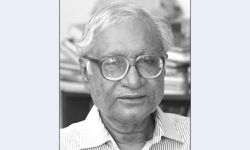প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব আইনকানুন প্রচলিত আছে, তা সঠিক এবং যথাযথভাবে পরিপালনকেই সাধারণভাবে সুশাসন হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়াই প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন। সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানি দুভাবে হতে পারে। প্রথমত, সিদ্ধান্ত প্রদানের যৌক্তিক কারণ ছাড়াই অস্বাভাবিক বিলম্ব করা। দ্বিতীয়ত, সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে কোনো ধরনের ঘুস-দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হয় কিনা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করেন, তাদের দক্ষতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সেবা পাওয়া যায় না। সরকার প্রতি বছর অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এডিপি) বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রতিবারই লক্ষ করা যায়, অর্থবছরের প্রথম ৮-৯ মাসে মোট বরাদ্দের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়। পরের মাসগুলোতে দ্রুত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা দৃশ্যমান থাকে। আর শেষের তিন-চার মাসে মোট এডিপি বরাদ্দের ৭০-৭৫ শতাংশ ব্যয় দেখানো হয়। এভাবে তাড়াহুড়া করে এডিপি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানা ধরনের দুর্নীতি এবং অপচয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সুশাসন প্রত্যাশা করা হয়, প্রায়ই তা লঙ্ঘিত হয়। কাজের মান ঠিক থাকে না। এগুলো সবই সুশাসনের অভাবে ঘটে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা পুরোটা ব্যয় হয় না। আর যেটুকু ব্যয় হয়, তাও সঠিকভাবে ব্যয়িত হয় না। ফলে জনগণের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে যে সুফল পাওয়ার কথা, তা পাচ্ছে না। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা ব্যয় করতে পারাটাই মূল লক্ষ্য নয়। গৃহীত প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হলো, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
যে কোনো উন্নয়ন কর্ম টেকসই ও জবাবদিহিমূলক করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সুশাসনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে অর্থ ব্যয় হবে ঠিকই; কিন্তু উন্নয়ন কাজ গুণগত মানসম্পন্ন ও টেকসই হবে না। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্ম এবং ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সুশাসন নিশ্চিত হলে কোনোভাবেই নিম্নমানের কাজ কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুশাসনের সঙ্গে জবাবদিহিতার প্রশ্নটিও যুক্ত। কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে যদি জবাবদিহিতা না থাকে, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্পাদিত প্রতিটি কাজই নিম্নমানের হতে বাধ্য। এজন্যই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রিওয়ার্ড ও পানিশমেন্টের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ভালো কাজ করেন, তাহলে তাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর কেউ যদি দুর্নীতি-অনাচারে লিপ্ত হন এবং তার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এটা করা হলে প্রতিটি কর্মী ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত হবেন। কোনো দেশই যেনতেনভাবে উন্নয়ন অর্জন করে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তারা সব সময়ই চাইবে অর্জিত উন্নয়ন যেন টেকসই, মানসম্পন্ন এবং স্থিতিশীল হয়।
আমি অর্থ উপদেষ্টা থাকাকালে দুটি জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেছিলাম। আমি চেষ্টা করেছি কীভাবে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ছিল, সেগুলো সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যদিও সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি খুব একটা সহজ নয়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই চাইলেই রাতারাতি সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। তবে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশ্বব্যাংক মাঝেমাঝেই বিভিন্ন দেশের সুশাসনের অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে থাকে। যেমন, বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ ‘ইজ অব ডুয়িং বিজনেস’ সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৬তম। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস সূচক প্রকাশ বন্ধ আছে। এর পরিবর্তে সংস্থাটি ‘বিজনেস রেডি’ নামে একটি নতুন সূচক প্রকাশ করেছে। সেখানে ৫০টি দেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এতে বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অগ্রগতি হয়নি।
বস্তুত বাংলাদেশে বিদ্যমান সুশাসনের অবস্থা মোটেও ভালো নয়। বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর বিভিন্ন দেশের গভর্নেন্স ইন্ডিকেটর প্রকাশ করে, যাতে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ে থাকে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা উন্নয়ন অর্জন করছি, কিন্তু এখনো সুশাসন নিশ্চিত করতে পারিনি। শুধু বিদেশি বিনিয়োগ নয়, স্থানীয় বিনিয়োগও পর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, আমরা কোনো ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সুশাসন নিশ্চিত করতে পারিনি। দেশে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ অনেক দিন ধরেই জিডিপির ২২/২৩ শতাংশে ওঠানামা করছে। বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের ব্যত্যয় ঘটলেই বিনিয়োগকারীরা অন্য দেশে চলে যেতে পারেন। স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা নানা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে নিজ দেশে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হন; কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। তারা কোনো দেশে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ না পেলে অন্য দেশে চলে যান। আমি জাতিসংঘে থাকাকালে বেশকিছু গবেষণা করার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে লক্ষ করি, যে দেশে স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করেন না, সেদেশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশিত মাত্রায় আসে না। স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একটি বার্তা পায় যে, দেশটিতে বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অভাবের কারণেই মূলত আমাদের দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না। স্থানীয় বিনিয়োগকারীরাও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করছেন না। আমরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করি; কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হবে না, যদি দেশে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়। আর বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।