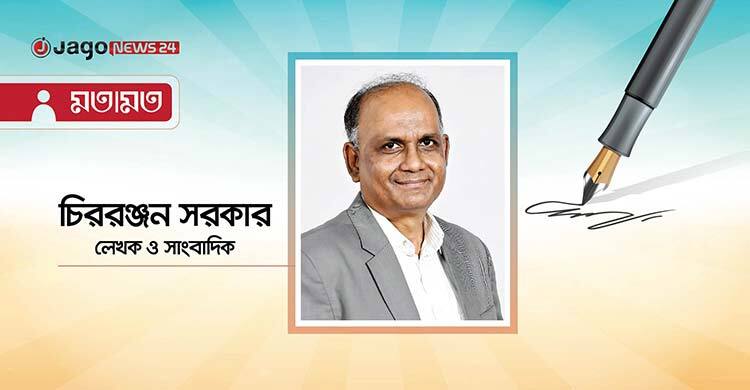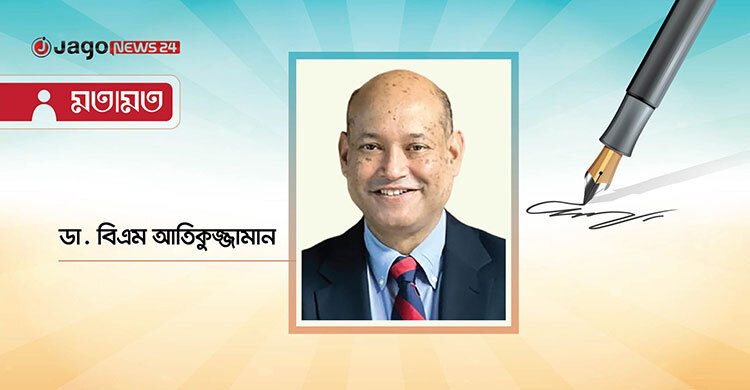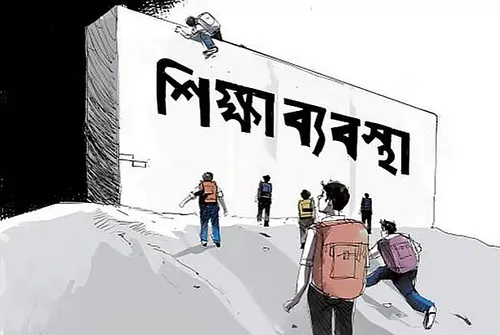
এসএসসি পরীক্ষার প্রয়োজন কতটুকু আছে?
কয়েক দিন আগে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ছয় লাখের বেশি শিক্ষার্থী সেখানে অকৃতকার্য হয়েছে। একটি পাবলিক পরীক্ষায় ১৬ বছর বয়সী প্রতি তিনজনে একজন গড়ে ফেল করলে বা অকৃতকার্য হলেও এ ব্যাপারে আমাদের তেমন কোনো বিকার নেই।
কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, প্রতিবছর বাংলাদেশের গড়ে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের প্রথম ধাপ হিসেবে একসময় এসএসসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
কিন্তু ২০২৫ সালে এসে এই পরীক্ষার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার। কারণ, শুরুতে ও দীর্ঘদিন ধরে এসএসসি পরীক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল, এখন কিন্তু তা আর নেই; বরং এটি শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এসএসসি শুধু একটি পরীক্ষা নয়; এটি শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত মানসিক চাপ, প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংনির্ভরতা এবং মুখস্থনির্ভর পাঠ্যপদ্ধতির প্রতীক। এই প্রক্রিয়া আমাদের নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দিচ্ছে।
বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি একটি পরীক্ষার পেছনে, যার ব্যবহারিক মূল্য এখন ক্ষীয়মাণ; যদি এর পরিবর্তে দক্ষতা, প্রকৃত শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নে বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারত।
ঔপনিবেশিক ভারত ও ‘কেরানি বানানোর শিক্ষা’
ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন পোক্ত হতে শুরু করলে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসন চালানোর জন্য অনেক লোকের দরকার হয়। তখন সব লোককে ইংল্যান্ড থেকে আনাটা সহজ ছিল না। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষানীতিতে তাই একটা মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয় মেকলে মিনিটের (ম্যাকলে মিনিট অন এডুকেশন) আদলে।
থমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁর এই প্রস্তাবে ইংরেজি জানা একটি শ্রেণি গড়ে তোলার কথা বলেন, যারা হবে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগকারী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের এই সাংস্কৃতিক কৌশলের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের জন্য ‘ভারতীয় চেহারার কিন্তু ব্রিটিশ চিন্তার’ জনবল তৈরি করাই ছিল মুখ্য।
এই নীতির ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয় এবং পরীক্ষানির্ভর কাঠামোর সূচনা ঘটে। বলাবাহুল্য, এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার আবশ্যকতাও তৈরি হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গড়া মানেই সেখানে ভর্তির জন্য একটি ‘প্রবেশিকা’ বা যোগ্যতা ঠিক করা দরকার।
‘ম্যাট্রিকুলেশন’ শব্দটা এসেছে লাতিন ভাষা থেকে, যার মানে হলো কোনো তালিকায় নাম লেখানো। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ‘তালিকায় নাম লেখা’। এ জন্য প্রথমবারের মতো ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয় ১৮৫৭ সালে। এরপর এটিই চালু হয়ে যায়।
কিন্তু পরে দেখা যায় যে ম্যাট্রিকুলেশনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে তাদের সরাসরি বিএ ক্লাসে পড়ানো কঠিন। কারণ, বিএ ক্লাসের সিলেবাস আর দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার মধ্যে একটা বড় ফাঁক রয়েছে। তখন একটি ‘মধ্যবর্তী’ বা ‘ইন্টারমিডিয়েট’ ব্যবস্থা চালু করার দরকার হয়।
কাজেই ভারতবর্ষে ফার্স্ট আর্টস (এফএ) বা ইন্টারমিডিয়েট এক্সামিনেশন ইন আর্টস চালু হয় ১৮৫৯ সালে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিন স্তরবিশিষ্ট কাঠামো ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে: প্রথমে ম্যাট্রিকুলেশন, তারপর ইন্টারমিডিয়েট (এফএ) এবং পরিশেষে বিএ বা বিএসসি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- এসএসসি পরীক্ষা