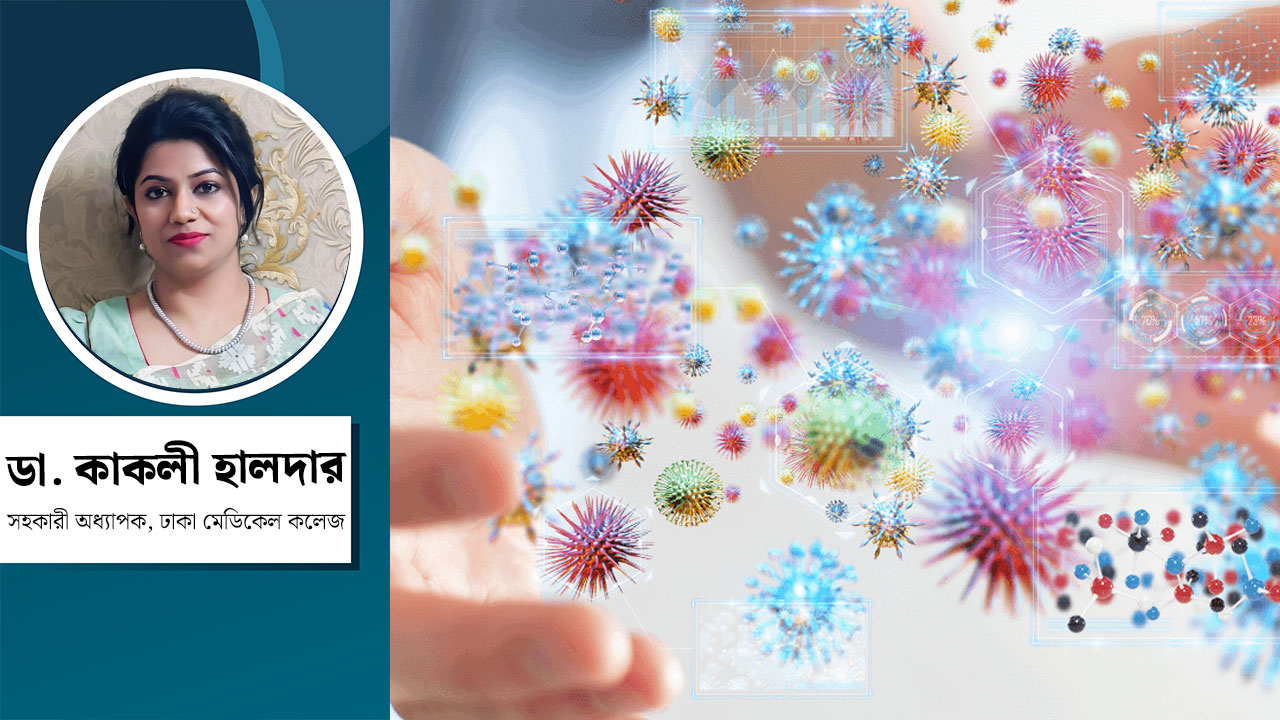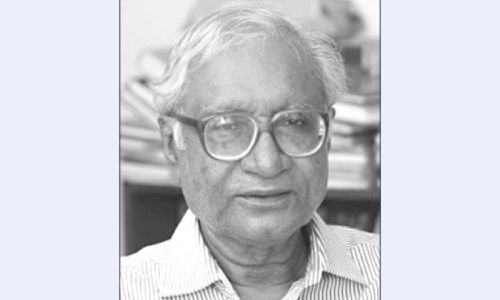
আত্মরক্ষাকে আত্মসমর্পণ মনে হতে পারে
ভাষা কেবল ফেব্রুয়ারি মাসের সমস্যা নয়, সারা বছরেরই। নির্ভয়ে বলা যাবে সমস্যা সে যুগ-যুগান্তরের। কিন্তু তাই বলে ভাষা যে আবার কারো নিজস্ব সম্পত্তি, তা-ও নয়, যদিও কেউ কেউ কখনো কখনো তা মনে রাখে না এবং এমনও আচরণ করে, যেন ভাষা তাদের ঘরের চাকর, যা-তা করবে, যেমন ইচ্ছা খাটাবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা অবশ্যই রয়েছে, থাকা দরকার, আমরা প্রত্যেকেই একেক সময় একেক ভাষা ব্যবহার করি, রাগলে এক প্রকার, শান্ত সময়ে ভিন্ন, ঘরে এক, বাইরে অন্য।
কথা হচ্ছে নিজের ভাষাকে সবার ভাষা করার চেষ্টা। যেমনটা পাকিস্তানি আমলে হয়েছিল। সে সময়ে, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে সরকারি মাহে নও পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, ‘গোজাশত এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল সবাইকে স্বীকার করতেই হবে যে শৈশবেই বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহদের নেক নজরেই পাওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকত হাসিল করেছিল।
’ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিন একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে উদ্ধৃতিটি আবার পড়লাম। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হাসবে নিশ্চয়ই এবং অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করবে এ কথা ভেবে যে এই সম্পাদকীয়কে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কেননা এ তো অত্যন্ত হাস্যকর এবং সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।
এর তো তৎক্ষণাৎ উড়ে যাওয়ার কথা ছিল, যেমন গেছে সে উড়ে—শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ, তাই। হাস্যকর এবং পরিত্যাজ্য বটে।
তবু এর গুরুত্ব অবশ্যই ছিল। এমনিতে মনে হবে যে এটি সম্পাদকের নিজস্ব ভাষা।

তাঁর ব্যক্তিগত ভাষাকে তিনি সর্বজনীন করতে চাইছিলেন। তা চান না কেন, তাতে আসে যায় কী। কত পাগল আছে সংসারে, ছাগলেরও কোনো অভাব নেই। না, ব্যাপারটা অতটা সহজ ছিল না। এ কোনো ব্যক্তিগত ভাষা নয়, চেষ্টা ছিল ওই ভাষাকেই বাংলা ভাষা করার। ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে আপত্তির কোনো কারণ থাকার কথা নয়, যদি তা ঘটে সাহিত্যের প্রয়োজনে। ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বহু লেখক আরবি-ফারসি শব্দের চমৎকার নন্দনতাত্ত্বিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যঙ্গ রচনায়ও এসব শব্দ অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের ঠগচাচা তো বটেই, আমাদের ঘরের কাছের আবুল মনসুর আহমদের ‘হুজুর কেবলা’ পর্যন্ত বহুজনেই মাহে নওয়ের ওই জবানের কাছাকাছি ভাষায় কথা বলেছে। সে নিয়েও কারো আপত্তি নেই। কেননা ব্যাপারটি শৈল্পিক, নন্দনতাত্ত্বিক। মাহে নওয়ের সম্পাদকীয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। সেটিকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না ব্যক্তির রুচিবিকৃতি মনে করে, গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না শৈল্পিক সৃষ্টি হিসেবে। কেননা সমস্ত বিষয়টি ছিল রাজনৈতিক। ওই সম্পাদকীয়ের পেছনে রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল দাঁড়িয়ে। তারই অভিপ্রায় প্রকাশ পাচ্ছিল ওর মধ্য দিয়ে। বিপদ ছিল সেখানেই। গুরুত্বও সে জন্যই।
মনে হতে পারে যে ভাষাকে তখন ইসলামীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি তা-ই। ওই গবেষণা প্রবন্ধেও সেটি বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামীকরণ না বলে পাকিস্তানীকরণ বলাই বোধ করি অধিক সংগত হবে। কেননা তাতে ওই যে রাজনীতির ব্যাপার, সেটি থাকবে সামনে। পাকিস্তানি শাসকরা যে উত্কৃষ্ট ইসলামপন্থী ছিল তা নয়, তারা অতি উত্কৃষ্ট জালেম ছিল, একাত্তরে যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মের নামে ওই খুনিরা তখন নির্বিচারে অসংখ্য ধার্মিক মানুষকে হত্যা করেছে। তাদের সেই খুনের সঙ্গে ধর্ম-কর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ধর্ম ছিল অজুহাত মাত্র। বাঙালির ভাষাকে তারা যদি অবলুপ্ত করে দিতে চেয়ে থাকে, তবে তা এ ভাষা ‘ইসলামবিরোধী’ ছিল বলে নয়, একে নষ্ট করে দিলে বাঙালিদের চিরকালের জন্য পদানত করে রাখতে পারবে মনে করে। অনুপ্রেরণাটি মোটেই ধর্মীয় নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। ওই সম্পাদক যে অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তা মনে করার কারণ নেই, তবে তিনি যে অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি ছিলেন, সেটি নিঃসন্দেহ। তিনি জানতেন কর্তারা কী চান, যা চান তা-ই লিখেছেন এবং লিখে, খুবই সম্ভব, উচ্চতর পদ লাভ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের চাকর, তার বেশি কিছু নয়।
আবুল মনসুর আহমদের কথা উল্লেখ করেছি, তিনি বাংলা ভাষার পক্ষের মানুষ ছিলেন আজীবন, জেল খেটেছেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে। তাঁরও একটি ব্যক্তিগত ভাষা ছিল, সেটি তাঁর এলাকার, ময়মনসিংহের। তা থাকুক, থাকা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু তিনি তাঁর ওই ভাষাকে যখন সাহিত্যের ভাষা করতে চাইলেন এবং তাকে ব্যবহার করে ‘জীবনক্ষুধা’ নামে আস্ত একটি উপন্যাস প্রকাশ করে ফেললেন, তখন অনেকেরই চক্ষু বস্ফািরিত হয়েছিল। ব্যাপারটি কেবল যে ব্যক্তিগত রুচিতাড়িত কিংবা নন্দনতত্ত্বের অনুরোধ-উপজাত ছিল, তা মনে হয় না, যখন দেখি অন্যত্রও এমন ভাষা তিনি ব্যবহার করতে চাইছেন; যাকে অন্য ভালো নামের অভাবে বলা যাবে ‘পাক-বাংলার কালচারী’ ভাষা। ওই নামটি তাঁরই দেওয়া। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তানে, বাংলায় ও কালচারে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ আমরা বাঙালি বটে, কিন্তু আবার পাকিস্তানিও এবং আমাদের সংস্কৃতিতে ইংরেজি উপাদানও ঐতিহাসিক কারণে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের তিন সত্য। তা পাকিস্তানের আমলে অনেকেই নিজেদের একাধারে বাঙালি ও পাকিস্তানি বলে বিশ্বাস করতেন বৈকি এবং যাঁরা নিজের বাঙালিত্ব ভুলে কেবল পাকিস্তানি মনে করতেন নিজেদের, তাঁদের তুলনায় এঁরা যে প্রগতিশীল ছিলেন, তা-ও ইতিহাসের সেই স্তরে সত্য ছিল। নইলে আবুল মনসুর আহমদকে কারাদণ্ড দেওয়া হবে কেন? কিন্তু ওই যে পাক-বাংলার কালচারের ধারণা, ওটি যে একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় আসলে, সেখানেই রয়েছে এর বিশেষ তাৎপর্য।