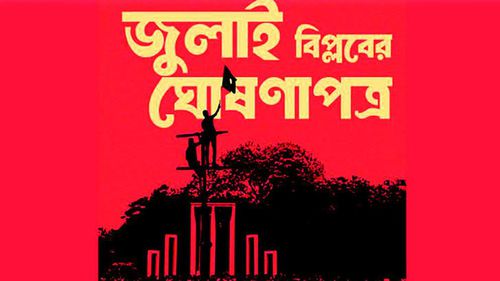
প্রত্যাশা ছিল অনেক, প্রাপ্তিও কম নয়
ছাত্র-জনতার এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মুখে গত বছর ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ইতিহাসের এক নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে শেষ হয় সাড়ে ১৫ বছরের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম এবং স্বপ্ন ছিল বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার-যেখানে নিশ্চিত হবে জনগণের সব নাগরিক অধিকার, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা ও সুশাসন।
আবার জুলাই পেরিয়ে আগস্ট এসেছে। চোখের পলকেই পেরিয়ে গেছে একটি বছর। লিখতে বসে মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন এই টেবিলে বসে থাকা অবস্থায়ই বাসায় র্যাবের গোয়েন্দা শাখা আর ডিবির নজরদারি শুরু হলো। কল আসতে শুরু করল র্যাবের মিডিয়া উইং পরিচয়ে। সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস ফেলে বেরিয়ে পড়লাম পেছনের রাস্তা দিয়ে। ২৪-এর সফল গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দল এবং জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। জনগণের প্রত্যাশা ছিল, এ সরকার হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দায়িত্বশীল। কিন্তু আন্দোলনকে ‘মেটিক্যুলাস ডিজাইন’ হিসাবে তুলে ধরে জনগণের বাস্তব ভূমিকা অস্বীকার করা হয়। অভ্যুত্থানের একক নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব নির্দিষ্ট করতে গিয়ে গণ-আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা সংকুচিত করে ফেলার চেষ্টা হয় সচেতনভাবেই। আন্দোলনের সময় কেউ দেখেনি তার পাশের লোকটা কে? তার রাজনৈতিক পরিচয় কী? তার সামাজিক অবস্থান কী? লিঙ্গ কী, ধর্ম কী? সে গণতন্ত্রের পুনর্জন্মের লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গ করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে এবং পাশের লোকটার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সে মুহূর্তটা আমরা ধরে রাখতে পারিনি। সেই মানুষে মানুষে মিশে যাওয়া, রক্তে রক্তে মিলে যাওয়া-সে সময়টা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সেখান থেকেই প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে ফারাকের শুরু; বছর শেষে যা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর আমাদের প্রত্যাশা এত বেশি যে, এক বছর পর ওটাই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ এ অভ্যুত্থানকে বিপ্লব বলার চেষ্টা করছিলেন। প্রথম সংকট ছিল আন্দোলনের অংশীজনের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা আর দ্বিতীয় সংকট হলো, এ অভ্যুত্থানকে জোর করে বিপ্লব হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কারণ, বিপ্লবের কাছে আমাদের চাওয়া, আমাদের প্রত্যাশা অনেক বড় থাকে। বিপ্লবের পর সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রে খোলনলচেই পালটে যায়। কিন্তু আমরা যদি একে গণ-অভ্যুত্থান হিসাবেই গ্রহণ করতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা কম, কিন্তু সুনির্দিষ্ট থাকত। গণ-অভ্যুত্থানের কাছ থেকে যতটুকু অর্জন করা সম্ভব, আমরা অন্তত অতটুকু অর্জন করতে পারতাম। কেউ কেউ বিপ্লবী সরকার গঠন করতে না পারা, সংবিধান ছুড়ে ফেলে দিতে না পারার ব্যর্থতার কথা বলেন। বাস্তবতা হলো, অভ্যুত্থানের সরকারের ওপরে বিপ্লবের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার কারণে একটা শক্তিশালী সরকারই গঠন করা যায়নি। ফলে গণ-অভ্যুত্থানের কাছ থেকে আমাদের যতটুকু প্রাপ্তি সম্ভব ছিল, ততটুকু পাইনি।
আমরা যখন সংস্কারের আলোচনায় প্রবেশ করলাম, তখন কেউ কেউ অনেক কিছু একসঙ্গে করে ফেলতে চাইল আর আরেক পক্ষ সেই লক্ষ্যকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। সংস্কার প্রশ্নেও দলীয় এজেন্ডা সামনে নিয়ে আসা হলো। সংস্কার এবং নির্বাচনকে পরস্পরবিরোধী এবং পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। এমনকি প্রায় দুই মাস চলা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় দফার সংলাপে অংশ নেওয়া অনেক দলও আলোচনা চলমান অবস্থায় রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ থেকে এ সংলাপ থেকে গৃহীত সনদে স্বাক্ষর না করার হুঁশিয়ারি দেয়। কিছু দল এখন বলছে, সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি ছাড়া তারা অংশ নেবে না। অথচ প্রায় ৬ মাস আগে ঐকমত্য কমিশন কাজ শুরু করার পর থেকে প্রথম পর্বে এমনকি দ্বিতীয় পর্বের সংলাপ শুরুর পরও এ আলোচনা তারা সামনে আনেননি। তারও আগে যখন ১১টি কমিশন গঠিত হয় এবং রিপোর্ট প্রদান করে, তখনো এ ধরনের দাবির প্রসঙ্গ সামনে আসেনি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপ যখনই সফলতার মুখ দেখতে শুরুর করল এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি ঐতিহাসিক জাতীয় সনদের দিকে আমরা অগ্রসর হতে শুরু করলাম, কেউ কেউ ঠিক তখনই এসব বিষয় সামনে আনতে শুরু করল। সংস্কার, বিচার বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক না হলে নির্বাচনে যাব না-এসব দাবি রাজনৈতিক চাপের এজেন্ডা হলে ঠিক আছে; কিন্তু এসব দাবি তুলে কি নির্বাচন আটকে দেওয়া হচ্ছে? এ কথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তি আছে যে, জুলাই অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশকে যে পক্ষ অস্থিতিশীল করে রাখার চেষ্টা করেছে, তারাই এখন নানা যুক্তিতে নির্বাচন বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ তো নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করেছেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার গঠন আবশ্যিক ছিল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা তাকে ছাড়া সম্ভব হতো না। সরকারের দুর্বলতা রয়েছে। শুধু দুর্বলতা নয়, সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ পক্ষপাত দেখিয়েছে। একশর বেশি মাজার ভাঙা হয়েছে, বিভিন্ন ইস্যুতে নারীরা লাঞ্ছিত হয়েছেন, নাটক বন্ধ করা হয়েছে, বাউলগান বন্ধ করা হয়েছে, একজন নারী কীভাবে ওড়না পরবেন বা সিগারেট খাবেন কি না, সেটি নিয়েও কথা হয়েছে। এ ক্ষেত্রগুলোয় সরকার খুব একটা শক্ত অবস্থান নেয়নি। মনে হয়েছে, সরকারের মধ্যে কারও কারও এ নিয়ে এজেন্ডা আছে। তারা হয়তো চেয়েছেন, মাঠের একটি বড় শক্তি হিসাবে দক্ষিণপন্থি এ গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে। জুলাই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা একটি অংশ নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছে যাদের প্রতি সরকারের পক্ষপাত এখন এতটাই প্রকাশ্য যে, কেউ আর এ বিষয়কে অস্বাভাবিক মনে করছে না। এ অংশ থেকেই সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা, তাদের এপিএস, পিও এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সেক্টরে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে এখন দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠে আসছে, কারও কারও বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অভ্যুত্থানের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ বিশেষ অংশের দখলে চলে গেছে। এ প্ল্যাটফর্ম এবং এখান থেকে সৃষ্ট কমিটি এবং দল দুর্নীতির অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, দেশের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য রাজনৈতিক দল এমনকি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও দুর্নীতি, দখলদারিতে মোটামুটি প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- জুলাই ঘোষণাপত্র


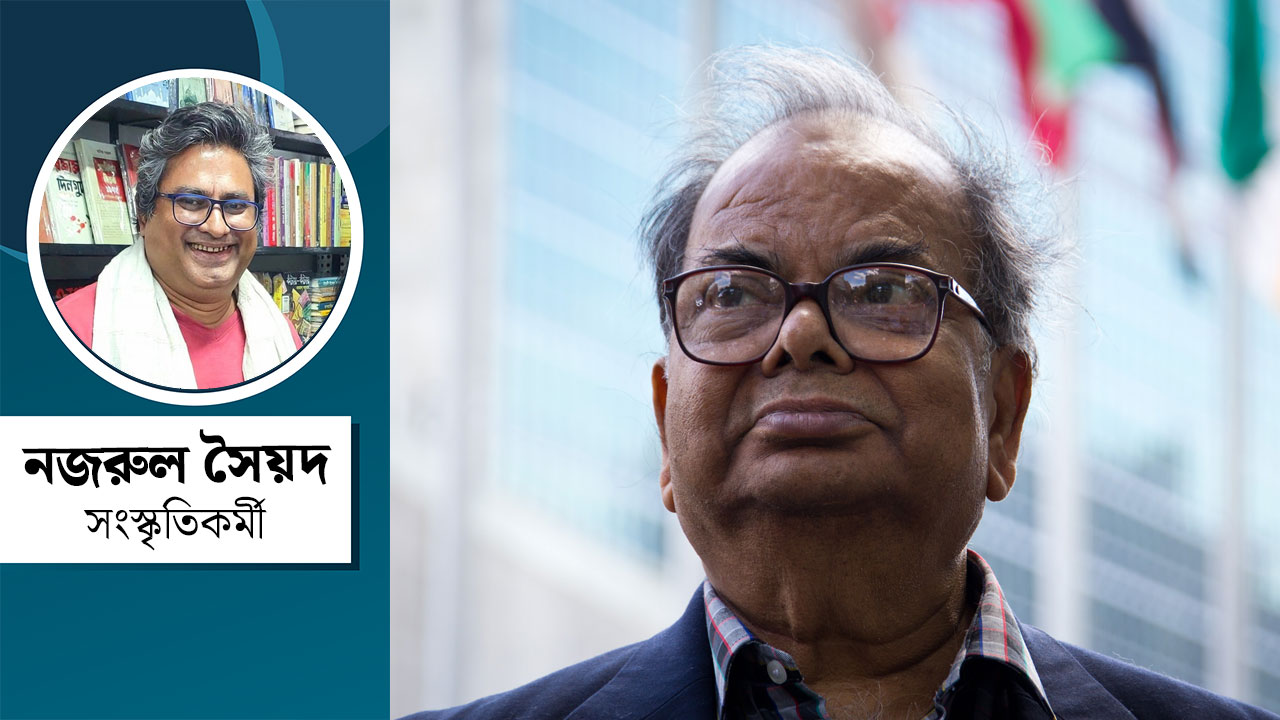
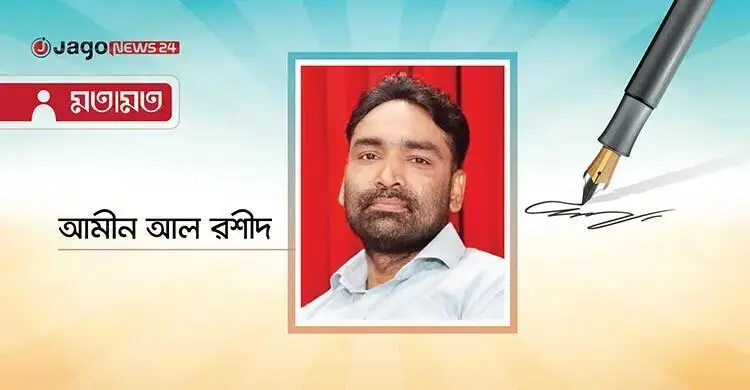

-699b8e6511dac.jpg)

