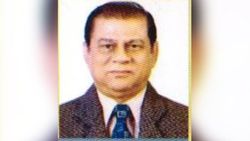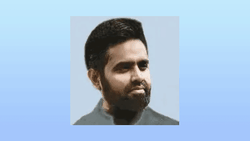উন্নয়ন ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা
‘Development consists of the removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity of exercising their reasoned agency. The removal of substantial unfreedoms, it is argued here, is constitutive of development.’
―Amartya Sen, Development as Freedom বিগত বছর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সাংবাৎসরিক কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল—সংক্ষেপে ‘এবিসিডি কনফারেন্স’। তিন দিনের এই কনফারেন্সে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত সমাজ চিন্তক ও গবেষকদের সমাবেশ ঘটেছিল বিশেষত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণে।
ওই কনফারেন্সে ‘উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা’ শিরোনামে প্রধান বিষয়বস্তু বক্তব্য (কি-নোট স্পিচ) প্রদান করেছিলেন যুক্তরাজ্যের আলসটার ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন অর্থনীতির অধ্যাপক এস আর ওসমানী। বলতে দ্বিধা নেই যে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সঙ্গে অধ্যাপক ওসমানীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সারগ্রাহী বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আমাকে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করেছে।
দুই.
আমরা অবহিত যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে তিনটি দর্শন পথ প্রদর্শন করে। এগুলো হচ্ছে উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা। বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ে তো বটেই, এই দর্শনত্রয়কে হরহামেশা উদগিরণ করে থাকে নীতিনির্ধারক এবং রাজনীতিক মহলও। প্রসঙ্গত স্বীকার করা দরকার যে উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় হাজির হতে পারে এবং তাদের মধ্যকার বিদ্যমান সংযোগটি হয়তো অনুমান করা যায়, কিন্তু সেই সংযোগ স্পষ্টত প্রতীয়মান হতে একটু সময় নেয়।
তবে সন্দেহ নেই যে সংযোগটি আত্মস্থ করার গুরুত্ব অপরিসীম।
প্রথম কথা উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? সাধারণ উপলব্ধিতে উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক ব্যাপার অর্থাৎ মানুষের বস্তুগত জীবনমানের উন্নতিই উন্নয়ন। গেল শতকগুলোতে উন্নয়ন চিন্তকরা এই ধারণা বিপুল পরিশুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তার পরও অদ্যাবধি তা রাজনৈতিক অর্থনীতির অংশ হিসাবেই ধরা হয় (পলিটিক্যাল ইকোনমি)। অন্যদিকে ন্যায়বিচার ন্যস্ত রয়েছে নীতিবিদ্যার অঙ্গ হিসাবে (এথিকস); পক্ষপাতহীনতা এবং অধিকারবোধ ধারণার খুব কাছাকাছি এর অবস্থান।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, ন্যায়ানুগ হওয়া মানে সবাইকে সমান চোখে দেখা এবং অন্যদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। একটি ন্যায়সংগত সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকের অধিকার, স্বাধীনতা, সম্পদ এবং সুযোগ বিতরণে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। মোটকথা, উন্নয়নের এলাকা হলো রাজনৈতিক অর্থনীতি, ন্যায়বিচার বাস করে নীতিশাস্ত্রে এবং স্বাধীনতার রাজ্য রাজনীতি।
তিন.
তবে লক্ষণীয় যে এই তিনটি দর্শন পৃথক বৈশিষ্ট্যময় হলেও এরা একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রথিত, সম্পৃক্ত এবং সংযুক্ত। বস্তুত বিভিন্ন বিন্দুতে তাদের পথের মিলন ঘটে, যার ফলে একটির ওপর অন্যটির বা অন্য দুটির প্রভূত প্রভাব প্রতিফলিত হয়।
এই আন্ত সংযোগের পরিণাম হচ্ছে অন্য দুটির সহায়তা ছাড়া যেকোনো একটি লক্ষ্য অর্জন চরমভাবে অপূর্ণ থাকে। কাজেই কোনো একটি লক্ষ্য অর্জনকল্পে একই সঙ্গে তিনটির দিকে তীর তাক না করতে পারলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উন্নয়নশীল বিশ্বের বেশির ভাগ সরকার সচরাচর যা করে থাকে আমরা যদি সে রকম উন্নয়নকে লক্ষ্যবস্তু করি, তখন আমরা ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার দাবি অবজ্ঞা করতে পারি না। অর্থাৎ যতক্ষণ না ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়, স্বয়ং উন্নয়ন নামক লক্ষ্যটির অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
প্রসঙ্গত উপরোক্ত আলোচনার দুটি ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। প্রথম ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত যুক্তি হচ্ছে এই যে উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা এই তিনটিই মহামূল্যবান লক্ষ্য। সুতরাং এদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাক বা না থাক অথবা কিভাবে সংযুক্ত, সে কথা ভেবে একটিকে অবজ্ঞা করে অন্য দুটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। আমরা সব কটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি বিধায় নিশ্চয়তা চাই যে তিনটিই পূরণ হোক। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় এমনও মনে করা যেতে পারে যে এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধীয় সংযোগ আছে। যেমন আমরা ধরে নেই যে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা উন্নয়ন গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর তাই ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা না গেলে উন্নয়ন নিজেই হোঁচট খাবে। প্রথম ব্যাখ্যানটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি স্বকীয় ব্যাখ্যা (ইনট্রিনসিক ইন্টারপ্রেটেশন) হিসাবে। কারণ কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে এদের প্রত্যেকের স্বকীয় অন্তর্নিহিত গুরুত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে বা কারণীভূত ব্যাখ্যা (ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন্টারপ্রেটেশন) অর্থাৎ আমরা উন্নয়ন সাধনে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। অন্য কথায়, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের কারণে উন্নয়ন ঘটছে বলে ধরে নেওয়া। আবার কিছু সংগত কারণেই দ্বিতীয়টিতে কনসটিটিউটিভ বা গঠনে সহায়ক এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়।
চার.
যা হোক, এই দুই ব্যাখ্যার তফাত শুধু জ্ঞানজাগতিক বা দার্শনিক নিরিখে নয়, বরং অবলম্বিত উন্নয়ন কৌশলের প্রকৃতি বুঝতে পার্থক্যটা খুব ব্যাবহারিক তাৎপর্য বহন করে। যদি কেবল প্রথম ব্যাখ্যা ভর করে অন্তর্নিহিত মূল্যকেন্দ্রিক পথ আলিঙ্গন করা হয়, তাহলে উন্নয়নশীল দেশের কোনো এক সরকার হয়তো উন্নয়নের ওপর প্রাথমিক জোর দিয়ে থেমে থাকবে না, চাই কি তাকে নায়ক বানিয়ে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতাকে পার্শ্বনায়কের চরিত্রের ভূমিকায় ঠেলে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তারা যুক্তি দেখাতে পারে যে তিনটি লক্ষ্য অর্জন সর্বোত্তম, কিন্তু বাস্তব জীবনে একই সময়ে একই সঙ্গে তাদের পাওয়া খুব কঠিন; তাই আপাতত দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা উন্নয়নকে বেছে নিলাম—ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার দিকটি না হয় পরে দেখব। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যানে এমনটি বলার সুযোগ খুব কম। কারণ এই ব্যাখ্যান বলছে, স্বয়ং উন্নয়ন অর্জন করতে হলে আমাদের ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার বিষয়গুলোকে সমান গুরুত্বসহকারে সামনে আনতে হবে; তাদের ‘পরে’ এমন প্রতীক্ষায় রাখা যাবে না, আমাদের তিন ফ্রন্টে একই সময়ে লড়তে হবে। যেমন—ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নকেও সহায়তা দেয়, উন্নয়নের এমন প্রয়োজনীয় উপকরণ পাশে ঠেলে সরকার বলতে পারে না যে আমরা উন্নয়ন আগে করব এবং অবকাঠামো নিয়ে ভাবব পরে। তেমনি করেই যুক্তিতে আসবে না উন্নয়ন আগে, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার পরে। বস্তুত ওসমানীর পুরো উপস্থাপনে এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যানটিতে ছিল মূল মনোযোগ অর্থাৎ কারণীভূত বা ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন্টারপ্রেটেশন।
- ট্যাগ:
- মতামত
- স্বাধীনতা
- ন্যায়বিচার
- উন্নয়নশীল দেশ