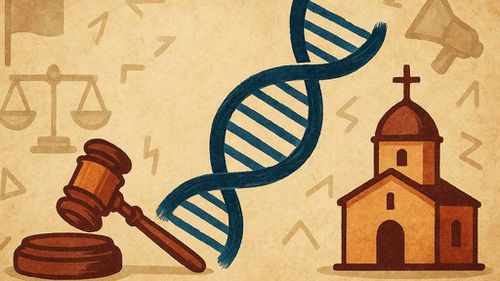
সত্য যাচাইয়ের যুগ: এআই, ভুয়া খবর ও নতুন কুসংস্কারের রাজনীতি
মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই সত্যের সন্ধান করেছে মানুষ। ধর্ম সত্যকে খুঁজেছে বিশ্বাসে, রাজনীতি খুঁজেছে শক্তিতে, আর বিজ্ঞান খুঁজেছে প্রমাণে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সত্য কোনো স্থিতিশীল সত্তা নয়; এটি অ্যালগরিদম, তথ্য ও প্রচারণার জটিল জালে আটকেপড়া। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভুয়া খবর ও তথ্যের রাজনীতি মিলেমিশে তৈরি করেছে এক নতুন বাস্তবতা, যেখানে বাস্তব ও মায়ার পার্থক্য ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত যুগে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, যখন প্রতিটি সত্যই নির্মিত, সম্পাদিত ও বিপণিত, তখন সত্য যাচাই কীভাবে সম্ভব?
তথ্যের এই যুগে প্রযুক্তিকে একসময় ভাবা হয়েছিল গণতন্ত্রের শক্তি হিসেবে। ধারণা ছিল ইন্টারনেট তথ্যকে মুক্ত করবে, মানুষকে বানাবে যুক্তিনির্ভর নাগরিক। কিন্তু বাস্তবচিত্র উল্টো। তথ্য এখন করপোরেট ও রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতে কেন্দ্রীভূত। সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম ঠিক করে দেয় আমরা কী দেখব, কী জানব, কী বিশ্বাস করব। এভাবে জন্মেছে এক ‘সত্য অর্থনীতি’, যেখানে সত্য বিক্রি হয়, বানানো হয়, এমনকি প্রয়োজনে বদলে ফেলা হয়। ফলে তথ্য পরিণত হয়েছে পণ্যে; মানুষ তথ্যের ভোক্তা, পরীক্ষক নয়।
এই তথ্যনির্ভর কৃত্রিম বাস্তবতায় ‘দেখা মানেই সত্য’ ধারণা ভেঙে পড়ছে। একটি এআই-তৈরি ভিডিও বা এডিট করা ছবি এখন বাস্তবের মতোই দেখায়। গবেষণার নামে প্রকাশিত অনেক তথ্য পরে প্রমাণিত হচ্ছে মিথ্যা বা আংশিক সত্য। ফলে জ্ঞান এখন প্রচারণার মতো আচরণ করছে, যেখানে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশে গেছে এবং মানুষ শিখছে যাচাই না করতে। এটি এক নতুন ধরনের ‘ডিজিটাল কুসংস্কার’, যেখানে প্রযুক্তিই হয়ে উঠছে নতুন ধর্ম, আর তথ্য হয়ে উঠছে নতুন বিশ্বাস।
ইতিহাসে ধর্ম, রাজনীতি ও বিজ্ঞান সকলেই সত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু ক্ষমতার ছায়া পড়লেই সত্য বিকৃত হয়েছে। ধর্ম যখন রাজনীতির হাতিয়ার হয়েছে, জন্ম নিয়েছে ধর্মীয় কুসংস্কার; রাজনীতি যখন বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রক হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার। আজ প্রযুক্তি যখন এই তিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায়, তখন গড়ে ওঠে ‘ডিজিটাল কুসংস্কার’, যেখানে অ্যালগরিদম-নির্মিত বাস্তবতাই সত্যের আসনে বসে।
এই প্রেক্ষাপটে সত্য যাচাই আর কেবল একাডেমিক প্রক্রিয়া নয়; এটি সভ্যতার টিকে থাকার শর্ত। নাগরিক যতক্ষণ তথ্য যাচাই করতে পারবে, ততক্ষণই গণতন্ত্র টিকে থাকবে। কিন্তু যাচাই-ক্ষমতা দমে গেলে জন্ম নেয় তথ্য-স্বৈরতন্ত্র—যেখানে রাষ্ট্র, করপোরেট বা প্রযুক্তি ঠিক করে দেয় কোনটি সত্য। তখন রাজনীতি বেছে নেয় সুবিধাজনক তথ্য, বিজ্ঞান নির্ভর হয় তহবিলের ওপরে, ধর্ম নৈতিকতার বদলে পরিচয়ের হাতিয়ার হয় আর প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা করে নীরব নজরদারি শাসন। সত্যের মালিকানা চলে যায় ক্ষমতার হাতে।
এ অবস্থায় দরকার নতুন কাঠামোগত চিন্তার, যেখানে ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও প্রযুক্তি প্রত্যেকের নিজস্ব যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতি থাকবে এবং তারা একে অপরকে প্রশ্ন করতে পারবে। ধর্মকে যাচাই করতে হবে নৈতিকতার ভিত্তিতে, রাজনীতিকে স্বচ্ছতা ও গণসম্মতির ভিত্তিতে; বিজ্ঞানকে পরীক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে, আর প্রযুক্তিকে ন্যায্যতা ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। এভাবেই সত্য বেঁচে থাকতে পারে। একটি পরিণত সমাজে ধর্ম হবে নৈতিকভাবে পরীক্ষণযোগ্য, রাজনীতি হবে তথ্যনির্ভর, বিজ্ঞান হবে স্বতন্ত্র, আর প্রযুক্তি হবে মানবিক নিয়ন্ত্রণাধীন।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ‘দেখা মানেই বিশ্বাস’ আর সত্যের মানদণ্ড নেই। ডিপফেইক ভিডিও, এআই-ভয়েস বা স্বয়ংক্রিয় সংবাদ মানুষের ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত করছে। ২০২৪ সালের বিভিন্ন নির্বাচনে এআই-তৈরি ভুয়া প্রচারণা ভোটারদের বিভ্রান্ত করেছে; এমনকি কিছু বৈজ্ঞানিক জার্নালে এআই-তৈরি ভুয়া গবেষণাও ছাপা হয়েছে। এটি শুধু তথ্যগত ভুল নয়, জ্ঞানের ওপর সরাসরি আঘাত।
এই সংকট থেকে বেরোতে হলে প্রয়োজন দ্বিস্তরীয় যাচাই। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ যাচাই যেখানে একটি ক্ষেত্র নিজেকে নিজেই পরীক্ষা করে; যেমন বিজ্ঞানীরা পরস্পরের গবেষণা পুনরায় যাচাই করেন বা সংবাদমাধ্যমে ফ্যাক্ট-চেকিং দল কাজ করে। দ্বিতীয়ত, আন্তঃক্ষেত্রীয় যাচাই যেখানে এক ক্ষেত্র অন্য ক্ষেত্রকে প্রশ্ন করতে পারে; যেমন প্রযুক্তিনীতির নৈতিক মূল্যায়ন বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ব্যবহার। এই দুই স্তরের যাচাই ছাড়া কোনো সত্যই স্থায়ী নয়।
এই সত্য যাচাইয়ের স্বাধীনতাকে ভবিষ্যতের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যেমন অতীতে বাকস্বাধীনতা ছিল চিন্তার মুক্তির শর্ত, তেমনি আগামীতে যাচাইয়ের স্বাধীনতাই হবে জ্ঞানের মুক্তির শর্ত। কারণ, প্রশ্ন করার অধিকারই মানবজ্ঞানকে সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।







