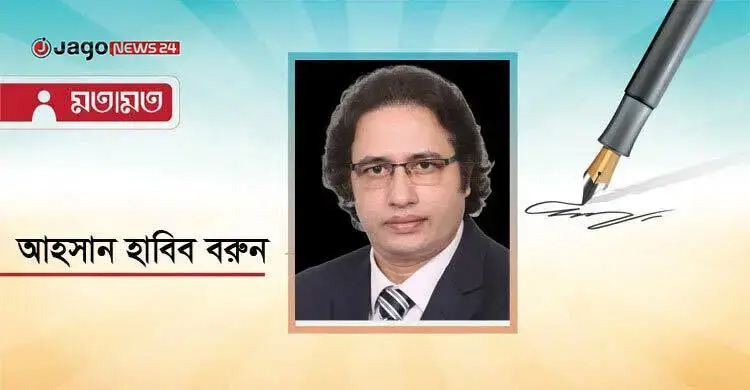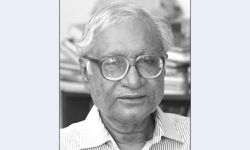বাস্তবতার আলোকেই নির্বাচন হওয়া উচিত
পতিত শেখ হাসিনা সরকারের সর্বশেষ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আউয়াল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তার পদত্যাগের আগে দেওয়া বক্তব্যে দেশের নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সমরূপতার (হোমজিনিটি) পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের বিষয়ে প্রস্তাবনা রেখে যান, যা নিয়ে গত এক বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল এবং সুশীল সমাজে বেশ আলোচনা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের ‘পিআর’ পদ্ধতিতে নির্বাচনে ব্যাপক আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আগামীর নির্বাচন আয়োজন কিছুটা অনিশ্চয়তায় পড়বে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে এ পদ্ধতি আমাদের দেশের আম-জনতার কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।
বিশ্বে বেশ কয়েকটি প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে দেশগুলো তাদের জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচন করে। এখানে প্রধান নির্বাচন পদ্ধতিগুলো তুলে ধরা হলো-১. প্রথম পাস্ট দ্য পোস্ট, ২. আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর পদ্ধতি), ৩. রানঅফ নির্বাচন, ৪. র্যাংকড চয়েস ভোটিং, ৫. মিশ্র নির্বাচন ব্যবস্থা। প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে, যা সেই দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। তবে আমি প্রথম দুটি পদ্ধতি নিয়েই আলাপ করতে চাই। কারণ, প্রথমটি বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, আর দ্বিতীয়টি আগামী নির্বাচনের অনুসরণের জন্য বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রচারণা চলছে।
প্রথম পাস্ট দ্য পোস্ট (ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট) : এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে কাজ করা একটি পদ্ধতি, যেখানে একটি নির্দিষ্ট আসনে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তিনি নির্বাচিত হন। ব্রিটেন, ভারত, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক দেশে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও ওয়েস্ট মিনস্টার পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন হয়ে আসছে। সুবিধা : এ পদ্ধতিতে ভোট গণনা এবং বিজয়ী নির্ধারণ সহজ ও সরল। এ ধরনের নির্বাচনে সাধারণত বৃহৎ দলগুলো জয়ী হয়, ফলে একক দল ক্ষমতায় আসে এবং স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়। এ ছাড়াও নির্বাচিত প্রার্থীর সঙ্গে তার নির্বাচনি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়। এতে ভোটের টার্ন-আউট ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। অসুবিধা : ছোট দল বা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাধারণত এ পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কোনো প্রার্থী নির্বাচনে হারলে তার পক্ষে দেওয়া ভোটগুলো কার্যত বিফলে যায়। ফলে এতে অসম প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ ভোটের সংখ্যা এবং আসনের অনুপাতের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (প্রপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) : এ পদ্ধতিতে দলগুলো প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদে আসন পায়। মূলত দলভিত্তিক নির্বাচনের প্রতীকের ওপর ভোটিং হয় এবং দলগুলো তাদের প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে সংসদ-সদস্য মনোনীত করে। জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইসরাইলসহ বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সুবিধা : এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটের মূল্য থাকে এবং আসন বণ্টনে সঠিক প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা থাকে। ছোট দলগুলো সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায় এবং নানা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব সংসদে থাকে, যা নীতিনির্ধারণে বৈচিত্র্য আনে। অসুবিধা : এ পদ্ধতির নির্বাচনে প্রায়ই কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, ফলে জোট সরকার গঠন করতে হয়, যা স্থিতিশীলতার অভাব তৈরি করতে পারে। এতে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া ধীর হতে পারে, কারণ বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতা প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থী না থাকা এবং দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সংসদ-সদস্যরা সরাসরি এলাকাবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে কম বাধ্য থাকেন।
প্রতিটি নির্বাচন পদ্ধতির নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। প্রথম পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিটি সহজ হলেও গণভোটের অপচয় ঘটায়। আনুপাতিক পদ্ধতি ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে, তবে জোট সরকারের ঝুঁকি বাড়ায়। কোনো পদ্ধতিই এককভাবে নিখুঁত নয়, তবে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সঠিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ।