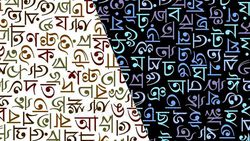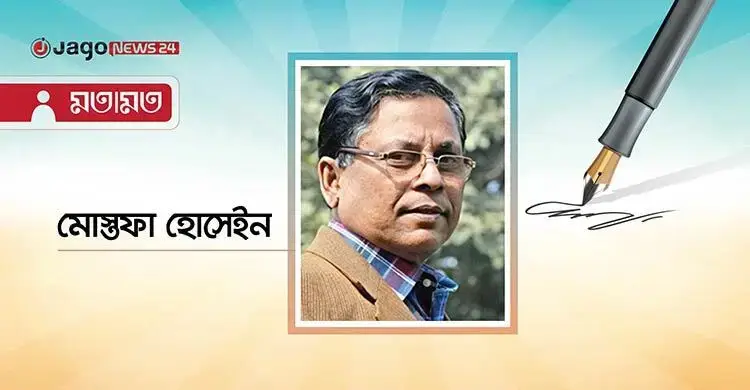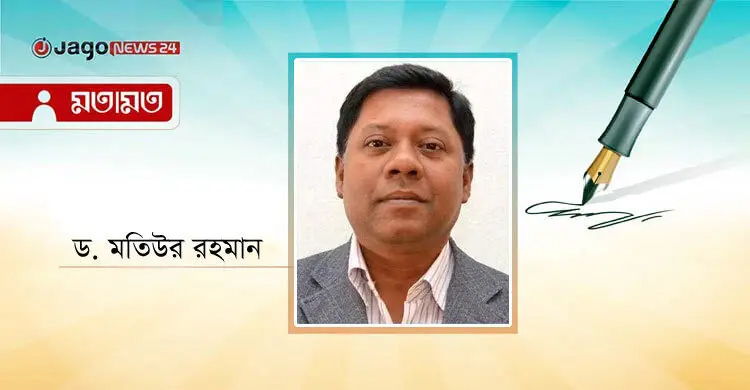‘বেঁচে নেই, জীবিত আছি’
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেসব চিন্তকদের জন্ম হয়েছে যতীন সরকার তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে আগামী প্রজন্মের জন্য পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাতিঘর হয়ে উঠেছেন।
যতীন সরকার গোটা কর্মজীবন ধরেই মার্কসীয় মতাদর্শ অবলোকন করে চলেছেন। তিনি যা কিছু করেছেন তার মধ্যে নিরন্তর সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা গ্রথিত। নিজের সাহিত্যকর্মে তিনি যেমন এই ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি অন্যদের লেখার মধ্যেও তিনি তা অনুসন্ধান করেছেন।
বাংলার লোকসংস্কৃতি তিনি অবলোকন করেছেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে। এরমধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের প্রতিচ্ছবি। খুঁজে পেয়েছেন তাদের জীবন ভাবনার ইতিবাচক দিক। যে কারণে লোকসংস্কৃতির প্রতি তার একটা আলাদা টান অনুভব করতে দেখেছি। বিশ্লেষণ করতে দেখেছি লোকসংস্কৃতির খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ।
তিনি অবশ্য শুধু লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত থাকেননি। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়েও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তার লেখা ও কথাবলায় থাকে তারই প্রতিচ্ছবি ও অকাট্য যুক্তি। তার ‘রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা’ নামক বইয়ের ‘সব সত্য কথাই হক কথা নয়’ প্রবন্ধে দেখেছি ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে বিষয়াবলীর যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপন।
তিনি প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন, ‘নিরেট সত্য কথা হয়েও যদি সেটি নিরপরাধ মানুষের জন্য অকল্যাণ বা অমঙ্গল বলে আনে, তবে সেটি হক কথা হবে না। যে কথা মানুষের জন্য কল্যাণকর, সেকথা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে বা আক্ষরিক অর্থে অসত্য কথাও হয় তবু তা সত্যের মূল মর্ম ধারণ করে বিধায় তা হক কথা।’
এ প্রবন্ধের আরেক অংশে তিনি বলেছেন, ‘সত্য কথা বলা যত সহজ, হক কথা বলা তত সহজ নয়। কোনোরূপ বিচার বিবেচনা ছাড়াই সত্য কথা বলে ফেলা যায়। কিন্তু হক কথা বলতে হলে বিচারবুদ্ধিকে সদা জাগ্রত রাখতে হয়। আপাত সত্যের সঙ্গে প্রকৃত সত্যের পার্থক্যটি স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হয়, মানুষের হক কথা বা মানবাধিকারের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার ক্ষমতা থাকতে হয়। দায়িত্বহীন ব্যক্তিও সত্য কথা বলে ফেলতে পারেন। আর হক কথা বলতে পারেন কেবল দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই।’ আমার মনে হয়, এ কথাগুলোই যতীন সরকারকে পরিচিত করানোর জন্য যথার্থ।
যতীন সরকারের সাথে আমার পরিচয় তার লেখার মাধ্যমে। সম্ভবত ১৯৯৩ সাল। তখন সবেমাত্র বিভিন্ন ঘটনাচক্রে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত গোটা বিশ্ব। সেই উন্মত্ত পৃথিবীর অন্তরালে সোভিয়েতের জনগণের যে ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে থাকে তা তিনি তুলে ধরেন সে সময়ের বহুল প্রচারিত পত্রিকা ‘আজকের কাগজে’। সেখানে তিনি লিখেন—‘সর্বং হন্তি বুবুক্ষতা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ।
প্রবন্ধটি তিনি শুরু করেছিলেন এভাবে যে, ‘যদি কোথাও দর্শনের আলোচনা হতে থাকে, সেখানে যদি কাব্য চর্চা শুরু হয়ে যায় তাহলে দর্শনের আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। কাব্যেন দর্শনাং হন্তি—কাব্য দর্শনকে হত্যা করে। আবার যদি কোথাও কাব্য চর্চা হতে থাকে সেখানে সংগীত চর্চা শুরু করলে কাব্য চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ কাব্য অপেক্ষা সংগীত আরও বেশি চিত্তাকর্ষক আবার কোথাও যদি সংগীত চর্চা হতে থাকে সেখানে নারী বিলাসের আকর্ষণ চলে আসে তাহলে সংগীত চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ সংগীত অপেক্ষা নারী বিলাসে আকর্ষণ আরও বেশি প্রকট। আবার দর্শন, কাব্য, সংগীত, নারী বিলাসের আকর্ষণ শিকেয় ওঠে যদি পেটে ভাত না থাকে। সর্বং হন্তি বুবুক্ষতা। ক্ষুধা সবকিছুকেই হত্যা করে।’
তার পরপর তিনি বলেছেন, সোভিয়েত সরকার সেখানকার জনগণকে ভালো মডেলের একটা ঘড়ি কিংবা ভালোমানের রঙিন পানীয়র ব্যবস্থা হয়তো করতে পারেননি। কিন্তু ইতিপূর্বে এক টুকরো বিড়ালের মাংসের জন্য সেখানকার জনগণকে কামড়াকামড়ি করতে দেখিনি। যা এখন সেখানে বর্তমান।
কী অসাধারণভাবে গল্প-কথায়, উদাহরণে সে সময়ের গোটা সোভিয়েতের চিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন। তাঁর সেদিনের সেই লেখনীই পরবর্তী সময়ে তার প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করে তোলে।
উদীচীর প্রয়োজনে বহুবার যতীনদা’র কাছে লেখা চেয়েছি তখনই তার প্রথম প্রশ্ন থাকত— ‘লেখাটা কখন দিতে হবে?’ যদি কখনো দ্রুততম সময়ে কোনো লেখা চেয়েছি সাথে সাথেই বলে উঠতেন—‘ও অমিত, আমি তো কষ্ট লেখক। এত তাড়াতাড়ি লেখা দিতে পারব না।’
এই কষ্ট লেখক প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বললেন, ‘দ্যাখ আমি জানি আমাকে লেখালেখির মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। আমাকে লিখতেই হবে। আমি এও জানি আমি কবি কিংবা কথাসাহিত্যিক হতে পারব না। সুতরাং, আমাকে প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে হবে। তার জন্য আমাকে পড়াশুনো করতে হবে এবং তারপর লিখতে হবে।’
- ট্যাগ:
- মতামত
- স্মরণ
- যতীন সরকার