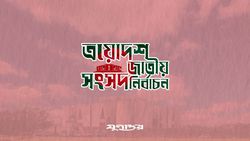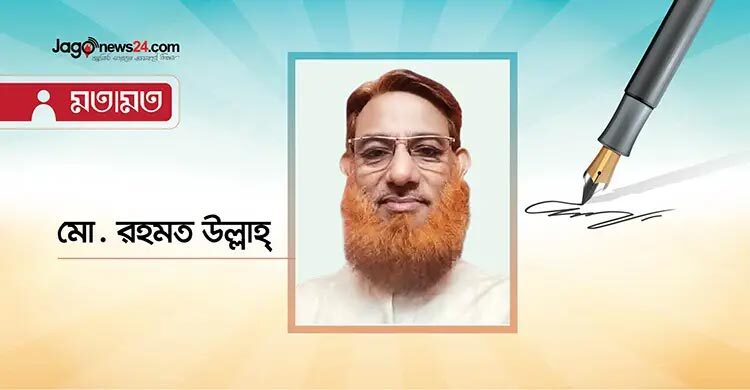‘আলংকারিক’ রাষ্ট্রপতিকে এভাবে ক্ষমতায়নের চেষ্টা নজিরবিহীন
ঐকমত্য কমিশনের দুই মাসব্যাপী টানা আলোচনার সর্বশেষ দিনে (৩১ জুলাই ২০২৫) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি।
ঐকমত্য কমিশন মনে করে, রাষ্ট্রপতির পদটি ‘আলংকারিক’ না থেকে তা ‘ক্ষমতাশালী’ হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদধারীদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতির সরাসরি সিদ্ধান্তে হওয়া প্রয়োজন।
ঐকমত্য কমিশন প্রস্তাব করে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, এনএসআই প্রধান, ডিজিএফআই প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ ১২টি পদে নিয়োগে রাষ্ট্রপতির সরাসরি এখতিয়ার থাকা দরকার।
এ বিষয়ে আলোচনাকালে বিভিন্ন দল বিভিন্নমুখী অবস্থান নেয়। সংসদীয় কাঠামোয় রাষ্ট্রপতির ‘আলংকারিক’ পদকে এভাবে ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা নজিরবিহীন।
রাষ্ট্রপতির এ ধরনের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা নির্বাহী বিভাগ; অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনকাঠামোয় ভারসাম্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। প্রকারান্তরে সংসদীয় কাঠামোয় আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে যা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থাকা প্রয়োজন, এ ধরনের কৃত্রিম ক্ষমতায়ন এর জন্য সহায়ক না হয়ে তাকে ভারসাম্যহীন করতে পারে।
ঐকমত্য কমিশনে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে মূলত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্স’-এর মধ্যে নিয়ে আসার অভিপ্রায় থেকে। এটা সত্য যে পূর্বতন সরকারগুলোর সময় নির্বাহী বিভাগের হাতে যে ক্ষমতা ছিল, তা এককভাবে কুক্ষিগত ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে।
দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদটি আলংকারিক করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর হাতে নির্বাহী বিভাগের সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার একক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কমতে কমতে ঠেকেছিল শূন্যের কোঠায়, রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম পরিচালিত হতো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে।
এই অতিকেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতা এককভাবে হস্তগত হওয়ার কারণে নির্বাহী বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ পদের মনোনয়ন ও পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্তই ছিল। বিগত দশকগুলোয় নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন শীর্ষ পদে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি দলীয় আনুগত্যও নিয়োগপ্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল।
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে মনোনয়ন যোগ্যতা বিচার করার কথা ছিল, তা বিচার্য হয়নি। ফলে এসব মনোনয়ন ও নির্বাচন প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তার চেয়ে বড় কথা, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চেয়ে বিভিন্ন সময় অন্যান্য স্বার্থ অগ্রাধিকার পেয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকার এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধ করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল সীমিত করা, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদীয় কমিটিগুলোর প্রধান নির্বাচন করা, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। প্রস্তাবিত এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহি বাড়বে এবং রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ—আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের ওপর প্রধানমন্ত্রীর অযাচিত প্রভাব কমবে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা