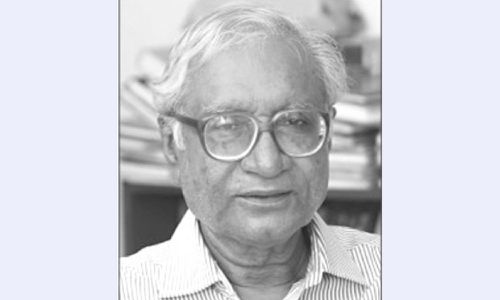
তারুণ্যের কাছে প্রত্যাশা
তাহলে এখন কী করা দরকার আমাদের? দরকার হলো গোটা ব্যবস্থাটাকে বদলানো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা দেওয়ার, তা এরই মধ্যে দিয়ে ফেলেছে, এর পরে সে আর কিছু দিতে পারবে না, ধ্বংস ছাড়া। যাকে আমরা আধুনিক যুগ বলে জানি, সেটি একদিন বের হয়ে এসেছিল সামন্তবাদের অন্ধকার ছিন্ন করে। নতুন যুগের কারিগরদের একজন ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন।
তিনি ছিলেন বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ, তাঁর মৃত্যু ঘটে বৈজ্ঞানিক এক অনুসন্ধান পরিচালনা করতে গিয়ে। বরফের সংরক্ষণশীলতা বিষয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন এবং সেই অসুখেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ বিচারক এবং ওই পদে থাকাকালেই কিন্তু তিনি উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন। অপরাধটি ধরা পড়ে এবং তিনি শাস্তি পর্যন্ত পান।
শুধু তা-ই নয়, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ওই শাস্তি তাঁর প্রাপ্য ছিল। যাকে রেনেসাঁস বলা হয়, আধুনিকতার সেই ধারাপ্রবাহেই পুঁজিবাদের জন্ম এবং পুঁজিবাদের ওই দ্বৈত চেহারা বটে; একদিকে সে জ্ঞানকে মর্যাদা দেয়, অন্যদিকে বেপরোয়া। পুঁজি সংগ্রহ করে পুঁজিবাদ যখন পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহণ করে, তখন তার পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন অভাবিতপূর্ণ উৎকর্ষ অর্জন করতে থাকে, তেমনি এবং ঠিক একইভাবে মুনাফালিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে সে মনুষ্যত্ববিনাশী চরম আচরণ শুরু করে। তার ডান হাত যদি হয় জ্ঞানের, তবে বাঁ হাত অর্থলোলুপতার।
পরিণতিতে দেখা গেছে, অর্থেরই জয় হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চলে গেছে অর্থের অধীনে। এরই মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্য আধুনিক মানুষ সংগ্রাম করেছে; স্বাধীনতার তবু দেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু সাম্য আসেনি, যে জন্য মৈত্রীর পরিবর্তে সংঘাতই প্রধান সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশের অবস্থান প্রান্তিক পুঁজিবাদী; এখানে পুঁজিবাদের গুণগুলো বিকশিত হয়নি, দোষগুলো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার অর্থ তো আত্মসমর্পণ। মানুষ ইতিহাসের মধ্যেই বাস করে, তবে ওই বন্ধনের ভেতরে থেকেও ইতিহাসকে বদলানোর চেষ্টা করে।
এবং ইতিহাস যে বদলায়নি, তা-ও তো নয়। বদলেছে। কিন্তু ব্যক্তির কতটুকু সাধ্য ইতিহাস বদলানোর কাজে লাগে? না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জন্য সে সাধ্য মোটেই নেই। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হলে মানুষ শক্তি অর্জন করে বৈকি। যে তারুণ্য ও জ্ঞান নিয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করছে, তা নিশ্চয়ই দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেককে সচেতন রাখবে। সেই সচেতনতাকে আরো বিকশিত করা এবং তাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া মস্ত বড় একটি কাজ। ব্যবস্থা বদলের জন্য সেটি অত্যাবশ্যকীয়ও বৈকি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিককার সমাবর্তনগুলোর একটিতে ইংরেজ চ্যান্সেলর মন্তব্য করেছিলেন যে শিক্ষার্থীদের যাকেই তিনি জিজ্ঞেস করেন জীবনের লক্ষ্য কী, সে-ই বলে লক্ষ্য সার্ভিস। সার্ভিস বলতে তারা সরকারি চাকরিই বুঝিয়েছে, সার্ভিসের অন্য অর্থ যে সেবা, সেটি তারা খেয়ালে রাখেনি। যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তারা সরকারি চাকরির বদলে বেসরকারি কর্মে যুক্ত হতেই পছন্দ করবে বলে আমাদের ধারণা। অর্থাৎ কিনা চাকুরে নয়, সেবক হতেই চাইবে। সেবাও অবশ্য এখন পরোপকারে উৎসাহী নয়, সে বেচার ও ক্রয়-বিক্রয়ের সমগ্রী হয়ে পড়েছে। শিক্ষা তো ওই পথে আগেই গেছে চলে; চিকিৎসাও একই পথের যাত্রী। তবু এর মধ্যেও সমাজের প্রতি দায়টাকে তরুণরা এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা থাকবে। বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে এখন মানববন্ধন হয় এবং হবেও। বড় রকমের একটি মানববন্ধন, প্রত্যক্ষ শুধু নয়, অপ্রত্যক্ষেও গড়ে ওঠা চাই। সেটি হবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য। এই যুগে সমাজ পরিবর্তনের মূল দাবিটিই হলো সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা। সামাজিক মালিকানাই পারবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, যে গণতন্ত্রের ভিত্তি হওয়া চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং যে সাম্যকে এগিয়ে নেওয়া দরকার মুক্তির অভিমুখে। হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের অগ্রগমন ব্যক্তিমালিকানার অধীনেই ঘটেছে। দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজ পার হয়ে বিশ্ব এসেছে অতি উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, সে ব্যবস্থাও এখন চরম দুর্দশায় নিপতিত। পীড়িত বিশ্বের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, উন্নতির কোন পথে সে এগোবে? ব্যক্তিমালিকানার, নাকি সামাজিক মালিকানার? ব্যক্তিমালিকানার পথটি কিন্তু প্রতারক; সেটি আসলে উন্নতির নয়, পতনের।
- ট্যাগ:
- মতামত
- তারুণ্যের প্রত্যাশা






