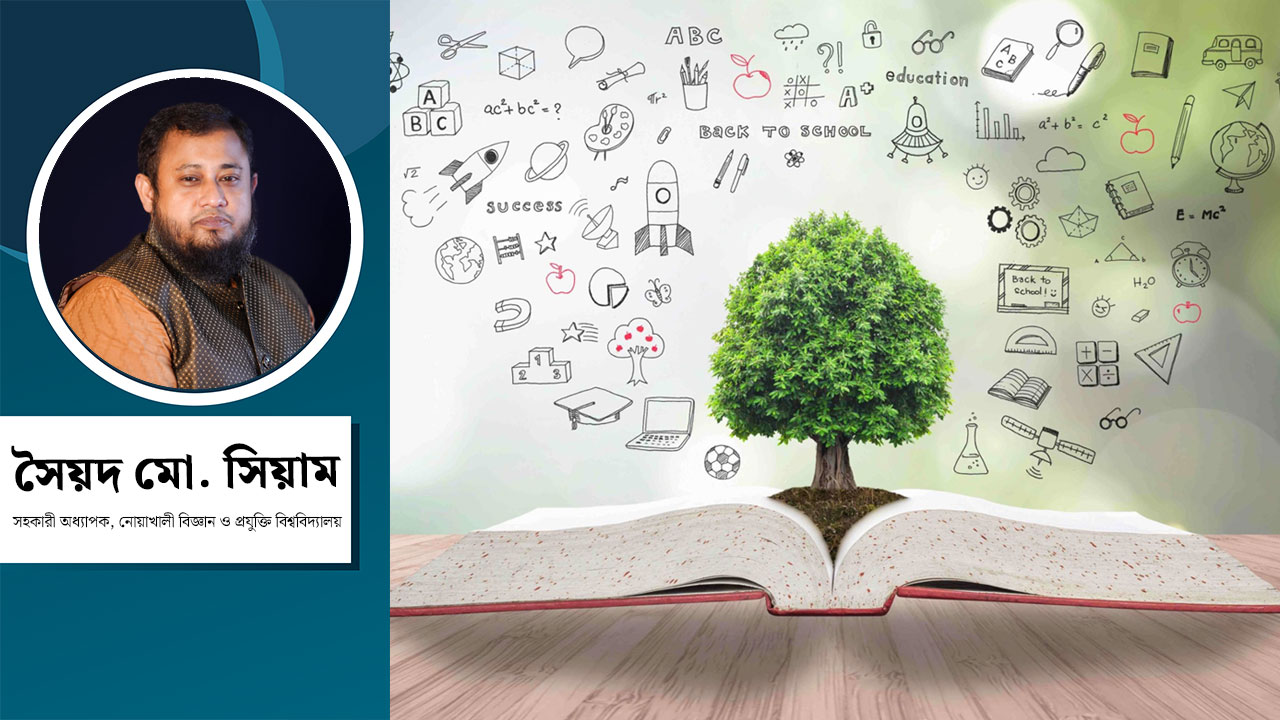মঙ্গল শোভাযাত্রায় অন্তর্ভুক্তির নামে অন্তর্ঘাতমূলক জাত্যভিমান
‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ একটা সংকটে আছে। সংকটটা রাজনৈতিক কারণে যতটা হয়েছে, সাংস্কৃতিক কারণে ততটা হয়নি। সাংস্কৃতিক আধিপত্যটা আগের মতোই রয়ে গেছে। কিন্তু, এই আধিপত্য দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে নাম লেখানো ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদে’র কাছেই শুধু জিম্মি নেই। লক্ষ করলে দেখা যাবে, খোদ এই জাতীয়তাবাদের বাইনারি হিসেবেই এখানে ‘বাঙালিবাদ’ আরও একটি মারণাস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
এই আধিপত্যটা ভাঙার চেষ্টা বাঙালির একাত্তরের পরেই করতে পারা দরকার ছিল। সেটা হয়নি। না হওয়ার দরুণ সেটি পরিচয়বাদিতার জায়গা থেকে রাজনৈতিকভাবে ছিনতাই হয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদীরা এটিকে অবশ্য রাজনৈতিক তকমা দিয়েই খারিজ করতে চাইছেন। কিন্তু, তাতে সংকট বাড়ছে বৈ কমছে না।
‘বাঙালি জাতীয়তাবাদে’র রাজনৈতিক ব্যাটন আওয়ামী লীগের হাতে। ফলে, আওয়ামী লীগ-বিরোধী মাত্রই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যাবেন, এ আর আশ্চর্য কী! কিন্তু, এতেই কি বাঙালিত্বের সাংস্কৃতিক আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে যাবে? যাবে না। কেননা, রাজনৈতিক পরিচিতির ব্র্যাকেটবন্দি ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদে’র বিরোধী পক্ষেরও সিংহভাগ তথা সংখ্যাগুরুর জাতিগত পরিচয় বাঙালি, বিশেষত বাংলাদেশে। ফলে, এই বিরোধীরা যা করেন, সেটিও আসলে সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিয়ানার ‘বাঙালিবাদ’কেই শক্তিশালী করে। এ রাষ্ট্রে এখন ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদে’র সংকট দশার মধ্যেই অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ‘বাঙালিবাদী’ রাজনীতির পাটাতন দিনকেদিন সর্বময় ক্ষমতাধর হয়ে উঠছে।
২.
বাঙালির সংখ্যাগুরু অহমিকা, জাত্যভিমান ও ‘বাঙালিবাদী’ রাজনীতির একটা নিদারুণ উদাহরণ আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্য। বাংলাদেশের পাহাড়ে দীর্ঘকাল ধরে এই জাত্যাভিমানের অগণতান্ত্রিক চর্চা আমরা দেখে আসছি। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসীদের প্রতি যে আগ্রাসন বাঙালি তার সংখ্যাগুরুর অহমিকাবোধ থেকে জন্ম দিয়েছে, তার ভয়ঙ্কর উদাহরণ বাংলাদেশের সংবিধানে আরোপিত ‘অস্বীকৃতি’, যেখানে তাদের পরিচয় ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’।

সাম্প্রতিক সময়ে এই আগ্রাসন খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে এনসিটিবির গ্রাফিতি-কাণ্ডে। পাঠ্যপুস্তকের মলাটে ‘আদিবাসী’ শব্দ-সম্বলিত গ্রাফিতিটি সংযুক্ত করে, তা দঙ্গলের চাপে প্রত্যাহার করে নেওয়ার যে ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছিল, সেটির স্বাভাবিক প্রতিবাদই আদিবাসীসহ আগ্রাসনবিরোধী বিক্ষুব্ধ নাগরিকরা করেছেন। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে গিয়ে যে দানবীয় হামলা আদিবাসীদের ওপর চালিয়েছে একটি উগ্রবাদী সংগঠন, তার অসংখ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু গভীর তলদেশে থাকা উদ্দেশ্যটির একটিই ব্যাখ্যা— বাঙালিবাদী দাপট!
সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন দানবীয় চরিত্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। আবার, এর বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধও আছে। বাংলাদেশেও আছে। কিন্তু, বাংলাদেশে অভ্যুত্থানোত্তর-পর্বে যেটি অপ্রত্যাশিত ছিল, সেটিই বাস্তবে রূপ দিয়েছে দঙ্গলবাজরা, আদিবাসীদের ওপর ওই হামলা চালিয়ে। এই বৈষম্য এক চলমান প্রক্রিয়া। এই বৈষম্যবাদী চরিত্রের বৈচিত্র্যের শেষ নেই যেন!
৩.
বাংলা অঞ্চলে নববর্ষ সমাগত। বাংলাদেশেও ঠিক তাই। পাঠক লক্ষ করুন, এখানে ‘নববর্ষে’র কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, বলা হয়নি ঠিক কোন নববর্ষের ওপর আলো ফেলা হচ্ছে। নানা জাতিগোষ্ঠীর সম্মিলনে এই বাংলাদেশ তথা বাংলা অঞ্চল। কিন্তু, শোরগোল শুধু ‘বাংলা নববর্ষ’ নিয়েই। এর পুরোভাগে রয়েছে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ বনাম ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’র মুখোমুখি বয়ান।
এই বয়ান বহুদিন ধরেই আছে, কিছু চিরায়ত সংস্কৃতিবিরোধী, লোকসংস্কৃতিবিরোধী গোষ্ঠীবাদীদের মধ্যে। কিন্তু, তারা ভুলে যান ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নয়। তথাপি সেই প্রতিষ্ঠান, যার নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘চারুকলা’, তাদের গণআমন্ত্রণে বহু মত-পথের মানুষ এখানে সম্মিলিত হন। যদিও একটি অরাষ্ট্রীয় বা অসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বহু স্বর ও সুরের যৌথ খামারে পরিণত হওয়া এমন আয়োজনকে বিতর্কিত করার প্রয়াস চলমান। আর বিতর্ক যারা তৈরি করেছেন, তারা এ কথাটিও ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলতে পারছেন না যে, ‘মঙ্গল’ নাম নিয়ে তাদের ঠিক সমস্যাটা কোথায়, সমাধানইবা কী? উল্টো সমস্যার কথা বলতে গিয়ে একে ‘সাম্প্রদায়িক’ রং দিয়ে বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন!
এবার সেই বিতর্কে ঘৃতাহুতি দিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বলা ভালো দিয়েছেন খোদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। সরকারি উদ্যোগ তথা মন্ত্রণালয়ের সরকারি বৈঠক বাদেও, ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নানাভাবে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মঙ্গল শোভাযাত্রাকে প্রতিস্থাপন করতে জনসম্মতি আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু, জননিন্দা ও সমালোচনার মুখে নাম পরিবর্তনের কূট-উদ্দেশ্য থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সঙ্গে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ প্রপঞ্চটি যে ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সেই চাপটিও কাজ করে থাকতে পারে।
তবুও, প্রশ্ন থেকে যায়, একটি অসরকারি-অরাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, তা-ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ বা অনুষদের আয়োজনে সরকার কেন হস্তক্ষেপ করতে মরিয়া হয়ে উঠল? কোন অনুপ্রেরণায়? কার বা কাদের প্ররোচনায়? নিজের মনে যা চাইল, ইতিহাসের বাছবিচার না করে তা-ই চাপিয়ে দেওয়ার নাম কি গণতন্ত্র? এজন্য গণমানুষ একটা রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছিল?
- ট্যাগ:
- মতামত
- বাংলা নববর্ষ
- মঙ্গল শোভাযাত্রা


-69890d3d62cc6.jpg)