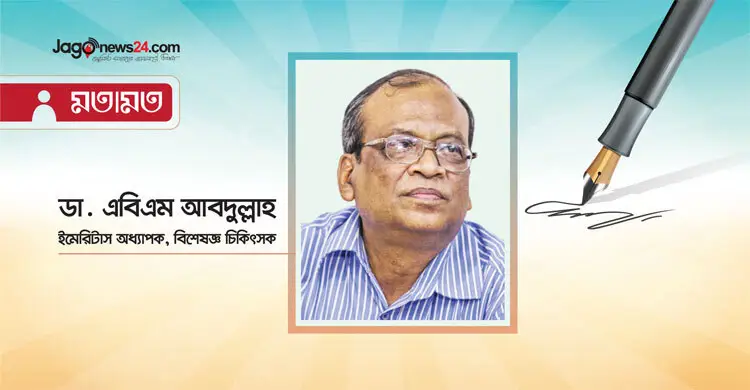মূল্যস্ফীতি কমানো যদি এত সহজ হতো!
আগামী ছয় মাসে মূল্যস্ফীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা দেখার জন্য দেশের সিংহভাগ মানুষ বোধহয় অপেক্ষা করে নেই। দীর্ঘ সময় ধরে যে অভিজ্ঞতা, তাতে কারও আশ্বাসে আস্থা রাখার সুযোগ তাদের আছে বলেও মনে হয় না। মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ে কি না, সে আশঙ্কা নিয়েই তারা আছে বোধহয়। প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে, সেটার পক্ষে বক্তব্য নেই বললেই চলে। মানুষ তো দেখেছে, চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা এক শতাংশ (সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত) বাড়িয়েও মূল্যস্ফীতিকে এর ধারেকাছেও নামানো যায়নি। টানা ১৫ মাস একটা দেশে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের বেশি! প্রকৃত হিসাবে এটা আরও উপরে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বেশি। গরিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্যস্ফীতি হবে আরও বেশি-যে হিসাব করা হচ্ছে না!
মূল্যস্ফীতি কমাতে না পেরে আবার কিছু ‘ভুল তথ্য’ পরিবেশন করা হচ্ছে। সারা দুনিয়াতেই নাকি মূল্যস্ফীতি বেশি! এটা ঠিক, অনেক দেশেই মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল কোভিড থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বের হওয়ার মুহূর্তে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর। জরুরি পণ্যের সরবরাহ কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ব্যাহত হলে এর প্রভাব কত তীব্র হতে পারে, সেটা আমরা তখন দেখেছিলাম। এর সঙ্গে পালটা সামরিক, বাণিজ্যিক পদক্ষেপও সরবরাহ ব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়ে বিশ্ববাজারকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এর বিরাট প্রভাব পড়ে মূলত আমদানিনির্ভর দেশগুলোয়। বাংলাদেশ স্বভাবতই এটা এড়াতে পারেনি। সন্দেহ নেই, এই একক কারণেই এখানে দীর্ঘদিন স্থিতিশীল থাকা মূল্যস্ফীতি বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু বিশ্ববাজারের সেই পরিস্থিতি কি এখনো বিরাজমান? আর ‘ইউক্রেন যুদ্ধের’ প্রভাবে বেড়ে যাওয়া মূল্যস্ফীতি কমাতে কি আমাদের মতোই ব্যর্থ অবস্থায় রয়েছে সবাই? ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত কী বলে? সেটা এই বলে যে, এরই মধ্যে বিশ্ববাজার অনেকখানি স্থিতিশীল হয়ে এসেছে এবং উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত নির্বিশেষে যারাই মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিল, তারা কমবেশি সুফল পেয়েছে। ঘরের কাছে বহুল আলোচিত শ্রীলংকা এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বলে বিবেচিত হবে নিশ্চয়।
ইউক্রেন যুদ্ধসহ বাইরের ঘটনাবলির প্রভাবেই কেবল এখানে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে-এমন একটা বয়ান বহাল রাখার চেষ্টাও লক্ষণীয়। দেশের ভেতরকার ব্যবস্থাপনা যেন পুরোপুরি ঠিক ছিল এবং আছে। কৃষিসহ পণ্য উৎপাদন পরিস্থিতি, সেবার সরবরাহ ও এর বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু অনেক পুরোনো। আজও মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে কোনো একটা পদক্ষেপ নেওয়া হলে প্রশ্ন ওঠে, বাজার ব্যবস্থাপনায় নতুন কী করবেন? প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় কর-শুল্কে ছাড় দিলেও দেখা যায় সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে এবং ভোক্তা এর সুফল পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নিত্যপণ্যের উৎসে কর অর্ধেক ছাড় দিয়েছে, তার সুফল ভোক্তার বদলে ব্যবসায়ীরাই পাবে বলে কথা উঠেছে এরই মধ্যে। এ নিবন্ধ ছাপা হতে হতে কুরবানির পশুর হাট বসতে শুরু করবে। প্রতিবারের মতো বিপুল অর্থের লেনদেন হবে এ খাতে। কিন্তু এর ব্যবস্থাপনাগত গলদগুলো দূর করার কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ কি রয়েছে? গরু-ছাগলের দেশময় সরবরাহটাও কি নির্বিঘ্ন রাখা যাবে? চাঁদাবাজিসহ দুর্বৃত্তদের তৎপরতা রোধ হবে? কুরবানির পশুর পরিবহণ খরচ কমিয়ে রেখে এর বাজার স্বাভাবিক রাখার কোনো উদ্যোগও কি রয়েছে?
এদেশে মূল্যস্ফীতি ঠিক কী কী কারণে বাড়ছে, সেটাও বুঝে ওঠা প্রয়োজন। নইলে এটা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলো যথাযথ হবে না। ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থনীতির দেশে যা সুফল দেয়, সেই পদক্ষেপ একই সুফল নাও দিতে পারে এদেশে। উদাহরণস্বরূপ, সুদের হার বাড়িয়ে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতি কমানোর কৌশলের কথা বলা যায়। এটা যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোয় কার্যকর হলেও বাংলাদেশেও সুফল দেবে, এমন নয়। কারণ এখানে ভোক্তাঋণ খুবই কম। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার চেষ্টায় সে পদক্ষেপও তো নেওয়া হয়নি এখানে। দীর্ঘদিন ব্যাংকঋণের সুদের হার বরং বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাতে ওই সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগ অনেক বেড়ে গিয়েছিল বলেও খবর মেলেনি। বরং বছরের পর বছর বিনিয়োগ একটা জায়গায় আটকে থাকাটাই দেখতে হয়েছে, যা নিয়ে প্রত্যেক বাজেটের আগে-পরে আলোচনা হয়। এবারও হচ্ছে। অনেক দেরিতে সুদের হার বাজারভিত্তিক করার পর এটা যখন বাড়ছে, তখন আবার বিনিয়োগ বাড়বে কীভাবে-এরও কোনো সদুত্তর নেই। অথচ এক্ষেত্রেও একটা বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে!
- ট্যাগ:
- মতামত
- নিয়ন্ত্রণ
- মূল্যস্ফীতি