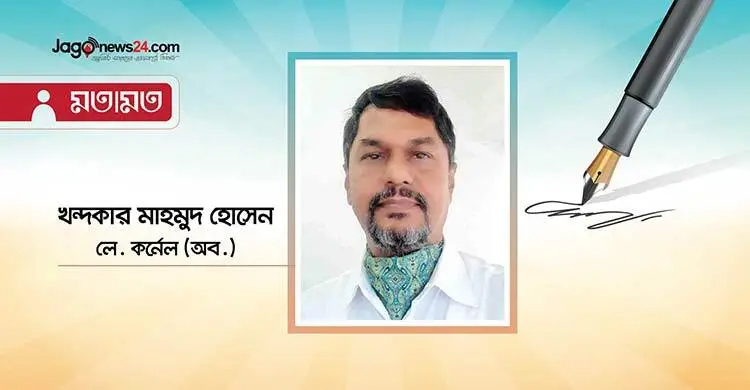
বিদেশি নির্ভরতার কারণ, প্রভাব ও সম্ভাব্য রুপরেখা
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা দীর্ঘদিন ধরেই একটি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন—দেশীয় স্কলারদের রচিত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলা ভাষায় তো নয়ই; ইংরেজি ভাষায়ও খুব কম বাংলাদেশি লেখকের অ্যাকাডেমিক টেক্সটবুক পাওয়া যায়। ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিদেশি লেখকদের বই, বিদেশি উদাহরণ, এবং বিদেশি জ্ঞান কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। প্রশ্ন হলো—কেন এমন হচ্ছে? দেশীয় মেধাবী শিক্ষক-গবেষক কি নেই? নাকি কাঠামোগত কোনো দুর্বলতা রয়েছে?
নিচে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণ, বিদেশি নির্ভরতার ঝুঁকি, গবেষণা বনাম টেক্সটবুকের দ্বন্দ্ব, এবং ভবিষ্যতে দেশীয় বই তৈরির জন্য কী করা দরকার—সেসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করা হলো।
দেশীয় টেক্সটবুকের অভাবের মূল কারণসমূহ
• দুর্বল গবেষণা ইকোসিস্টেম: একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় টেক্সটবুক শিল্প সাধারণত শক্তিশালী হয় যখন দেশটিতে নিয়মিত গবেষণা, আপডেটেড জ্ঞান উৎপাদন, ল্যাব/ফান্ডিং, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইত্যাদি মজবুত থাকে। বাংলাদেশে গবেষণা উৎপাদন, গবেষণার মান, গবেষণাকে সমর্থনকারী কাঠামো, অর্থায়ন, নীতি এবং অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতি—সবকিছুই অপর্যাপ্ত বা কিছু ক্ষেত্রে অকার্যকর। বাংলাদেশে গবেষণা সিস্টেম সীমিত হওয়ায় নতুন জ্ঞান উৎপন্ন হলেও তা টেক্সটবুকে রূপ নেওয়ার মতো শক্তিশালী ইকোসিস্টেম তৈরি হয়নি।
• বই লেখাকে অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে গুরুত্ব না দেওয়াঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদোন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো— SCOPUS/ISI জার্নালে প্রকাশনা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রচনা খুব কম মূল্যায়িত হয়, কখনো গুরুত্বই পায় না। ফলে শিক্ষকরা অগ্রাধিকার প্রবন্ধ, গবেষণা, সেমিনার, কনফারেন্স-কে অগ্রাধিকার দেন। আর টেক্সটবুক লেখার দিকে তাদের ঝোঁক কম হয়।
• শিক্ষক ওভারলোড এবং সময়ের অভাবঃ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককে প্রতি সেমিস্টারে ৩–৫ কোর্স, প্রশাসনিক কাজ, পরীক্ষা/স্ক্রিপ্ট মূল্যায়ন ইত্যাদি সবকিছু সামলাতে হয়। কিন্তু একটি মানসম্পন্ন টেক্সটবুক রচনায় লাগে ১–৩ বছর। বর্তমান কাঠামোতে এত সময় শিক্ষকরা পান না।
• বিদেশি টেক্সটবুকের একচেটিয়া আধিপত্যঃ আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, ভারতীয় বা অন্যান্য বেশ কিছু দেশের লেখকদের বই সহজলভ্য এবং সিলেবাসে “স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স” হিসেবে স্বীকৃত। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই সব বইগুলিকে সফল করার জন্যও অনেক প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি বইয়ের নিরাপদ পথেই থাকতে চান।
• অ্যাকাডেমিক প্রকাশনা শিল্পে পেশাদারিত্বের অভাবঃ প্রকাশনা শিল্পে যথাযথ পিয়ার রিভিউ বোর্ড, অ্যাকাডেমিক সম্পাদক, ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনার বা মান পরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। ফলে টেক্সটবুক তৈরির জন্য পেশাদার প্ল্যাটফর্ম খুবই দুর্বল।
• মানসিক বাধা: 'কে পড়বে বাংলাদেশি বই' ঃ এটি একটি গভীর, কাঠামোগত ও সংস্কৃতিগত মানসিক বাধা। অনেক শিক্ষকই মনে করেন— আন্তর্জাতিক স্তরের মতো বই লেখা কঠিন, বাজার ছোট, ক্লাস নোটই যথেষ্ট ইত্যাদি। এই মানসিকতা পাঠ্যপুস্তক রচনার পথে বড় বাধা। অনেক শিক্ষক-গবেষকের মধ্যে একটি প্রচলিত ধারণা ও মনোভাব রয়েছে যে—“বাংলাদেশি লেখকের বই ছাত্ররা কিনবে না” বা “বিদেশি বই মানেই স্ট্যান্ডার্ড” বা “লোকাল কন্টেন্ট তেমন মূল্যবান নয়।” এই মানসিক বাধার ফলে স্কলাররা বই লিখতে আগ্রহী হন না, গবেষণা দেশীয় জ্ঞানে রূপান্তরিত হয় না, এবং শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশি বইয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
বিদেশী বইগুলি আন্তর্জাতিক মানের হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতির সাথে একইভাবে পথ চলে না। বিদেশি লেখকদের বই বহু দশক ধরে উচ্চশিক্ষার প্রধান উৎস। যেমন McGraw-Hill, Pearson, Oxford, Wiley ইত্যাদি। এই ব্র্যান্ডগুলোর বই দেখতে সুন্দর, মুদ্রণমান উচ্চ, গ্রাফিক্স সমৃদ্ধ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক ও ছাত্র মনে করেন—“এটাই তো স্ট্যান্ডার্ড।” বাংলা/দেশীয় ইংরেজি বইয়ে সাধারণত ডিজাইন, সম্পাদনা, গ্রাফিক্স দুর্বল থাকে। এর ফলে একটি মানসিক তুলনা তৈরি হয়।
এই ধারণা লেখককে বই লেখার আগেই হতাশ করে দেয়। শিক্ষকদের একটা চিন্তার সংকট (cognitive barrier) আছে। যখন তারা দেখেন: বিদেশি লেখকের বইতে ২০–৩০ বছরের গবেষণা, টিমওয়ার্ক, পেশাদার সম্পাদনা রয়েছে কিন্তু তারা বাংলাদেশে তা পান না। দেশে বই লেখাকে সময়, অর্থ, মানসিক সমর্থন—কোনোটিই দেওয়া হয় না। ফলে তারা মনে করেন: “আমি লিখলে বিদেশি বইয়ের তুলনায় দুর্বল হবে।” এই নিজস্বতার সংকট (inferiority mindset) বই লেখার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে, লেখকের বাস্তব চিন্তা হলো, একটা বই লিখতে ১–৩ বছর লাগবে, কত কপিই বা বিক্রি হবে, প্রকাশক খুব কমই রয়্যালটি দেবে, তেমন আর্থিক লাভ নেই। ফলে তারা ভাবেন এত পরিশ্রম করে লাভে নেই বা একেবারেই কম। এমন মনোভাব বই লেখার ইচ্ছাকে হত্যা করে। অনেক শিক্ষক আছেন যারা মনে করেন, ক্লাস নোটই যথেষ্ট। এটা একটি বিপজ্জনক অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- সংকট
- উচ্চ শিক্ষা
- পাঠ্যপুস্তক

