-691b95dac7ad8.jpg)
ইতিহাসে চিরভাস্বর এক অগ্নিপুরুষ
উনিশ শতকের শেষভাগে এ উপমহাদেশে অনন্য প্রতিভার অধিকারী যে মুষ্টিমেয় ক্ষণজন্মা পুরুষ নিঃস্ব-নির্যাতিত, সর্বহারা মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৭ নভেম্বর ছিল তার ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৭৬ সালের এ দিনে তৎকালীন ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে দাফন করা হয়। মওলানা ভাসানী তার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন। অধিকারবঞ্চিত, অবহেলিত ও মেহনতি মানুষের অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় আজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। জাতীয় সংকটে জনগণের পাশে থেকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি দেশে ও জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বার্থকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন বরাবর। ক্ষমতার কাছে থাকলেও ক্ষমতার মোহ তাকে কখনো আবিষ্ট করতে পারেনি। শোষণ ও বঞ্চনাহীন, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে মওলানা ভাসানী সংগ্রাম করে গেছেন। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থরক্ষায় ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করেছেন, সাতচল্লিশের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন একইভাবে সোচ্চার। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এদেশের অধিকারবঞ্চিত মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রতিটি ঐতিহাসিক আন্দোলন সংগঠনে মওলানা ভাসানী ছিলেন অন্যতম অগ্রপথিক। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, এমনকি একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলনে অপরিসীম অবদান উল্লেখ করার মতো। মওলানা ভাসানীই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন। ১৯৫৭ সালের সেই কাগমারীর সম্মেলনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে তার সেই বহুল আলোচিত ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলার মাধ্যমে মওলানা ভাসানীই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা প্রথম উচ্চারণ করেন, যা ইতিহাসে স্বীকৃত।
মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন মহাত্মা গান্ধীর মতোই নিজ মাতৃভূমির বাইরে থেকে শুরু হয়েছিল। গান্ধী যেমন ১৮৯৩ সালে আইন ব্যবসার উদ্দেশে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। মওলানা ভাসানীও তেমন ১৮৯৭ সালে আসামে গিয়ে সেখানকার অধিকারবঞ্চিত বাঙালির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯০৩ সাল থেকেই তিনি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে থেকে স্বরাজ্য পার্টি গঠনে ভূমিকা রাখেন। সেসময় আসাম সরকারের কুখ্যাত ‘লাইন প্রথা’ আইনের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আন্তর্জাতিকভাবে একজন কৃষক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন যেমন আসামের বিজেপি সরকার, অন্যায় ও অন্যায্য বিধিব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে; সে সময়েও বাঙালিদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অমানবিক আচরণ করা হতো। ১৯২০ সালে আসাম সরকার বাঙালি বসতি বিস্তার রোধে ভৌগোলিকভাবে একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিল, যাতে ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুররা নির্ধারিত সীমানার বাইরে যেতে না পারে। আসাম সরকারের এ অমানবিক ব্যবস্থাই কুখ্যাত ‘লাইন প্রথা’ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪০ সালে তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ‘অহম জাতীয় মহাসভা’র উসকানিতে আসাম থেকে ‘বাঙ্গাল খেদা’র নামে বাঙালি উচ্ছেদ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেও মওলানা ভাসানী সোচ্চার হন এবং আসাম সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। ফলে ভাসানীর নেতৃত্বে আয়োজিত সভা-সমিতির ওপর আসাম সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিরাপত্তা আইনে তাকে একাধিকবার গ্রেফতারও করা হয়। তারপরও তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান। একই সঙ্গে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও যুক্ত হন। বাংলা ও আসামকে তিনি পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ৬-৭ জুলাই, সিলেটের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত গণভোটেও ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলায় ফিরে এলেও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃত্ব থেকে তাকে দূরে রাখা হয়। ফলে মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। এরই মধ্যে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে থাকে। বাংলার মানুষের প্রতি তাদের অব্যাহত উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণে অস্বীকৃতি এবং বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে দলের যুব সদস্য ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিম লীগের ক্ষুব্ধ সদস্যরা ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। মওলানা ভাসানী হন সে দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ভাসানী এরই মধ্যে বাংলা ভাষা আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দম্ভোক্তির পর কিছুদিন পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেও বায়ান্নর জানুয়ারিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পরপর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তারপর থেকেই দেশব্যাপী ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠায়; তার পরের ইতিহাস তো সবারই জানা আছে।
মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন। এর মধ্যে তার অবিস্মরণীয় কীর্তি ১৯৫৭ সালের ‘কাগমারী সম্মেলন’। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর তাৎপর্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। মওলানা ভাসানী যখন কাগমারী সম্মেলনে আয়োজন করেন, তখন তারই প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ওই সময়ে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে বিশেষ করে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিসহ বাগদাদ চুক্তি, পূর্ব এশিয়া সামরিক চুক্তির প্রশ্নে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মতদ্বৈততা চরম আকার ধারণ করে বলে সম্মেলনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ নিয়ে সৃষ্ট অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে এ সম্মেলনের আয়োজন পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানী ইতঃপূর্বে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়সহ পাকিস্তানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য ২১ দফা দাবির রূপায়ণে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এ কর্মসূচি নিয়েও তাদের ভেতর একধরনের ভয় কাজ করছিল। কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী তার ভাষণের একপর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে তার সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত ‘আসসালামু আলাইকুম’ উচ্চারণ করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ ‘আসসালামু আলাইকুম’ উচ্চারণের তাৎপর্য হলো, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও ত্যাগের সংকল্পও ওই উচ্চারণের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের পর ভাসানী ও তার সমর্থকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান এবং তাদের সহকর্মীদের ও সমর্থকদের সঙ্গে নীতির প্রশ্নে আপসের সুযোগ ছিল না। তারা বলেছিলেন, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন তো হয়েই গেছে এবং মার্কিনপন্থি জোটভুক্ত পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলেও সোহরাওয়ার্দীর অনীহা ছিল। শেখ মুজিবও ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর পক্ষের লোক। এসব প্রশ্নে ভাসানী ছিলেন অবিচল ও আপসহীন। সোহরাওয়ার্দী সমর্থক পত্রপত্রিকাগুলোও কাগমারী সম্মেলনে নিয়ে পরোক্ষভাবে বিরূপ সমালোচনা শুরু করে। এমতাবস্থায় সম্মেলনের মাত্র স্বল্পসময়ের মাথায় মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন।



-698a648f3096f.jpg)
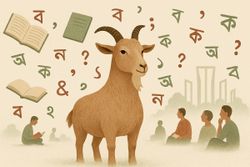

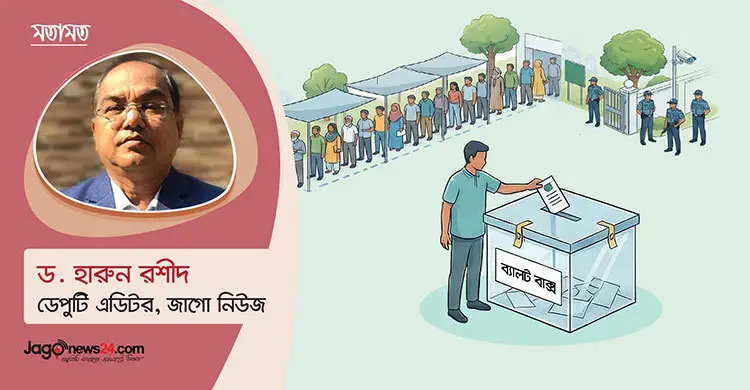

-698a65a64ca3e.jpg)
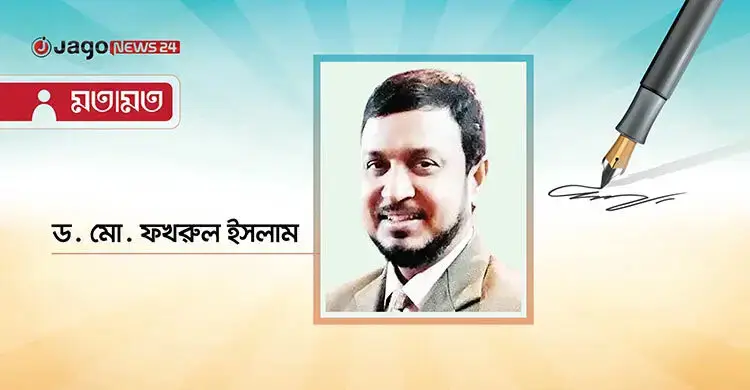
-698a65090f021.jpg)