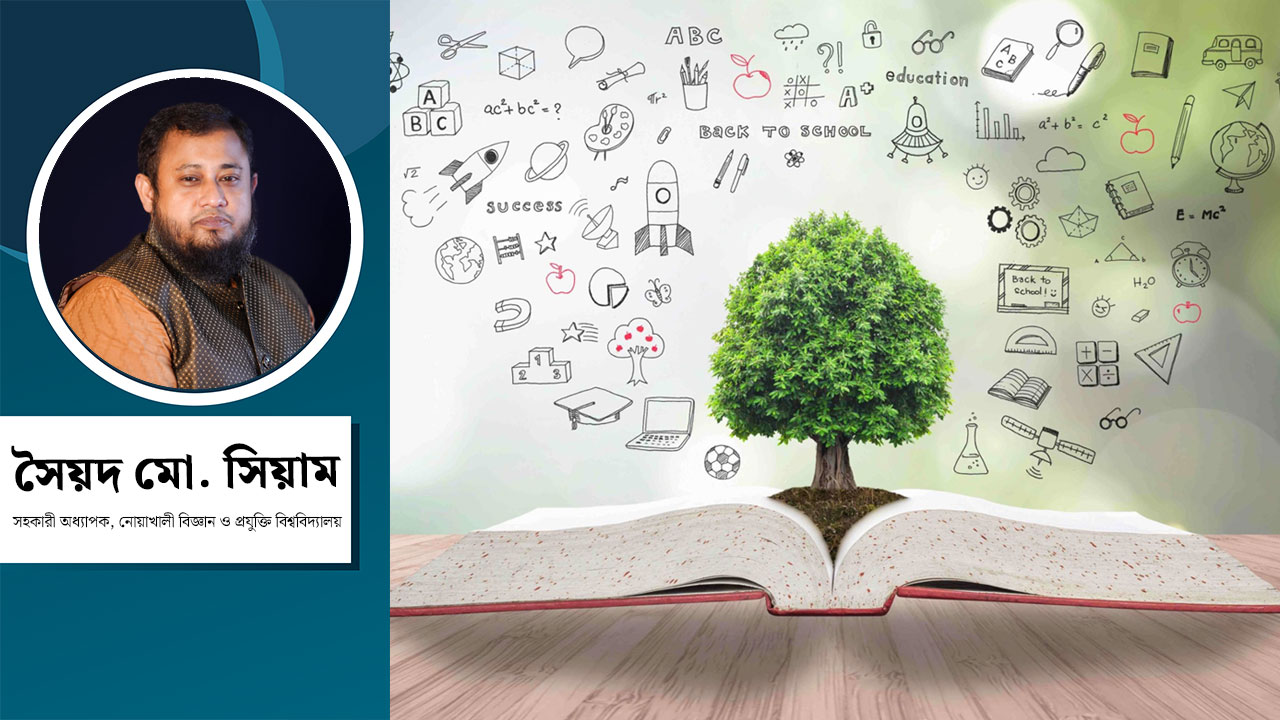লাইক সংস্কৃতির যুগে মানবিকতার সংকট
‘লাইক’ এখন শুধু একটা বাটনে ক্লিক করা নয়—এটা সময়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই ছোট্ট ক্লিকটাই যেন ঠিক করে দেয় কে কতটা জনপ্রিয়, কার কথা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এবং কে কতটা দেখনসই হয়েছে। অর্থনীতিরও এক অদৃশ্য ইঞ্জিন এই লাইক। তাই এখন দরকার, লাইক সংস্কৃতির এই দুনিয়া নিয়ে খোলামেলা কথা বলা, এর আলো-অন্ধকার, তরুণদের মানসিক প্রভাব, ইনফ্লুয়েন্সার সংস্কৃতি আর এই ক্লিকচালিত অর্থনীতির আড়ালের গল্পগুলো নিয়ে বোঝাপড়া করা। লাইক সংস্কৃতিটাকে কেবল প্রযুক্তির নয়, সমাজবিজ্ঞানের চোখে দেখতে হবে। সহজ স্বীকৃতির নেশায় আমরা ঠিক কী কী হারাচ্ছি তার হিসেব মেলাতে হবে এখনই।
মানুষ সব সময় স্বীকৃতি চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক। আগেকার দিনে এই স্বীকৃতি পেতে সময় ও আন্তরিক সম্পর্কের প্রয়োজন হত। এখন এক ক্লিকেই তা পাওয়ার আনন্দে বিভোর বহু মানুষ। মস্তিষ্ক যখন এই স্বীকৃতির সংকেত পায়, তখন ডোপামিন নিঃসৃত হয়, যা থেকে মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি জন্মায়। এই তাত্ক্ষণিক সুখের প্রতিক্রিয়া বারবার পুনরাবৃত্ত করতে চায় মন। ফলে লাইকের নেশা তৈরি হয়। আমরা নোটিফিকেশন চেক করি বারবার। করতে কৃত্রিম পৃথিবীতে ঢুকে পড়ি। চারপাশের বাস্তবতা মনোযোগ ছিন্ন হয়। ধীরে ধীরে অফলাইনের প্রাকৃতিক আনন্দগুলো হারাতে শুরু করি। এভাবে যখন ডিজিটাল স্বীকৃতিকে নিজের মূল্যায়নের মাপকাঠি বানাই, তখন আমাদের আত্মপরিচয় আলগরিদমের দখলে চলে যায়।
লাইকের সংখ্যা আজ সামাজিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। একটি পোস্টে যত বেশি লাইক, সেটি তত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। ব্যস্ত জীবনে যখন মানুষ দীর্ঘ মন্তব্যের সময় পায় না, তখন লাইকই হয়ে ওঠে প্রশংসার সংকেত। এই সংকেতের অর্থনৈতিক মূল্যও বেশ ভালো। কারণ প্রতিটি ক্লিক, থামা বা স্ক্রল বিজ্ঞাপন ও ডেটা-নির্ভর মনোযোগ অর্থনীতির জ্বালানি। প্ল্যাটফর্মগুলো তাই ব্যবহারকারীর সময় ধরে রাখার জন্য ক্রমাগত এমন কনটেন্ট দেখায় যা তার পছন্দের সঙ্গে মিলে যায়। যত বেশি সময় আপনি থাকবেন তত বেশি লাভ তাদের। এই অ্যালগরিদমচক্রই আমাদের মনোযোগকে বন্দি রাখে।
এর ফলে জন্ম নেয় মানসিক চাপ। কম লাইক পেলে অনেকেই হীনম্মন্যতায় ভোগে। রীতিমতন নিজের মূল্য নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। মানুষ আলগরিদমে খাপ খাওয়াতে গিয়ে স্বাভাবিকতা হারায়। জীবনের সাধারণ মুহূর্তগুলোর চেয়ে পোস্টযোগ্য মুহূর্তের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাস্তবের কষ্ট, ব্যর্থতা বা সংগ্রাম লুকিয়ে দেখানো হয় এক সাজানো জীবন। অন্যরা সেই সাজানো-গোছানো জীবন দেখে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে—তাদের মনে জন্ম নেয় ঈর্ষা।
বাংলাদেশে এই প্রবণতা খুব দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে ১৬ থেকে ২৪ বছরের তরুণ প্রজন্ম প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটিয়ে দিচ্ছে। ‘আরও একটু দেখি’ ভেবে ফোন হাতে নিয়ে বয়স্করাও নোটিফিকেশননির্ভর অভ্যাস আর উদ্দেশ্যহীন স্ক্রলিংয়ে রাতের ঘুম হারাম দিচ্ছেন। এর কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। নেটওয়ার্ক তৈরি করা, নতুন কিছু শেখা, ব্যবসা ও সৃজনশীল উদ্যোগে নিজেকে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু ক্ষতির দিকও অনেক। পড়াশোনায় মনোযোগ কমে। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।
সোশ্যাল মিডিয়া শুধুই খারাপ—এমনটা নয়। এখানেই মানুষ রক্তদাতা খুঁজে পায়, সহমর্মিতার হাত বাড়ায়, ব্যবসা শুরু করে, শিক্ষা ও সচেতনতার পথ খুঁজে নেয়। সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা আর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি না বরং প্রযুক্তিই আমাদের ব্যবহার করে। অ্যালগরিদম যখন আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে তখন সেটি আশীর্বাদ থেকে এক সময় ফাঁদে পরিণত হয়।
রাজনীতির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব গভীর। জনপ্রিয়তা-নির্ভর অ্যালগরিদম তথ্যের গুণের চেয়ে আকর্ষণকেই অগ্রাধিকার দেয়। ফলে তৈরি হয় ‘ইকো চেম্বার’, যেখানে মানুষ শুধু নিজের মতো মতামতই দেখতে পায়। মতভেদ কমে না বরং বাড়ে। এই অবস্থায় তথ্য বিকৃতি, গুজব ও অপপ্রচার আরও দ্রুত ছড়ায়।
ইনফ্লুয়েন্সার অর্থনীতি এই বাস্তবতাকে আরও জটিল করেছে। বেশি ফলোয়ার মানে বেশি প্রভাব, আর প্রভাব মানে বিজ্ঞাপন ও আয়। এতে আপত্তি নেই, কিন্তু প্রভাবের সঙ্গে দায়িত্বও থাকা উচিত। যখন মনোযোগ কাড়ার প্রতিযোগিতায় সত্য, সৌজন্য ও সম্মান হারিয়ে যায়, তখন তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। অনলাইন নয়, অফলাইনে আনন্দ খুঁজে নিতে—বই পড়া, ব্যায়াম, আড্ডা বা স্বেচ্ছাসেবার মতো অভ্যাসগুলোর চর্চা রাখতে হবে।
শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায়—লাইক কি ভালো, না খারাপ? আমার মতে, এটি ভালো বা খারাপ কোনোটিই নয় বরং এটি নির্ভর করে আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর। এটি যোগাযোগের দ্রুত উপায় হতে পারে, আবার আসক্তির কারণও হতে পারে। তাই প্রয়োজন ভারসাম্য। এটি একই সঙ্গে যোগাযোগের শক্তি, অর্থনীতির চালিকা শক্তি, আবার মানসিক চাপের কারণও। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তির ব্যবহার নিজের হাতে রাখা, যাতে সেটি আমাদের না চালায়, আমরা সেটিকে চালাবার সক্ষমতা অর্জন করি। যদি আমরা প্রযুক্তিকে বুঝে ব্যবহার করি, নিজের সময়ের নিয়ন্ত্রণ রাখি এবং বাস্তবজীবনের সুখে প্রত্যাবর্তন করতে পারি, তাহলে এই ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।


-69890d3d62cc6.jpg)