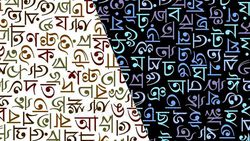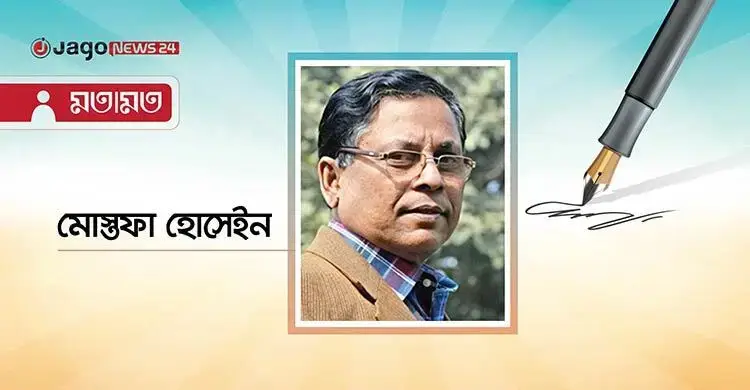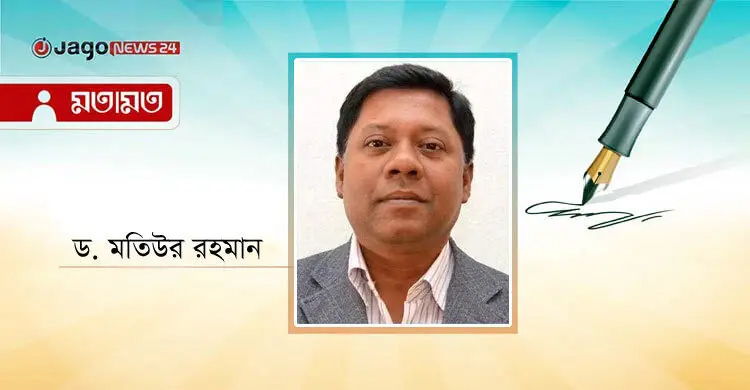কৃষি খাতে উৎপাদন দক্ষতা ও পুঁজির সঞ্চার
‘স্মল ইজ বিউটিফুল’। ছোটই সুন্দর। ছোট শিশুদের মতো সুন্দর, ঝামেলাহীন। জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ই এফ সুমাখারের শিক্ষক লিওপোন্ড কোর (১৯০৯-৯৪) ‘বড় হলে ভালো’-এ মূলধারার নীতির একটি বিকল্প হিসেবে ছোট, উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ওই শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন সুমাখার। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদ প্রচলিত সংস্কৃতির অবনতির বিনিময়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। তার বিশ্বাস হলো বৃহৎ শিল্প ও বৃহৎ শহরগুলো সম্পদের অবক্ষয় উসকে দেয়। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কথা বলেছেন। পরিবেশ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ইন্টারমিডিয়েট টেকনোলজি বা মধ্যবর্তী প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে জোরালোভাবে মতামত উপস্থাপন করেছেন। ১৯৬৫ সালে সুমাখার ও আরো কয়েকজন পরিবেশবিদ লন্ডনে ইন্টারমিডিয়েট টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।
কৃষি খাতে সুমাখারের ‘ছোট ভালো’ তত্ত্ব অনেকটা খাপ খেয়ে যায়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে একটি অভিমত জোরালো হয়ে ওঠে যে ছোট কৃষি খামারগুলো অধিক উৎপাদনশীল। ১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিচালিত খামারভিত্তিক সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়ে যে খামারের আকার ও উৎপাদনের মধ্যে ‘ইনভার্স রিলেশনশিপ’ বা নেতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ খামারের আকার বৃদ্ধি পেলে প্রতি ইউনিট উৎপাদন হ্রাস পায়। অমর্ত্য কুমার সেন (১৯৬২ ও ১৯৬৪) এ প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেন কৃষি শ্রমিকভিত্তিক যুক্তি দিয়ে। ছোট খামারগুলোয় পারিবারিক শ্রমিকের সরবরাহ বেশি। তারা নিবিড়ভাবে শ্রম দিয়ে প্রতি ইউনিট জমিতে অধিক ফসল ফলায়। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ধারণের পর ‘শ্রমিকভিত্তিক যুক্তি’ অনেকটা ফিকে হয়ে আসে। কৃষি অর্থনীতির গবেষকরা খুঁজে পান এক ধরনের ‘পজিটিভ রিলেশনশিপ’ বা ইতিবাচক সম্পর্ক। অর্থাৎ খামারের আকার বৃদ্ধি পেলে প্রতি ইউনিট জমিতে ফসলের উৎপাদন বেড়ে যায়। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে পরিচালিত খামারভিত্তিক সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে অপেক্ষাকৃত বড় খামারগুলোয় আধুনিক কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি হয় এবং তাতে প্রতি ইউনিট জমিতে বেশি ফসল পাওয়া যায়। বড় খামারের মালিকদের আর্থিক সক্ষমতা বেশি। তারা উৎপাদনের আধুনিক উপকরণ বেশি প্রয়োগ করেন এবং বেশি ফসল পান। ঝন ডব্লিউ মেলর (১৯৬৯) এবং কে গ্রিফিন (১৯৭৪) এ মতবাদের বড় প্রবক্তা। বাংলাদেশে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত বড় খামারের উৎপাদন দক্ষতার বিষয়ে অনেক সমীক্ষার ফলাফল আছে। তবে মাঝারি খামারের উৎপাদন দক্ষতা বিষয়ে নজির বেশি। এ খামারগুলো চাষাবাদে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আধুনিক উপকরণ প্রয়োগ করতে পারে। কৃষি শ্রমিকের ব্যবহারও পর্যাপ্ত। খামার ব্যবস্থাপনায় এরা দক্ষ। তাই এরা অধিক ফসল ফলায়। ১৯৭৪ সালে ময়মনসিংহে এবং ১৯৮২ সালে অন্যান্য এলাকায় পরিচালিত আমার সমীক্ষা থেকে এমন ফলাফল পাওয়া যায়।
পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে খামারের আকার বড়। ছোট খামারগুলো জমি বিক্রি করে যোগ দিয়েছে কৃষিবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে, শিল্পে ও সেবামূলক খাতে। বড় খামারগুলো যন্ত্রনির্ভর। আধুনিক চাষাবাদ সেখানে উৎপাদন দক্ষতা নিশ্চিত করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে খামারের আকার উল্টো পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বড় ও মাঝারি খামারগুলো ভেঙে ছোট হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারের সংখ্যা বাড়ছে। মূলত উত্তরাধিকার আইনে জমি বিভাজন হচ্ছে। তাছাড়া কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও নিট আয় কমে যাওয়ার কারণে বড় কৃষকরা তাদের কিয়দংশ জমি বিক্রি করে পরিণত হচ্ছেন ছোট কৃষকে। ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এক ধরনের প্রাকৃতিক ভূমি সংস্কার আমরা লক্ষ করছি। বর্তমানে প্রায় ৯২ শতাংশ কৃষকই ছোট। বড় ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা মাত্র ৮ শতাংশ। ছোট কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রায় ৬৯ শতাংশ জমি। ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বড় খামারগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা জমি কমেছে ৪৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। মাঝারি খামারগুলো খুইয়েছে ৩৬ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ জমি। পক্ষান্তরে ছোট খামারগুলো ৩২ দশমিক ২৪ শতাংশ জমি বেশি দখলে নিয়েছে। তাদের সংখ্যা বেড়েছে ৮৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ থেকে ৯১ দশমিক ৭০ শতাংশে। অন্যদিকে মাঝারি খামারগুলোর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ১৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ৭০ শতাংশে এবং বড় খামারগুলোর সংখ্যা কমেছে ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ থেকে দশমিক ৬০ শতাংশে। উৎপাদনের দক্ষতা ও আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের বিচারে খামারের আকৃতির এ স্খলন সম্ভাবনাময় কিছু নয়। তাতে কৃষি যান্ত্রিকীরণ ব্যাহত হতে পারে। খামারগুলোর আকার ছোট থেকে ছোট হওয়া কৃষিজমির চরম অভাবই প্রকাশ পায়। এ দেশে ভূমি দারিদ্র্য প্রকট। সময়ের ব্যবধানে তা বাড়ছে। ১৯৭৪ সালে গড় খামারের আকার ছিল ২ দশমিক ৮ একর। ২০০৮ সালে তা ১ দশমিক ৪৭ একরে এবং ২০১৯ সালে ১ দশমিক ২৯ একরে হ্রাস পায়। বর্তমানে জনপ্রতি জমির পরিমাণ গড়ে মাত্র দশমিক ১১ একর।
কৃষিজমির মালিকানার ধরনের যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি কৃষি খাতের গঠনেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। কৃষি খাতের উপখাতগুলো হচ্ছে শস্য, মৎস্য, পশুসম্পদ ও বনসম্পদ। অধিকালে উপখাতগুলোর ভার ও গুরুত্বের অনেক তারতম্য ঘটেছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষি খাতের মোট উৎপাদনে ফসল কৃষি খাতের শরিকানা ছিল ৭৭ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। মৎস্য, পশুসম্পদ ও বনসম্পদের শরিকানা ছিল যথাক্রমে ৯ দশমিক ৯৩, ৭ দশমিক ৫৪ ও ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এখন তা পরিবর্তন হয়ে ফসল খাত নেমে এসেছে ৪৬ দশমিক ৯২ শতাংশে। মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ও বনসম্পদের বেলায় তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২১ দশমিক ৬৬, ১৬ দশমিক ৩৮ ও ১৫ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশে। শস্যবহির্ভূত কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বেশি। বাণিজ্যিকীকরণের গতি ভালো। চাষকৃত মৎস্য খামারগুলোয় আধুনিকায়ন, বাণিজ্যিক দুগ্ধ এবং পোলট্রি খামারের উন্নয়ন এবং কৃষি বনায়ন সম্প্রসারণের ফলে শস্যবহির্ভূত কৃষি খাতের শরিকানা বাড়ছে। এক্ষেত্রে উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের প্রতি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদনে মুনাফার হার বেশি থাকায় উল্লিখিত উপখাতগুলোর উৎপাদন দ্রুত বাড়ছে। অন্যদিকে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি অনেকটা স্থির হয়ে আছে ২-৩ শতাংশের আশপাশে। তাছাড়া শস্য খাতে পুঁজির বিকাশ সীমিত। আধুনিকায়নের গতি মন্থর। এখন পুরো খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পুঁজির সঞ্চার।
কৃষি খাতে পুঁজি সঞ্চারের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি ঋণ। এবার কৃষি ঋণের মোট পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩৯ হাজার কোটি টাকা। গত বছর ছিল ৩৮ হাজার কোটি টাকা। বিতরণ করা হয়েছিল ৩৭ হাজার ৩২৬ কোটি টাকা। এটি ছিল লক্ষ্যমাত্রার ৯৮ দশমিক ২৩ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবার কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। দেশে মূল্যস্ফীতির হার যেখানে ন্যূনপক্ষে ছিল ৯ শতাংশ, সেখানে কৃষি ঋণের প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ খুবই অপ্রতুল। বর্তমানে দেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লাখ ৮১ হাজার ৭৫৭। গত অর্থবছরে কৃষি ঋণ পেয়েছে ৩৮ লাখ ১৯ হাজার ৫৯১টি পরিবার। তাতে দেখা যায় যে মাত্র ২২ দশমিক ৬৩ শতাংশ কৃষি পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আওতায় এসেছে। বাকিরা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছে অথবা প্রয়োজনীয় পুঁজির সংস্থান ছাড়াই চাষাবাদ করছে। এবার কৃষি ঋণ নীতিতে মোট ঋণের ৫৫ শতাংশ শস্য উৎপাদন খাতে, ২ শতাংশ সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে, ২০ শতাংশ প্রাণিসম্পদ খাতে, ১৩ শতাংশ মৎস্য খাতে এবং ১০ শতাংশ পল্লী অঞ্চলের উৎপাদন ও সেবা খাতসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। এ হার মোট কৃষি জিডিপিতে সংশ্লিষ্ট উপখাতের হিস্যা অনুসারে নির্ধারণ করা উচিত। ডাল, তৈলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল ও ভুট্টা উৎপাদনের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তাতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো যে মুনাফা লোকসান দেবে তা ভর্তুকি হিসেবে পূরণ করে দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোর আগ্রহ খুবই কম। গত বছর মোট বিতরণকৃত ঋণের ১ শতাংশেরও কম অর্থাৎ দশমিক ৭৫ শতাংশ ঋণ রেয়াতি সুদহারে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকগুলো যে কৃষি ঋণ দেয় তার সিংহভাগ যায় বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে। তাতে সুদহার বেশি। অনেক ঋণ চলে যায় কৃষিবহির্ভূত গ্রামীণ সেবা খাতে। ফলে অধিকাংশ কৃষি খামার তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় যথাযথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে না। তাতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পায় না।