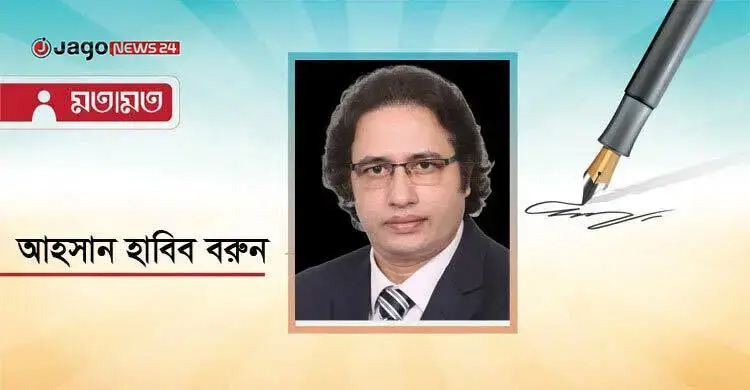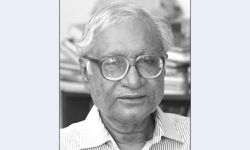কর্পোরেট সিন্ডিকেট ও আমাদের ভাতের দাম
চালের দাম বাড়ানো এখন যেন কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সহজ আয়ের কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য ভাতের দাম বাড়ছে।
কেজি প্রতি চালে মাত্র ১ টাকা দাম বাড়ালেই প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ তুলতে পারে এই কর্পোরেটরা—এমনই হিসেব দিয়েছেন ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সংগঠন ক্যাবের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসাইন। যদিও এই হিসেব অনুমাননির্ভর, তবু বাজারের বাস্তবতা এটিকে অস্বীকার করে না।
আমরা এমন এক বাজারে বাস করছি, যেখানে সরকারের মজুদ পর্যাপ্ত, উৎপাদন ও আমদানি স্বাভাবিক, আর আন্তর্জাতিক বাজারে গত আট বছরের মধ্যে চালের দাম সবচেয়ে কম। তবুও দেশে চালের দাম বাড়ছে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই। এর মানে স্পষ্ট—কিছু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যে হাত দিচ্ছে। আর এই প্রক্রিয়ায় লাভের পাহাড় গড়ছে কর্পোরেট ও বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী।
এ প্রশ্নটাই বড়—যখন খাদ্য নিরাপত্তা ও ভোক্তা সুরক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তখন এমন বাজার কারসাজি ঠেকাতে আমরা আসলে কতটা সক্ষম বা কতটা ইচ্ছুক?
টিসিবির হিসেবই প্রমাণ করছে, বাজারে চালের দাম কেমন করে ক্রমাগত বেড়েছে। গত বছরের অগাস্টের শুরুতে চিকন চালের দাম ছিল কেজিতে ৭৮ টাকা; এক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৮৫ টাকা। মাঝারি মানের চাল, যা সবচেয়ে বেশি মানুষের খাদ্য, তার দাম ৫৮ টাকা থেকে লাফিয়ে উঠে ৭৫ টাকা। আর গড় দাম ৫৪ টাকা থেকে ৬০ টাকায় পৌঁছেছে।
এই অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি শুধু ভোক্তার পকেট ফাঁকা করেনি, বরং মূল্যস্ফীতির চাকা আবারও ঘুরিয়ে দিয়েছে উল্টো দিকে। জুলাইয়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮.৫৫ শতাংশে—যা জুনের তুলনায় বেশি। খাদ্যমূল্যস্ফীতিও বেড়ে হয়েছে ৭.৫৬ শতাংশ, যেখানে আগের মাসে ছিল ৭.৩৯ শতাংশ। অথচ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় আমাদের মূল্যস্ফীতি এখনও অনেক বেশি।
বাংলাদেশের খাদ্যতালিকায় ভাতের আধিপত্য এতটাই বেশি যে, চালের দাম বাড়লেই সরাসরি তা মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে দেয়। এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও। ১২ অগাস্ট নতুন কৃষি ঋণ নীতিমালা ঘোষণার সময় তিনি স্বীকার করেছেন—আমাদের আমদানি নীতিমালাও খাদ্যমূল্যস্ফীতি বাড়াতে ভূমিকা রাখছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কথাতেই ধরা পড়ে, নীতিমালার দুর্বলতার কারণে যখন বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমদানির দরকার হয়, তখনই তা সম্ভব হয় না। অথচ গেল অর্থবছরে (২০২৪–২৫) সরকার রেকর্ড পরিমাণ চাল আমদানি করেছে—গত সাত বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। এ সময়ে আমদানি হয়েছে ১৪.৩৬ লাখ টন চাল, যেখানে আগের অর্থবছরে (২০২৩–২৪) এক কণাও আমদানি করতে হয়নি।
বৈশ্বিক বাজারের ছবিও আমাদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। বাংলাদেশের প্রধান আমদানির উৎস থাইল্যান্ডে ভাঙা সাদা চাল—যাকে আমরা আতপ চাল বলি—এর দাম টনপ্রতি নেমে এসেছে ৩৭৫ ডলারে, যা ২০১৭ সালের পর সর্বনিম্ন। থাইল্যান্ডের এই দামই আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের নীতিগত দুর্বলতা ও বাজার কারসাজি মিলিয়ে সাধারণ মানুষকে উচ্চমূল্যই গুনতে হচ্ছে।
বিগত সরকারের সময় বহু আগে থেকেই দাবি করা হচ্ছিল, বাংলাদেশ নাকি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমদানির বাস্তব চিত্র সেই দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আসল সমস্যাটা এখানেই—দেশে ঠিক কত চাল উৎপাদিত হয়, তার নির্ভুল তথ্য আমাদের কাছে নেই। এই তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছেই থাকার কথা, কিন্তু নানা কারণে তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে পাওয়া যায় না।
আগের সরকার যেমন অর্থনীতিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর জন্য পরিসংখ্যানে হেরফের করত, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছে। এখন সময় এসেছে এই ভাঁওতা বন্ধ করে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করার। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারকে সেই পথেই হাঁটতে হবে—নইলে চালের বাজারে মানুষের ভোগান্তি শেষ হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
গত পাঁচ অর্থবছরের তথ্য বলছে, দেশে ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েছে। ২০২০–২১ অর্থবছরে যেখানে উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৭৬ লাখ টন, ২০২৪–২৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ১৯ লাখ টনে। উৎপাদন বাড়লেও সরকার সতর্কতার জন্য—যে কোনো দুর্যোগের ঝুঁকি মাথায় রেখে—প্রতি বছর কিছু চাল আমদানি করে। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যও আমদানির এই পথ খোলা রাখা হয়। এ বছর অগাস্ট পর্যন্ত আমদানি হয়েছে ১৯.৬৯ লাখ টন চাল, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ লাখ টনেরও বেশি।