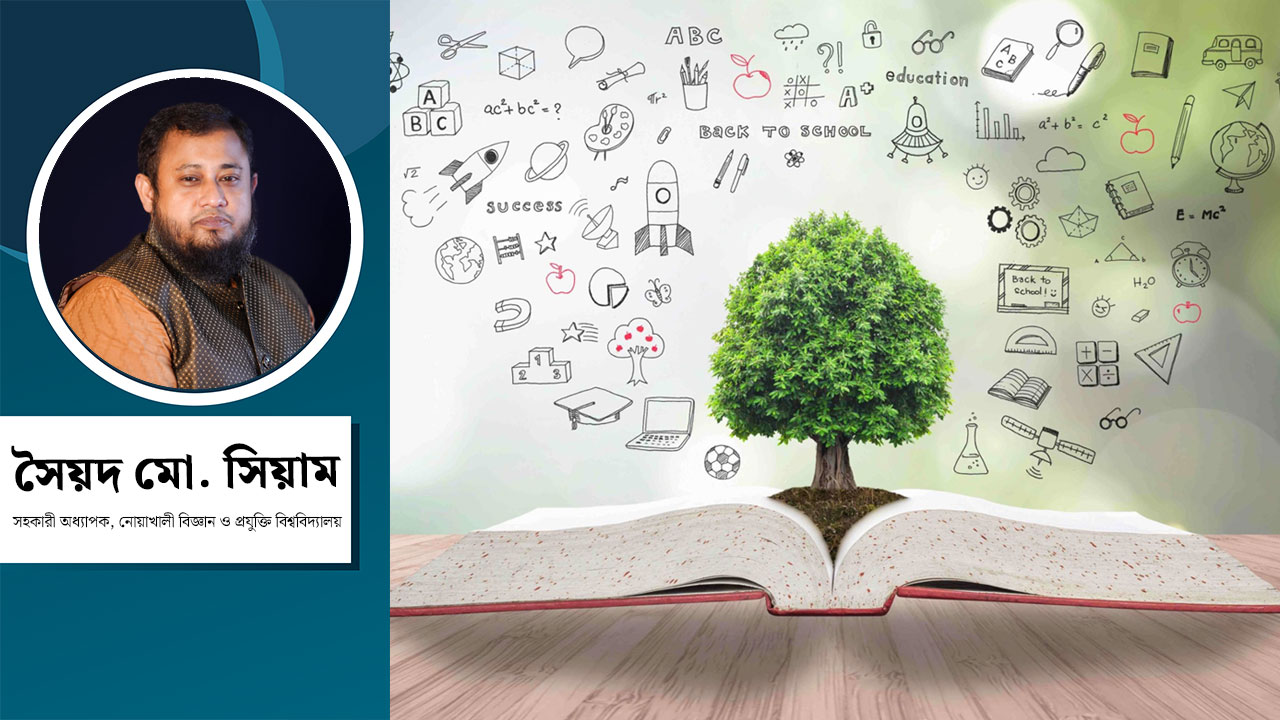অভ্যুত্থানের পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেন ব্রাত্য
বাংলাদেশ হলো আত্মমুগ্ধ ব্যক্তিদের (নার্সিসিস্টদের) দেশ। এ জনপদের মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে তাই ‘নার্সিসিস্ট পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার’ (এনপিডি) থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য একাডেমিকভাবে এ প্রবণতার ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। তবে জুলাই অভ্যুত্থানকে মানদণ্ড ধরলে এ মুহূর্তে বাংলাদেশকে ‘নার্সিসিস্টদের দেশ’ বললে অত্যুক্তি হবে না!
জুলাই অভ্যুত্থানকে নানা রঙে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। জাতিগতভাবে এটিও সম্ভবত আমাদের সাধারণ প্রবণতা। যে কারণে এই গণ-অভ্যুত্থানকে কখনো ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘বিপ্লব’, কখনোবা ‘মেটিকিউলাস ডিজাইন’ কিংবা ‘মাস্টারমাইন্ড তত্ত্ব’ দিয়ে আবরণ পরানো হয়েছে। এটা হয়েছে নিজেকে অধিপতিশীল ভাবার কারণে কিংবা নিজের সময়কে বৃহৎ ইতিহাসের নিক্তিতে অনেক বড় করে দেখার আরোপিত ভ্রান্তি থেকে।
একটা গণ-অভ্যুত্থান যে ‘মেটিকিউলাস’ কিংবা একক ভরকেন্দ্রিক হতে পারে না এবং সর্বোপরি গণ-অভ্যুত্থানকে অর্গানিক উপায়ে বিপ্লবে রূপান্তর করতে যে ‘উৎপাদন পদ্ধতি’ (মোড অব প্রোডাকশন) ও ‘উৎপাদন সম্পর্ক’ (রিলেশনস অব প্রোডাকশন) পরিবর্তন অনিবার্য, এটা ক্রিটিক্যালি পাঠ না করেই গণ-অভ্যুত্থানে আপামর শ্রেণির অবদানকে খাটো করে দেখেছেন হালের অধিপতিশীলরা।
আমি যা করেছি, সেটিই মহীয়ান, বাদ বাকি সব ‘অপর’—এই প্রবণতা থেকেই জন্ম হয় ফ্যাসিবাদের; আধিপত্যবাদী বয়ানের। এই মননের অন্তরেই ঘুমিয়ে থাকে নার্সিজম; অর্থাৎ নার্সিজম খোদ নিজেই এমন একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভরকেন্দ্র সৃষ্টিকারী, যা অধিকতর সংকটের মুখোমুখি করে ফেলে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে।
অভ্যুত্থান–উত্তর প্রথমবর্ষের মধ্যেই তার দিক উন্মোচন হতে শুরু করেছে, যা অভ্যুত্থানের প্রকৃত স্পিরিটকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক-গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বয়ান ও ক্ষমতাচর্চা তো জুলাইয়ের স্পিরিট নয়!

অতীতের নিক্তিতে চব্বিশের ঐতিহাসিক অবস্থান
চব্বিশের গুরুত্ব–বীরত্ব নিঃসন্দেহে নানামাত্রিকভাবে অভূতপূর্ব। তবে এই বীরত্বকে সাতচল্লিশ ও একাত্তরের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখার নিক্তিটিও ‘অভূতপূর্বভাবে’ বিপজ্জনক! এই বয়ান কয়েকটি দুর্দান্ত ঐতিহাসিক লড়াইকে একবারে নাকচ করে দিয়েছে। তার মধ্যে উনসত্তর ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান অন্যতম।
আশির দশকে প্রায় দশকব্যাপী আন্দোলনে ছাত্রসংগঠনগুলো একত্র হয়ে ১০ দফা দিয়েছিল। সেসব দাবির মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সর্বোপরি শ্রেণিবৈষম্য দূরীকরণে উৎপাদন সম্পর্ক বদলের তৎপরতা ছিল। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছয় ছফাকে বিস্তৃত করে ছাত্রসমাজের যে ১১ দফার ওপর দাঁড়িয়েছিল, তার কাছাকাছি দূরদর্শী রাজনৈতিক এজেন্ডা এর আগে-পরে বলতে গেলে তৈরিই হয়নি।
নতুন রাষ্ট্রপ্রকল্পের স্বপ্নে বিভোর শিক্ষার্থীদের আটষট্টি-উনসত্তরের ১১ দফার মধ্যে তিন–চতুর্থাংশ দাবি ছিল শ্রমজীবী শ্রেণির প্রশ্নে, যেগুলো উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছিল। আর প্রথম দফাতেই ছিল শিক্ষার আশু সংস্কারকল্পে হামুদুর রাহমান শিক্ষা কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল ও শিক্ষার্থীদের মাসিক ফি কমানোর দাবি। আশ্চর্যই বৈকি, বর্তমানের শক্তিশালীদের বয়ানে উনসত্তর নিয়ে কোনো কথাই নেই!
এরও আগে দুর্দান্ত দূরদর্শী ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনকেন্দ্রিক ২১ দফা, যার প্রথম আটটির মধ্যে সাতটিই ছিল কোনো না কোনোভাবে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার্থে। ৯ থেকে ১১ পর্যন্ত তিনটি দফা ছিল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সংস্কার প্রশ্নে।
পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের নিপীড়নমূলক স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের ওই ২১ দফা হয়ে উঠেছিল সত্যিকার অর্থেই জনগণের জন্য মুক্তির মেনিফেস্টো। তবে সেটা ছিল রাজনীতিকদের ভূমিকায় ঋদ্ধ আর আমাদের এই আলোচনা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা বিচারে সীমাবদ্ধ।


-69890d3d62cc6.jpg)