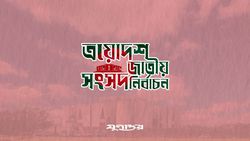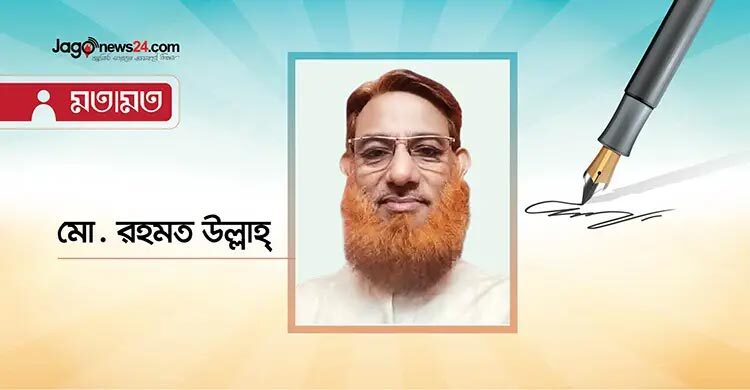যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থায় হ্যাকিং উদ্বেগে ব্যাংকিং খাত
লেখার শিরোনাম দেখে অনেক বিদগ্ধ পাঠক ভাবতে পারেন যে আমেরিকার ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার অফিসে হ্যাকিংয়ের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে লেখালেখি করে কী লাভ। সরাসরি লাভক্ষতির বিষয় সেভাবে না থাকলেও ঘটনার গুরুত্ব যে একেবারে নেই, তেমন নয়। অনেক দিক থেকেই বিষয়টি জানা এবং এ ব্যাপারে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্ব যথেষ্টই আছে। প্রথমত, আমাদের দেশের কিছু মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে হ্যাকিং, আর্থিক জালিয়াতি, সাইবার আক্রমণ ও মানি লন্ডারিংয়ের মতো ঘটনাগুলো শুধু আমাদের দেশেই ঘটে।
কিন্তু বাস্তব যে সে রকম নয়, রবং এসব ঘটনা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে উন্নত বিশ্বেই অনেক বেশি পরিমাণে ঘটে। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফিন্যানশিয়াল লেনদেনের নেটওয়ার্ক। তাই এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থাকবে, এটিই স্বাভাবিক
বিশ্বের যে প্রান্তেই ব্যাংকিং খাতে কোনো অঘটন ঘটুক না কেন, তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের ওপর পড়ে। আমেরিকার ব্যাংকিং খাতে কোনো রকম ক্ষতিকর কিছু ঘটলে তার প্রভাব বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ওপর পড়তে পারে।
আবার এর বিপরীতটাও হতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে কোনো অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তার প্রতিফলন আমেরিকার ব্যাংকিং খাতেও পড়তে পারে। বিশ্বের কোনো একটি দেশের ব্যাংকিং খাতের ঘটনা কিভাবে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, তা ব্যাখ্যা করতে গেলে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যার সুযোগ এখানে নেই।
এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হ্যাকিং ও সাইবার আক্রমণের ঘটনা উন্নত বিশ্বের তুলনায় যথেষ্ট কমই ঘটে থাকে।
এর কারণ বাংলাদেশ এখনো সে অবস্থায় পৌঁছায়নি যে সাইবার আক্রমণ করে হ্যাকাররা পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা নিতে পারে। কেননা এখন যে মাত্রার হ্যাকিং বা সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটে, সেখানে সাইবার অপরাধীদের পর্যাপ্ত অর্থ ও শ্রম দিতে হয়। তাই যেখানে হ্যাকিং বা সাইবার আক্রমণ চালিয়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা পাওয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুযোগ না থাকে, সেখানে সাইবার অপরাধীরা হাত দিতে চায় না। বাংলাদেশে যদি বর্তমানের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সেই পর্যায় যেতে পারে, তখন সাইবার অপরাধীরা বাংলাদেশকে সাইবার আক্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

যা হোক, এখন আসি ওসিসিতে (অফিস অব দ্য কম্পট্রোলার অব দ্য কারেন্সি) হ্যাকিংয়ের ঘটনায়।
ওসিসি হচ্ছে আমেরিকার ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের একটি বিভাগ, যারা মূলত সেখানকার ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্ব পালন করে। এই নিয়ন্ত্রক সংস্থা আমেরিকার ব্যাংক, ফেডারেল সরকারের নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি ব্যাংকের শাখার কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানকার ব্যাংকগুলোকে নিরাপদ ও সচ্ছল রাখা, যাতে আমেরিকার ব্যাংকিং সিস্টেম ঝুঁকিমুক্ত থাকে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের মতো আমেরিকা ও কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেখানকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুপারভাইজ করে না। এই কাজের জন্য আছে পৃথক দপ্তর বা এজেন্সি। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম এবং কানাডায় আছে ব্যাংক অব কানাডা। এখানকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত দেশের মুদ্রানীতি নিয়ে কাজ করে, বিশেষ করে নীতি সুদ হার, মূল্যস্ফীতি এবং কর্মসংস্থানের বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। সেই সঙ্গে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন এবং মূলধন সংরক্ষণের বিষয়টি সরাসরি দেখে থাকে। ব্যাংকের যে দৈনন্দিন কার্যক্রম আছে, সেসব দেখাশোনার জন্য আছে পৃথক সংস্থা। যেমন—আমেরিকার আছে ওসিসি এবং কানাডায় আছে অসফি (OSFI)।
ওসিসির সঙ্গে ব্যাংকগুলোর যোগাযোগের জন্য আছে সবচেয়ে নিরাপদ এবং অতি গোপনীয় ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, যাকে সংক্ষেপে সিকিউরড বা নিরাপদ ই-মেইল সিস্টেম বলা হয়। আমেরিকার ব্যাংকগুলো এই নিরাপদ ই-মেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে ওসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য ওসিসিতে প্রেরণ করে। ওসিসির এই নিরাপদ ই-মেইল সিস্টেম হ্যাকিং হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে। ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থায় সাইবার আক্রমণের ঘটনাটি এখনো তদন্তাধীন। ফলে হ্যাকিংয়ের উদ্দেশ্য এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো সেভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় আমেরিকার ব্যাংকিং খাত পড়েছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে। বিশেষ করে বড় ব্যাংকগুলো; যেমন—জেপি-মরগ্যান ও চেজ ব্যাংক, ব্যাংক অব আমেরিকা এবং ব্যাংক অব নিউইয়র্ক মেলনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে আছে। তারা ওসিসির নিরাপদ ই-মেইল ব্যবহার করে সংবেদনশীল তথ্য প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকে বিকল্প ব্যবস্থায় পাঠানো যায় কি না, তা নিয়ে ওসিসির সঙ্গে আলোচনা করছে। আমেরিকার ব্যাংকগুলোর উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, এই হ্যাকিংয়ের ঘটনায় কী ধরনের সংবেদনশীল তথ্য বেহাত হয়ে থাকতে পারে এবং এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ কী হবে, সেসব নিয়ে।
ওসিসিতে হ্যাকিং হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। এমনকি এই অফিস যাদের সুপারভাইজ ও নিয়ন্ত্রণ করে, সেই ব্যাংকগুলোকেও বিষয়টি জানানো হয়নি। যদিও তারা তাদের ওয়েবসাইটে হ্যাকিং সংক্রান্ত একটি সংবাদ রেখেছিল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকগুলোকে জানানো হয়নি। অনেক ব্যাংক জানতে পেরেছে ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর। এটিই স্বাভাবিক। এভাবেই হ্যাকিং, সাইবার আক্রমণ, আর্থিক জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মতো অপরাধ ম্যানেজ করা হয়, তা বিশ্বের যে প্রান্তেই ঘটুক। কেননা এ রকম ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নিরূপণ করার চেষ্টা হয় ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্য কী, কারা জড়িত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত। এরপর ক্ষতিপূরণের কাজটি নিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে এটিও নিশ্চিত করা যে আক্রান্ত সিস্টেমটি ব্যবহার করতে আর কোনো রকম ঝুঁকি নেই। এসব পদক্ষেপ সম্পন্ন করেই ঘটনাটি সবাইকে জানানো হয়।
- ট্যাগ:
- মতামত
- হ্যাকিং এর শিকার
- ব্যাংকিং খাত