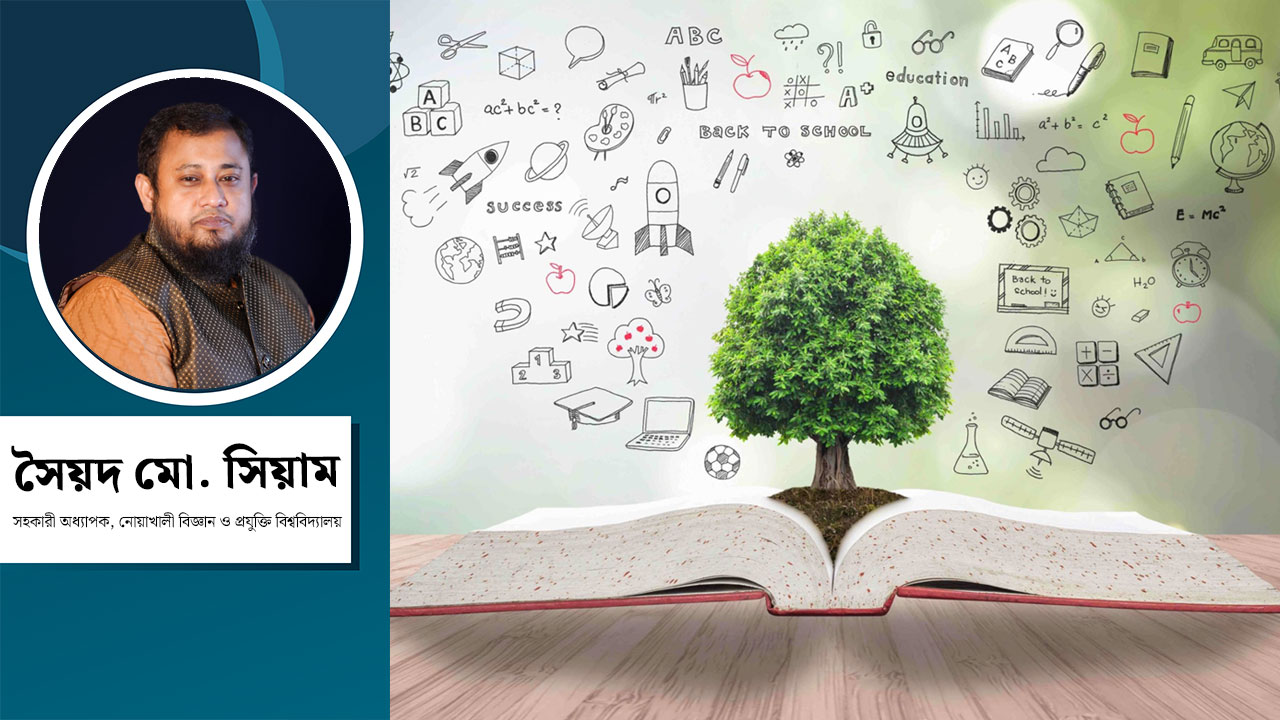মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম
উনিশ শতকের কোনো বাংলা জার্নাল যে ভাষায় প্রকাশিত, আজকের কোনো দৈনিক বা সাময়িকীর ভাষার সঙ্গে তার কত অমিল। মানুষের ভাষার অন্যতম প্রধান দলিল সাহিত্য, সেই সাহিত্যের ভাষাও কতভাবে বদলে যাচ্ছে। সেকালের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষায় লিখে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, একালের কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে ভাষায় লিখে, দুজনেই বাংলা ভাষায় লিখেছেন বটে তবু দুজনের ভাষাই একইরকম, তা কি বলা যাবে? ভাষা নিজেই সময়ের বাঁকে বাঁকে বদলে গেছে। ভাষা মুখে মুখে ছড়ায়, কালে কালে তার ভঙ্গি পাল্টায়। ১৮৯৯ সালে বাংলায় জন্মগ্রহণ করা দুটি শিশু বড় হতে হতে একদিন কবি হয়ে ওঠেন। একজন বর্ধমানের আসানসোলের চুরুলিয়াতে, একজন বরিশালে। একজন কাজী নজরুল ইসলাম, আরেকজন জীবনানন্দ দাশ।
লেখালেখিতে নজরুলের আত্মপ্রকাশ গত শতকের বিশের দশকেই, জীবনানন্দকে পাওয়া যায় ত্রিশের দশকে গিয়ে। জীবনানন্দ লেখালেখির শুরুর দিকে ভাষা-ছন্দে ঈষৎ নজরুল-আক্রান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই দাশ চিত্রিত করলেন এমন এক ভাষা, যে রকম ভাষাভঙ্গির কবিতা বাঙালি পাঠক আগে পড়েনি। অর্থাৎ একই বছরের জাতক দুজন কবির কবিতাও কত আলাদা আলাদা হট্যাঁ থাকে। যেভাবে একজন গ্রামীণ কৃষকের মুখের ভাষা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মুখের ভাষা এক নয়। সেখানে ভাষার কৌলীন্য বলে একটা বিষয় আমাদের মুখোমুখি চলে আসে। অর্থনৈতিক ও সাং¯ৃ‹তিক দূরত্ব প্রতিভাত হয়। তাই গ্রামীণ কবিয়ালের ভাষা ও ‘আধুনিক কবি’র ভাষার মধ্যে একটা শ্রেণিগত বৈষম্য বিরাজ করে। গ্রামের ¯ু‹লের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলে, শহরের ¯ু‹লের ছাত্রছাত্রীদের ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গি আলাদা হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বা এক ধরনের সূক্ষ্ম লড়াই জারি হয়ে থাকে। আর নিরক্ষরজনের মুখের ভাষাতে তো কোনো রচনা ছাপাই হয় না, হলে ভাষার আরও কত বৈচিত্র্য না আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু বিধান-ব্যবস্থাই এমন যে, শুধু লেখাপড়া লোকদের ভাষাই ছাপা হয়ে থাকে। নিরক্ষরজনের ভাষা যে একদম ছাপাখানায় যায় না, তা নয়। তবে সেটি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাটক বা সিনেমায়, কোনো নিরক্ষর চরিত্রের সংলাপে। কবিয়ালরাণও গ্রামীণ পর্যায়ের একটা চলনসই ভাষাতেই উপস্থাপিত হয়ে এসেছেন। অথচ ভাষা শুধু বর্ণমালাতেই প্রকাশিত নয়, ভাষা ব্যক্ত নয় শুধু মুখেই। ভাষা ব্যক্ত শারীরিকভাবেও, ইংরেজিতে যাকে বলে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। একজন সরকারি বড় কর্তার হাঁটাচলা ও একজন কেরানির হাঁটাচলার ভাষা কত আলাদা। ভাষা বর্ণমালার বাইরেও তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে চলে। ফলত, ভাষার লড়াই শুধু একটি ঐতিহাসিক শহীদী ঘটনা বা কোনো দিবস উদযাপনেই সীমিত থেকে যায় না, ভাষার লড়াই জারি থাকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাং¯ৃ‹তিক লড়াইয়ের অংশ হয়ে। লড়াই জারি আছে, লড়াই চলছে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- মাতৃভাষা
- মাতৃভাষা দিবস
- কথাসাহিত্যিক


-69890d3d62cc6.jpg)