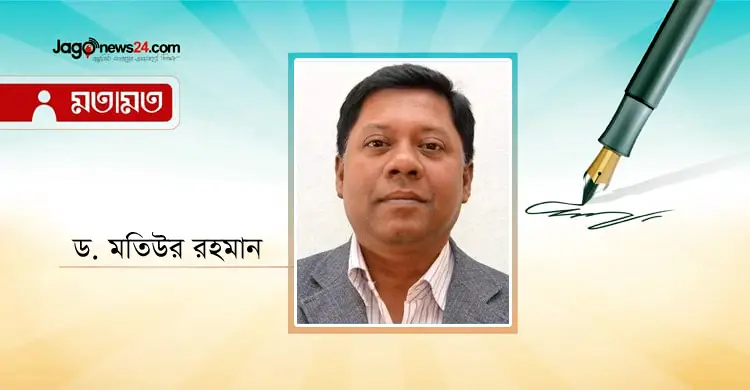
ভূমিকম্প ট্রমা ও উদ্বেগ : অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবিলায় উদ্যোগ চাই
ভূমিকম্পকে আমরা সাধারণত একটি নির্ভেজাল ভূতাত্ত্বিক ঘটনা হিসেবেই শ্রেণিবদ্ধ করি। কিন্তু এর সবচেয়ে গভীর, দীর্ঘস্থায়ী এবং অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি হয় মানুষের সামাজিক ও মানসিক জগতে। মাটির কম্পন যত বড় হয়, সমাজের অভ্যন্তরে তার আঘাত তত বেশি গভীরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ, অবকাঠামোগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অসম নগরায়ণের দেশে ভূমিকম্প কোনো ক্ষণস্থায়ী শারীরিক বিপর্যয়ই নয়; এটি একটি তীব্র সামাজিক মানসিক চাপ, যা মানুষের মন, সম্পর্ক, আচরণ, আস্থা এবং নিরাপত্তাবোধকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। এই মানসিক চাপই প্রকারান্তরে অর্থনীতি এবং উৎপাদনশীলতাকে স্থবির করে দেয়।
২০২৫ সালের ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পের মতো একটি মাঝারি কম্পনও তাই আমাদের সামনে দেশের মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গুরতাকে উন্মোচিত করেছে। ভূমিকম্পের প্রথম আঘাতটি আসে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে, যাকে অস্তিত্বগত অনিরাপত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কয়েক সেকেন্ডের সেই কম্পনের মধ্য দিয়ে মানুষ হঠাৎ উপলব্ধি করে যে তাদের জীবনের ভিত্তি (পৃথিবী) মোটেও স্থিতিশীল বা পূর্বানুমানযোগ্য নয়। এই উপলব্ধি এক ধরনের তীব্র মানসিক চাপজনিত ব্যাধি তৈরি করতে পারে, যা পরবর্তীতে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা পিটিএসডি-এর দিকে পরিচালিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।
ঢাকার মতো শহরে যেখানে মানুষ প্রতিদিন ফাটলধরা দেয়াল, সংকীর্ণ সিঁড়ি, অবরুদ্ধ অগ্নিনির্বাপক পথ এবং অনুমোদনহীন বহু-তলা ভবনের মধ্যে জীবন কাটায়, সেখানে ভয়ের ভিত্তি শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, বাস্তব। এই বাস্তব ঝুঁকি মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় অসহায়তা-বোধের। এই অসহায়তা-বোধ হলো এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যেখানে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের কিছু করার নেই, কারণ কর্তৃপক্ষ এবং অবকাঠামো নির্ভরযোগ্য নয়।






