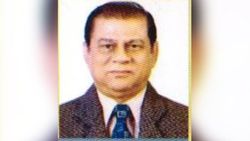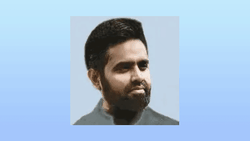ইসরায়েল প্রশ্নে তরুণদের ভাবনা
মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তা তহবিল পাসের শুনানিতে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক হাতে ‘লাল রক্তের প্রতীক’ ধারণ করে শান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছিল যে বছরের পর বছর ধরে লুকিয়ে রাখা সত্য আজ আর আঁধারে গোপন থাকছে না। রক্তের প্রতিটি ছোঁয়া, প্রতিটি দৃঢ় দৃষ্টি যেন একটিমাত্র বার্তা দিচ্ছিল—অবিচার আর নিপীড়নের ইতিহাসকে আর চুপচাপ স্বীকার করা যাবে না। ইসরায়েল বহু দশক ধরে চরম শক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দখলদারির ছায়ায় ফিলিস্তিনকে নিপীড়ন করে আসছে। বহু বছর ধরে পশ্চিমা মিডিয়া সেই কাহিনিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে—ইসরায়েলকে নিরপরাধ ভুক্তভোগী, আর ফিলিস্তিনকে আগ্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই চিরন্তন প্রোপাগান্ডার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। প্রতিটি ছবি, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং গাজার কণ্ঠ—সবই সরাসরি মানুষের চোখের সামনে সত্য তুলে ধরেছে।
প্রথমে এই পরিবর্তনকে অনলাইনে সক্রিয় কিছু কিশোরের ‘ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ’ হিসেবে অবহেলা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন স্পষ্ট—তথ্য আর সত্যকে চাপা দেওয়া আর সম্ভব নয়। মানুষ আজ দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে এবং অনুভব করতে পাচ্ছে—যা আগে ফিল্টার করে, প্রোপাগান্ডার আড়ালে চাপা রাখা হতো। রক্তের চিহ্ন, ভাঙা মহল্লা, ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল, অনাহারী শিশুদের অশ্রু—সবই আজ বিশ্বজনমনে প্রশ্ন তুলছে। এই দৃশ্যকল্প ও তথ্যের যুগে প্রজন্মগত পরিবর্তন অচল নয়। তরুণ আমেরিকানরা, যারা জীবনে দুই বা তিনটি খবরের সূত্রে বেড়ে ওঠেনি, এখন সত্যকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করছে। তাদের কাছে প্রোপাগান্ডা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তারা সরাসরি ভিডিও, রিয়েল-টাইম সংবাদ এবং ভুক্তভোগীর গল্পের মধ্য দিয়ে বুঝছে—ইসরায়েলের ভেজালি নৈতিকতা ও লুকানো ইতিহাসের মিথ আর টিকে থাকতে পারবে না।
নতুন জরিপের ফলাফলেও এই পরিবর্তনের গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছে। কুইনিপিয়াক ও নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ভোটাররা +৪৮ পয়েন্টে ইসরায়েলের পাশে ছিলেন। অর্থাৎ ইসরায়েল সমর্থনকারী ভোটাররা ফিলিস্তিন সমর্থকদের তুলনায় ৪৮ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজ সেই সমীকরণ উল্টে গেছে—ফিলিস্তিন সামান্য হলেও এগিয়ে, ভোটাররা +১ পয়েন্টে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান করছেন।
মানুষের চোখ খুলেছে এবং সত্য আর মিথের লড়াই এতটাই স্পষ্ট যে কোনো কৌশল বা প্রোপাগান্ডা এই পরিবর্তনকে রোধ করতে পারবে না। পরিবর্তন সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে। দুই বছর আগে তাঁরা +২৬ পয়েন্টে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; আজ সেই সমর্থন উল্টে গিয়ে +৪৬ পয়েন্টে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান করছেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ৭২ পয়েন্টের এই ওলটপালট প্রমাণ করছে, যাঁরা একসময় ইসরায়েলের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা এখন সমানতালে ফিলিস্তিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিকে, রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে বয়সভিত্তিক ভাঙন লক্ষ করা যাচ্ছে। ৫০ বছরের কম বয়সী ভোটাররা ইসরায়েলের প্রতি আগ্রহ কম দেখাচ্ছেন, আর বয়স্করা এখনো তুলনামূলকভাবে প্রথাগত সমর্থন বজায় রাখছেন। এটি আর সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়। এটি প্রজন্মগত, নৈতিক এবং বাস্তবভিত্তিক। তরুণ আমেরিকানরা এখন নিরপেক্ষ চোখে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড যাচাই করছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে ধারা চলে এসেছে—ইসরায়েলকে ভিকটিম হিসেবে দেখানো—এটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এমন একটি বিশ্বজনমতের অংশ, যারা ছোটবেলা থেকেই রুটিন নিউজের সীমাবদ্ধতা বা শীতল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেনি। তাদের জন্য তথ্যের উৎস এখন অবাধ, রিয়েল-টাইম ভিডিও প্রচলিত মিডিয়ার বাঁধাধরা বার্তাকে সরাসরি অতিক্রম করছে। তাদের চোখে সত্য আরও স্পষ্ট এবং প্রজন্মের এই জাগরণ চুপচাপ মিথকে আর ঠেকাতে পারবে না।
ইসরায়েল যখন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় প্রবেশের পথ বন্ধ করল, তখন সে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি আগুন জ্বালিয়ে দিল—বিকল্প সংবাদ চাহিদার আগুন। সোশ্যাল মিডিয়া আজ স্বাধীন তথ্যের এক অটল বাতিঘর হয়ে উঠেছে। এটি সমতার ভূমিকা পালন করছে এবং সেই নৃশংসতা প্রকাশ করছে, যা আগে পুরোনো মিডিয়ার ফিল্টার দিয়ে চাপা দেওয়া হতো। ফিলিস্তিনিদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইসরায়েল ও তার মিত্ররা বারবার কৌশল অনুসরণ করে ‘গল্প পরিবর্তন’ করছে—যেন সত্যের আলোকে আড়াল করতে চায়।
২০২৫ সালে জ্যাকি ও জেফ কার্শ নামের দুজন ধনী জায়নবাদী একটি নতুন ‘জার্নালিজম ফেলোশিপ’ চালু করেন। ‘সুপারফিসিয়াল’—এটি সাংবাদিকতার একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বলে দাবি করা হলেও, অন্তরে উদ্দেশ্য স্পষ্ট—ইসরায়েলের পক্ষে মিডিয়ার গল্প পুনর্গঠন। প্রোগ্রামে মেন্টর হিসেবে আছেন সিএনএন ও নিউইয়র্ক টাইমসের ইসরায়েলপন্থী সাংবাদিকেরা। মূল লক্ষ্য—প্রোপাগান্ডাকে সাংবাদিকতার পোশাক পরিয়ে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কিন্তু বাস্তবতা সোশ্যাল মিডিয়ার আঙিনায় অন্য রকম। আনফিল্টার করা ভিডিও, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং গাজার হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিশ্বজুড়ে পৌঁছে গেছে। জনমত এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, কোনো নিয়ন্ত্রিত কাহিনি আর আটকাতে পারছে না। সোশ্যাল মিডিয়া ভেজালি নৈতিকতার আড়াল ভেঙে দিয়েছে। কোনো বিলিয়নিয়ার তহবিল, কোনো কংগ্রেসে প্রশংসা—কিছুই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে যে মিথ টিকে রেখেছিল দখল, বৈষম্য ও শক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, তার ওপর এখন নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন তুলছে। রাজনৈতিক প্রভাবও গভীর। আগে ইসরায়েলের বিষয়ে দুই দলীয় সমঝোতা অটুট থাকলেও, আজ সেখানে দৃশ্যমান ফাটল।