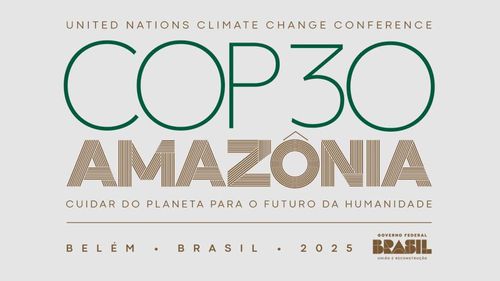
জলবায়ু সম্মেলন কি প্যারিসচুক্তিকে পথ দেখাতে পারবে
প্রতিবছর জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবারের সম্মেলনটি ৬ থেকে ২১ নভেম্বর ব্রাজিলের আমাজনের রেইনফরেস্ট এলাকায় বেলেমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো, বৈশ্বিক তাপমাত্রা সীমিত রাখার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জাতিসংঘের এই ৩০তম কপ সম্মেলনটি প্যারিসচুক্তির প্রায় ১০ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
কপ সম্মেলন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত প্যারিসচুক্তি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিসচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২০১৫ সালে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং প্রাক-শিল্পায়নের পর্যায়ের তুলনায় এটিকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। উন্নত দেশ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থায়ন ও প্রযুক্তি প্রদানের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সারা বিশ্ব ও জাতিকে রক্ষা করাই ছিল প্যারিসচুক্তির মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, এ চুক্তিটি ২০১৬ সালের নভেম্বরে কার্যকর হয়েছিল। ওই চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন ৩০ শতাংশ কমিয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্যের কোঠায় নামাতে হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্যারিসচুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে ২০৩০ সালের দিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, লিবিয়া ও ইয়েমেনের প্যারিসচুক্তির সঙ্গে ভিন্নমত রয়েছে। এসব দেশের অর্থনীতি অনেকটা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। যদি ওই দেশগুলো প্যারিস চুক্তির সঙ্গে একমত পোষণ করে, তাহলে তাদের তেল উৎপাদন ও রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির ওপর একটা বড় ধরনের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। আগে যুক্তরাষ্ট্র প্যারিসচুক্তিতে একমত পোষণ করলেও বর্তমানে চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৬৯ শতাংশ মানুষের প্যারিসচুক্তির সঙ্গে সহমত রয়েছে।
বৈশ্বিক উষ্ণতা দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস অনাকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া। বায়ুমণ্ডলে এ গ্রিনহাউজ গ্যাসের বৃদ্ধির জন্য অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পায়ন, গাছপালা নিধন, যানবাহন, শহরায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও জলাভূমি ভরাটকে দায়ী করা যেতে পারে।
বায়ুমণ্ডলে নির্গত প্রধান গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলো হলো-কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প, নাইট্রাস অক্সাইড ও ফ্লোরিনেটেড গ্যাস। এসব গ্যাস দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠের নির্গত তাপ শোষিত এবং আবারও বিকরিত হওয়ায় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ গ্যাসগুলোর নির্গমন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমাতে পারলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমে যাবে বলে আশা করা যায়। বায়ুমণ্ডলে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ কমাতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানো, সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পণ্যসামগ্রীর পুনঃব্যবহার, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষি উৎপাদন, গাছ লাগানো ও বনভূমি সংরক্ষণ বায়ুমণ্ডলে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ কমাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।
২০২৪ সালের জাতিসংঘের নির্গত গ্যাস রিপোর্ট অনুযায়ী, এনার্জির বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পায়ন, যানবাহন, ভবন নির্মাণ, জ্বালানি উৎপাদন ও শিল্পায়নে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে প্রায় ৭৭ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গমিত হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি, বনায়ন, ল্যান্ড ইউজ চেইঞ্জ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সেক্টর থেকে বাকি ২৩ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে।
বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের শীর্ষে রয়েছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। কয়লার ওপর নির্ভরতা ও বৃহৎ উৎপাদন খাতের কারণে চীন সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন করছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আবার মাথাপিছু নির্গমনের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রই সর্বোচ্চ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশ। তৃতীয় বৃহত্তম গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশ হলো ভারত। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনে ভূমিকা রাখছে।
বিশ্বব্যাপী তাপদাহ, বন্যা, খরা ও জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর ছোট দ্বীপরাষ্ট্র ও কিছু অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া মহাসাগরগুলো প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত তাপ ও কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের পানিতে এসিডিটি বাড়ছে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। খাদ্যশৃঙ্খলে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ায় অন্যান্য প্রজাতির জন্য খাদ্যের সংকট দেখা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের যেখানে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে অবস্থিত আমাজন রেইনফরেস্টের ইকোসিস্টেম ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্যদিকে আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলে পারমাফ্রস্ট থেকে বিপুল পরিমাণ মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি, মাইগ্রেশন, সংঘাত, অর্থনৈতিক হুমকি ও বৈষম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধিতে মানবজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। ভবিষ্যতে এ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাস্থ্যঝুঁকি, তাপদাহ, অনাকাঙ্ক্ষিত রোগের প্রাদুর্ভাব এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
- কপ সম্মেলন


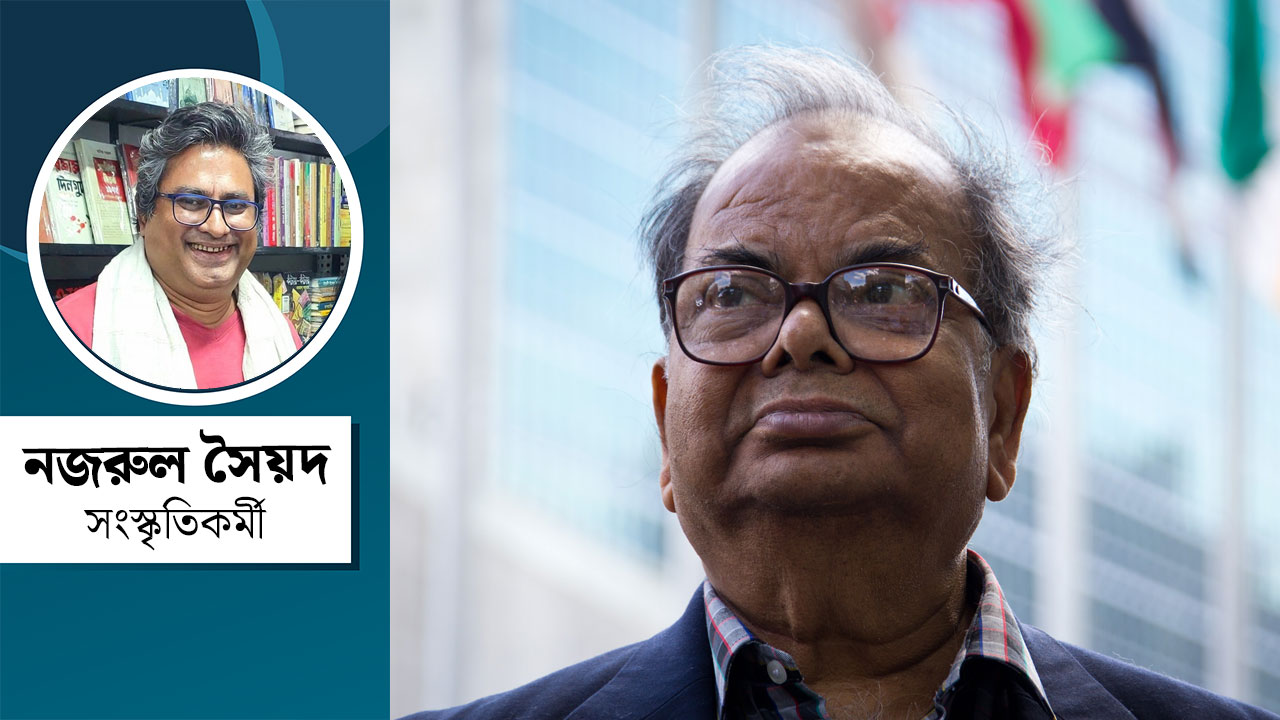
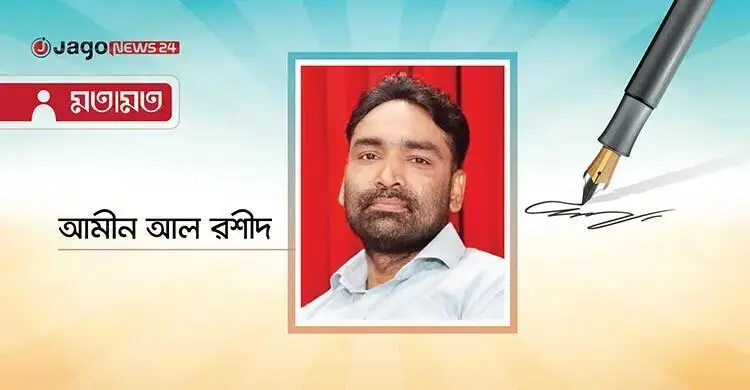

-699b8e6511dac.jpg)

