
বৃষ্টি-খরার দোলাচলে কৃষকের যুদ্ধ চলে
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ, যেখানে আবহাওয়া ও জলবায়ু ফসল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি ও অতিখরা—এই দুই চরম প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ফসল চাষে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।
অতিবৃষ্টির ফলে মাঠে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, মাটির বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ফসলের শিকড় পচে যায় এবং উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে। ধান, সবজি ও ডাল জাতীয় ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অন্যদিকে অতিখরার সময় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় মাটি শুষ্ক হয়ে পড়ে, ফসল পর্যাপ্ত পানি না পেয়ে শুকিয়ে যায় এবং কৃষকরা সেচনির্ভর চাষে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে বাধ্য হয়। এর ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ে ও লাভ কমে। অতিবৃষ্টি যেমন বীজ নষ্ট করে, তেমনি অতিখরা মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।
অতএব ফসল চাষের টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ও বৃষ্টিনির্ভর চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন অপরিহার্য। অন্যথায় অতিবৃষ্টি ও অতিখরার দ্বৈত প্রভাব বাংলাদেশের কৃষিকে দীর্ঘমেয়াদে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।
বৃষ্টির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ:
বৃষ্টি হলো প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ জলচক্রের অংশ, যা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। বৈজ্ঞানিকভাবে বৃষ্টির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয় জলচক্র বা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের মাধ্যমে। সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, হ্রদ ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে উঠে যায়। এই জলীয় বাষ্প বায়ুর ঠান্ডা স্তরে পৌঁছে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় রূপ নেয়। এই ক্ষুদ্র জলকণাগুলো মিলিত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে।
যখন মেঘে জলকণার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তাদের ওজন বায়ুর দ্বারা ধারণ করা সম্ভব হয় না, তখন সেই জলকণাগুলো পৃথিবীতে নেমে আসে, একেই আমরা বৃষ্টি বলি। এই প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, ও বায়ুচাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, উষ্ণ অঞ্চলে বাষ্পীভবনের হার বেশি থাকায় সেখানে বৃষ্টিপাতও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। বৃষ্টি সাধারণত তিন ধরনের হতে পারে, সংবহনজনিত বৃষ্টি, পর্বতবৃষ্টি এবং ঘূর্ণিঝড়জনিত বৃষ্টি। সংবহনজনিত বৃষ্টি হয় সূর্যের তাপে বায়ু দ্রুত উপরে উঠলে; পর্বতবৃষ্টি হয় যখন আর্দ্র বায়ু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঠান্ডা হয়; আর ঘূর্ণিঝড়জনিত বৃষ্টি ঘটে নিম্নচাপের কারণে বায়ু ঘূর্ণন সৃষ্টি হলে।
অতএব বৃষ্টি একটি জটিল কিন্তু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীর জলচক্রকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে এবং কৃষি, পরিবেশ ও জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
খরার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ:
অনাবৃষ্টি বা খরা হলো এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যখন দীর্ঘ সময় ধরে কোনো অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় না এবং এর ফলে পানির ঘাটতি দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকভাবে খরার মূল কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও জলচক্রের ভারসাম্যহীনতা।
প্রথমত, বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তন খরার প্রধান কারণ। যখন কোনো অঞ্চলে আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত না হয়ে শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন মেঘ তৈরি হয় না। ফলে বৃষ্টিপাতও কমে যায়। বিশেষ করে এল নিনো (El Niño) বা লা নিনো (La Niña) প্রভাবের কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রা পরিবর্তিত হলে বৈশ্বিক আবহাওয়ার ধরণেও পরিবর্তন আসে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে খরার সৃষ্টি করে।
দ্বিতীয়ত, জলচক্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া খরার একটি বৈজ্ঞানিক কারণ। সূর্যের তাপে অতিরিক্ত বাষ্পীভবন হলে মাটি থেকে আর্দ্রতা দ্রুত হারিয়ে যায়। একইসঙ্গে মেঘ গঠনের প্রক্রিয়ায় বাধা পড়ে, ফলে বৃষ্টিপাত কমে যায়।
তৃতীয়ত, বন উজাড় ও পরিবেশ দূষণও খরার প্রভাব বাড়ায়। বন ধ্বংসের ফলে স্থানীয় জলবায়ুর আর্দ্রতা কমে যায়, বাষ্পীভবন হ্রাস পায় এবং মেঘ সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়। শিল্প কারখানার ধোঁয়া ও গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা সৃষ্টি করে, যা জলচক্রে অনিয়ম ঘটায়।
- ট্যাগ:
- মতামত
- বৃষ্টি
- খরা
- কৃষি উৎপাদন
-698a65a64ca3e.jpg)
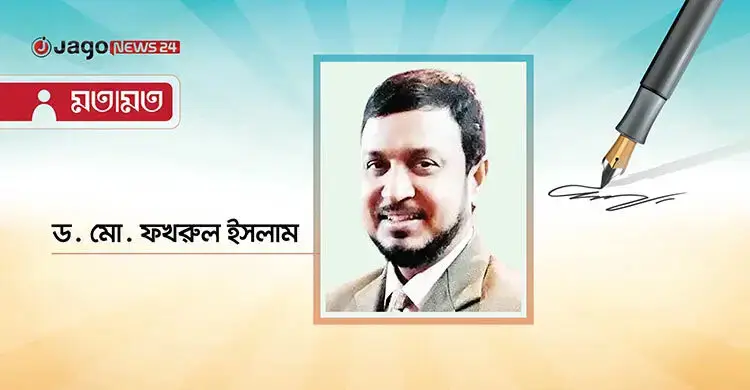
-698a65090f021.jpg)