
দায়মুক্তি ও সংসদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন
বাংলাদেশে দায়মু্ক্তির আলোচনা নতুন নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে গঠিত প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনীর নানা অপরাধের দায়মুক্তি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। আবার ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, তারা দেশকে অপশাসন ও দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ওই ঘটনার পরে ক্ষমতা গ্রহণকারী খন্দকার মোশতাক আহমদ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে হত্যাকারীদের ‘জাতির সূর্যসন্তান’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই দায়মুক্তির বিধান বাতিল করে ১৫ অগাস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। ২০০২ সালের পরে অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য দায়ীদেরও দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল—যা নিয়ে ওই সময়ে এবং পরে অনেক সমালোচনা হয়। তার মানে কোনো সরকার কোনো একটি ঘটনায় কাউকে দায়মুক্তি দিলেই যে সেটা চিরতরে দায়মুক্তি হয়ে যায়, ব্যাপারটা সেরকম নাও হতে পারে।
গত বছরের ১৫ জুলাই থেকে ৪ অগাস্ট পর্যন্ত আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিলেন, তাদেরও দায়মুক্তি দিয়ে নির্দেশনা জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরপর সম্প্রতি জুলাই সনদের অঙ্গীকারে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের পরিবার ও আহতদের আইনগত দায়মুক্তি, তাদের সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। যদিও আইনগত দায়মুক্তির বিষয়টি জুলাই সনদের চূড়ান্ত ডকুমেন্টে ছিল না। ‘জুলাইযোদ্ধাদের’ বিক্ষোভের মুখে অঙ্গীকারের সনদের ৫ নম্বরে সংশোধন এনে আইনগত দায়মুক্তির বিধান করা হয়।
জুলাইযোদ্ধা এবং এনসিপির মূল দাবি, এই সনদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এটির বাস্তবায়নের সাংবিধানিক আদেশ জারি করা। তারা মূলত এই নিশ্চয়তা চায় যে, ভবিষ্যতে কোনো সংসদ যাতে এই সনদ উপেক্ষা করতে না পারে বা সনদের কোনো ধারা বা পুরো সনদটি বাতিল করতে না পারে। তাদের মনে এরকম একটি সংশয় কাজ করছে যে, জুলাই অভ্যুত্থানে পুলিশ হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে ভবিষ্যতে ওই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যদি মামলা হয়, তাহলে তার আইনি সুরক্ষা কী হবে? এটি একটি বড় প্রশ্ন তাতে সন্দেহ নেই। আবার আগামী নির্বাচনের মধ্য যারা ক্ষমতায় আসবে, জুলাই সনদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান কী হবে, সে বিষয়েও হয়তো ‘জুলাইযোদ্ধা’ এবং বিশেষ করে এনসিপির সন্দেহ আছে। ওই কারণেই তারা এমন একটি আইনগত দায়মুক্তি চায়, যার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কেউ জুলাই অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিহত হওয়া বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের বিষয়গুলোকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করতে না পারে।
এটা ঠিক যে, রাষ্ট্রের ভারসাম্য রক্ষায় সংবিধানে এমন কিছু বিধান রাখা হয় যাতে চাইলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে সংসদ সদস্যরা যা খুশি করতে না পারেন। ওই আলোকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে যদি রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয় এবং কিছু প্রস্তাব এখনই এবং কিছু প্রস্তাব পরের সংসদে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়—সেটি এক কথা। কিন্তু যে দায়মুক্তির প্রশ্ন উঠেছে এবং ভবিষ্যতে কোনো সংসদ এটা বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে না বলে যে দাবি উঠছে, সেটি একাডেমিক্যালি ত্রুটিপূর্ণ। এরকম কোনো বিধান অন্তর্বর্তী সরকার সাংবিধানিক আদেশ জারির মধ্য দিয়ে করতে পারে কি না, এটা যেমন প্রশ্ন, তেমনি এরকম কোনো বিধান করা হলেই ভবিষ্যতে কোনো সংসদ এটা পরিবর্তন করতে পারবে না বা করবে না—সেটি এখনই বলা কঠিন।
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কতটা সার্বভৌম, ওই তর্ক অবশ্য পুরোনো। সংসদ সদস্যদের যুক্তি হলো তারা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে যান এবং যে কোনো আইন পাস করতে পারেন। এ কারণে দেখা যায়, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে সর্বোচ্চ আদালত যেদিন রায় দিল, তার তিনদিন পরে ২০১৭ সালের ৪ অগাস্ট সিলেটে এক অনুষ্ঠান শেষে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত পরিষ্কার ঘোষণা দেন, “আদালত যতবার এই সংশোধনী বাতিল করবে, ততবারই সংসদ এটা পাস করবে। করতেই থাকবে।” জনাব মুহিত বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন, “দেখি জুডিশিয়ারি কতদূর যেতে পারে।” বিচার বিভাগ জনগণের প্রতিনিধিদের নেওয়া সিদ্ধান্ত কী করে বাতিল করে ওই প্রশ্নও তোলেন তিনি। এমনকি বিচারকদের তারা চাকরি দেন বলেও মন্তব্য করেন। (দৈনিক যুগান্তর, ৫ অগাস্ট ২০১৮)।
বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো সার্বভৌম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি যে সংসদ সার্বভৌম। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের পূর্ণাঙ্গ রায়ে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতি এ নিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, বাংলাদেশে সংসদ নয়, সার্বভৌম হচ্ছে জনগণ আর সংবিধান। রায়ে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদে কোনো আইন প্রণয়ন করলে তা পর্যালোচনা করে বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ে বলা হয়েছে, Parliamentary sovereignty may be contrasted with separation of powers, which limits the legislature’s scope often to general law-making, and judicial review, where laws passed by the legislature may be declared invalid by the Supreme Court in certain circumstances. (ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়, পৃষ্ঠা ২৬২)।
রায়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা লিখেছেন, সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে সংবিধানে। সার্বভৌম হচ্ছে শুধু জনগণ এবং সর্বময় হচ্ছে সংবিধান। বাকি সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নেহাতই সংবিধানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার মাত্র। আমাদের সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়নি। তিনি লিখেছেন: parliamentary supremacy has two meanings: one is that Parliament can make and unmake any law; another meaning is that as long as Parliament has the power to make laws regarding a subject matter, the exercise of that power cannot be challenged or reviewed by judiciary. The second meaning is more consistent with the Federal system and the practice of judicial review, as judiciary cannot review on the merits of the parliament (legislature)’s exercise of power. (ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়, পৃষ্ঠা ২৬৪)।
ওই রায়ে বিচারপতি ইমান আলী লিখেছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিনটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করা। তিন বিভাগের ক্ষমতার পৃথকীকরণ মানে হচ্ছে নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ সংবিধান বর্ণিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। সংবিধান তাদের যে ক্ষমতা দিয়েছে তার মধ্যে কাজ করতে তিনটি বিভাগই বাধ্য।
কিন্তু তারপরও সংসদীয় গণতন্ত্রে এটা মেনে নেওয়া হয় যে, কোনো সংসদ বা কোনো সরকার কোনো বিধান বা আইন করে পরবর্তী সংসদের কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। অর্থাৎ পরের সংসদ কী করতে পারবে এবং পারবে না, সেটি পূর্ববর্তী সংসদ বা আগের সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে যে সংসদ সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানও সংশোধন করতে পারেন, তারা কী করতে পারবেন আর পারবেন না, সেটি পূর্ববর্তী সরকার (নির্বাচিত/অনির্বাচিত উভয়ই) বা সংসদ ঠিক করে দিতে বা তাদের কাজের সীমারেখা ও এখতিয়ারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে কি না, সেটিই বিতর্কের জায়গা।


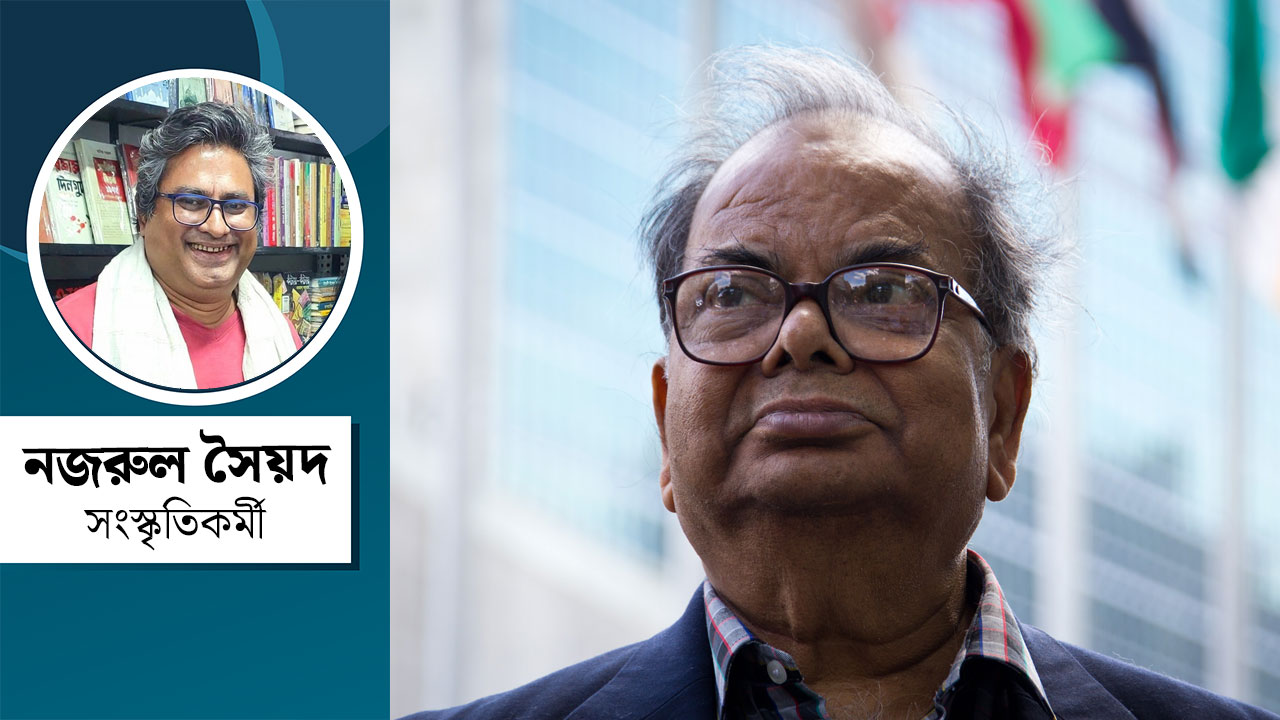
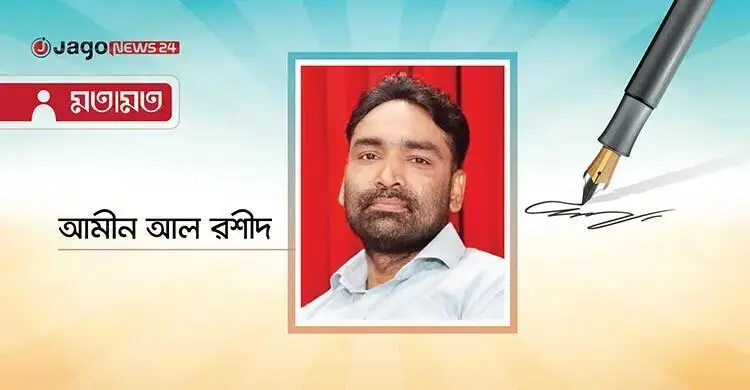

-699b8e6511dac.jpg)

