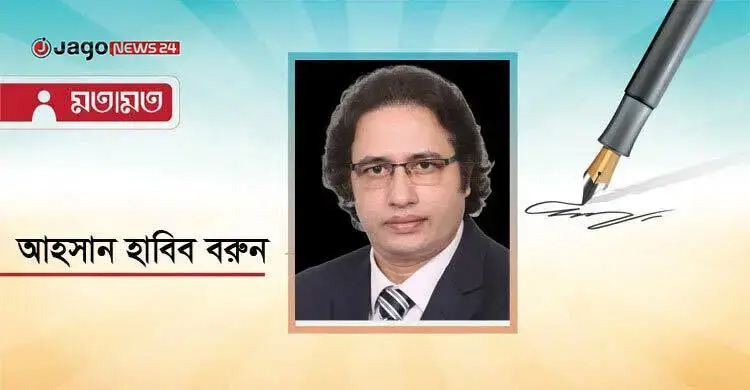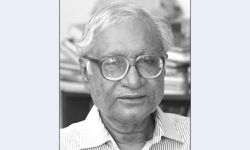মননশীলতা বনাম বাণিজ্যিক বিনোদন
একসময় উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতি (Highbrow culture) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই সংস্কৃতি অভিজাত রুচি, পরিশীলিত সংবেদনশীলতা এবং গভীর মননের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এটি কেবল ধনী বা অভিজাত শ্রেণির বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্য, ধ্রুপদী সংগীত, নাটক ও চারুকলার মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলন, প্রগতিশীল চিন্তা এবং মানবিক মূল্যবোধকে রূপ দিয়ে একটি জাতিসত্তার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।
তবে গত কয়েক দশক ধরে এই সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আজ, বাজার অর্থনীতির বাণিজ্যিকীকরণ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দ্রুত প্রসারের কারণে জনপ্রিয় সংস্কৃতি উচ্চবিত্ত ঐতিহ্যকে গ্রাস করছে। একসময়কার প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক ধারা যেমন রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্মুখী সুর, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা, জীবনানন্দের বিষণ্ন আধুনিকতা, অথবা ঢাকার মঞ্চ নাটক—এগুলো এখন ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে।
এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় কেবল একটি সাধারণ পরিবর্তন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর, বিশ্বায়নের প্রভাব এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর প্রভাব শুধু নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জাতীয় পরিচয়, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তি এবং সামাজিক সংহতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। এই অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধানে আমাদের ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশ্লেষণ করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে, পিয়েরে বোর্দিউর 'সাংস্কৃতিক মূলধন' (Cultural Capital) এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভিত্তি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শৈল্পিক সাধনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এর সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের (বেঙ্গল রেনেসাঁস) মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা সাহিত্য ও সংগীতকে সামাজিক পরিবর্তনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিলেন। এই সাংস্কৃতিক রূপগুলো সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং তা স্বাধীনতা, সামাজিক সংস্কার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে কণ্ঠস্বর দিয়েছিল।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সেসময় কবিতা, দেশাত্মবোধক গান এবং নাটক রাজনৈতিক প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক গর্বের ওপর ভিত্তি করে একটি সম্মিলিত পরিচয় গড়ে তুলেছিল। একইভাবে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গান, কবিতা এবং শিল্পকর্ম জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়েছিল। স্বাধীনতার পর, ঢাকার থিয়েটার পাড়া, কবিতা সমাবেশ এবং সংগীত সন্ধ্যাগুলো এই বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারকে সযত্নে বহন করে চলেছে।
অতএব, বাংলাদেশের উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতি কেবল অবসর বিনোদনের বিষয় ছিল না। এটি ছিল সামাজিক রূপান্তর, নাগরিক সংলাপ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক শক্তিশালী মাধ্যম। এর বর্তমান পতন শুধু একটি সাংস্কৃতিক ক্ষতিই নয়, বরং এটি সেই বুদ্ধিবৃত্তিক আঠার দুর্বলতাকেও চিহ্নিত করে, যা একসময় এই জাতিকে সংহত করে রেখেছিল।
- ট্যাগ:
- মতামত
- বিনোদন
- বাণিজ্যিক
- বাঙালির মনন