
কোন শ্রেণির মানুষ অপরাধের শিকার বেশি হয়?
অপরাধীরা ভয়ংকর ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের মনে ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। মানুষ যেকোনো পরিস্থিতিতে অপরাধে আক্রান্ত হতে পারে, এমন আশঙ্কা ও ভয়ই মূলত ভয়ের সংস্কৃতির আবহ তৈরি করে। ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদে বাসায় ফিরে আসতে পারবে এমন সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাংলাদেশে ভয়ের সংস্কৃতির ব্যাপকতা বেড়েছে এবং মানুষের অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। আবার মানুষের জীবনাচরণ ও জীবনবোধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ততার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাও প্রকট আকার ধারণ করছে। অপরাধে মানুষ সাধারণত তিন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়।
প্রথমটি হচ্ছে প্রাথমিক ক্ষতিগ্রস্ততা (Primary Victimization) যেখানে ব্যক্তি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তি কারও দ্বারা আঘাতের শিকার হয়েছে কিংবা গুরুতর আঘাতের শিকার হয়েছে।
দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাধ্যমিক ক্ষতিগ্রস্ততা (Secondary Victimization)-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কিন্তু ব্যক্তির সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেমন ব্যক্তির ঘরবাড়ি লুট, আগুনে দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি।’
তৃতীয়টি হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ততা (Tertiary Victimization)-রাষ্ট্রীয় স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি; এর প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিকেল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে সমাজের বিপুল জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানা ইত্যাদি।
অপরাধবিজ্ঞানের Lifestyle Theory of Victimization তত্ত্বটি Michael Hindelang, Michael Gottfredson, এবং James Garofalo ১৯৭৮ সালে প্রদান করেন। একজন ব্যক্তির জীবনাচরণ তার অপরাধে আক্রান্ত হওয়া তথা ক্ষতিগ্রস্ততার জন্য কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে তত্ত্বটিতে।
পরিবর্তিত দায়িত্ব ও কর্মসূচির কারণে মানুষের জীবনাচরণ ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে। জীবনাচরণের বৈচিত্রতা এবং ভিন্নতর অবস্থানের কারণে অনেকের উচ্চতর ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আবার যাদের সঙ্গে উঠাবসা, দৈনন্দিন সময় কাটানো, বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করা তাদের যাপিত জীবন পাশের জনকে প্রভাবিত করতে পারে।
লাইফস্টাইল তত্ত্বের অন্যতম একটি প্রস্তাবনা হলো: একজন ব্যক্তি লোকসমাগমে (বড় রাস্তা, পার্ক, বাজার) যত বেশি সময় ব্যয় করবে ঐ ব্যক্তির অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে। বিশেষ করে রাতের বেলা লোকজ স্থানে অধিক সময় ব্যয় করলে উক্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার মুখোমুখি হবে। বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশে অপরাধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাতের বেলা অপরাধের হার দিনের তুলনায় বেশি এবং যারা বেশিক্ষণ ঘরের বাইরে সময় কাটায় তাদের অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রাতের বেলায় অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যে বা যারা বাইরে বেশি সময় কাটায় তাদের আক্রান্ত হওয়ার অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি।
দ্বিতীয়ত: রাতে পাবলিক প্লেসে থাকার কারণে মানুষের জীবন দর্শন ও জীবনাচরণে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। যারা নিয়মিত রাতের বেলা বাইরে সময় কাটায় তাদের জীবন দর্শন স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এই ব্যতিক্রম জীবনবোধের কারণে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়ে থাকে। তাছাড়া অপরাধীরা রাতের সময় টার্গেটকে লক্ষ্য করে ভুক্তভোগীর ক্ষতিসাধন করে থাকে। কেননা গভীর রাত কিংবা ভোর রাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলেঢালা হওয়ায় অপরাধীরা সহজেই অপরাধ করে পার পেয়ে যায়।
তৃতীয়ত: সামাজিক বন্ধন ও মিথস্ক্রিয়া আনুপাতিক হারে ঘটার কারণে মানুষের অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক বন্ধনের সাথে সাথে মানুষের পারস্পারিক মেলবন্ধন একই গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সামাজিক কন্ট্রাক্টের সাথে যদি মেলবন্ধনের পার্থক্য দেখা যায় তাহলে ব্যক্তির অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সামাজিক বন্ধন হয় মূলত পারস্পারিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে। এর বিপরীতমুখী অবস্থান ব্যক্তিকে আক্রান্ত করে থাকে, সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এবং সামাজিক সাম্যবস্থার বিচ্যুতি ঘটায়।
- ট্যাগ:
- মতামত
- অপরাধমূলক কর্মকান্ড


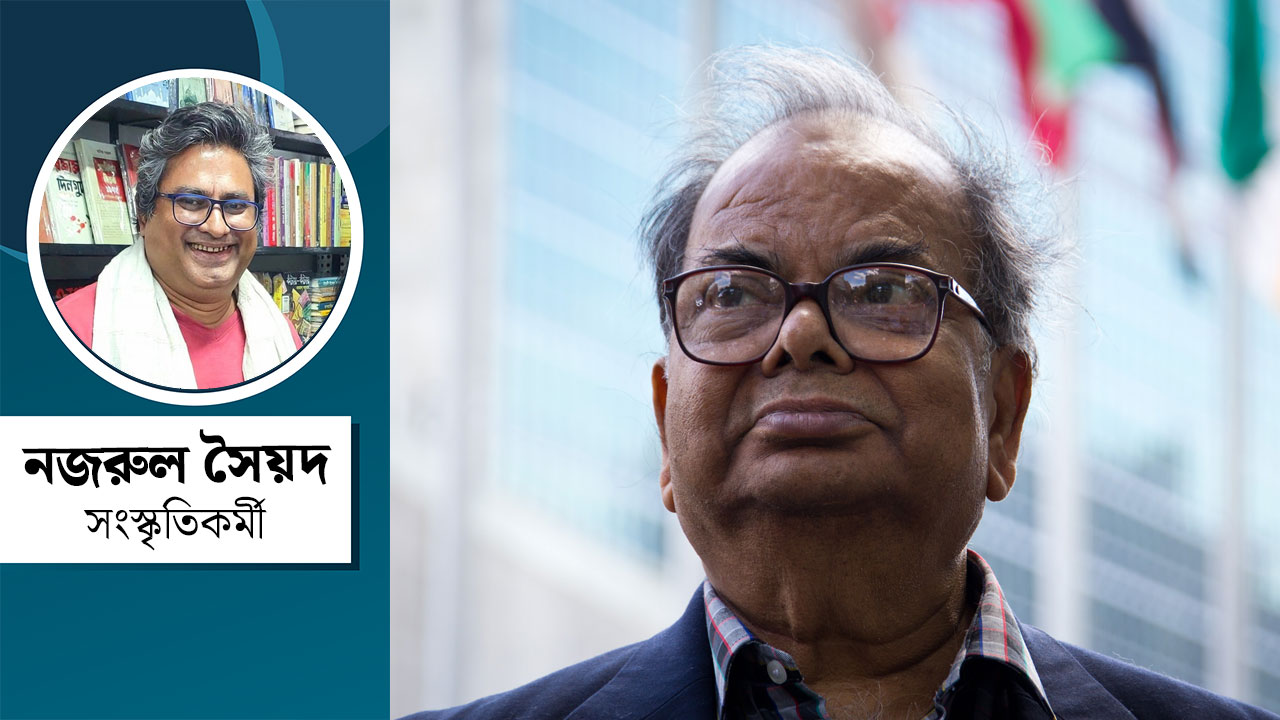
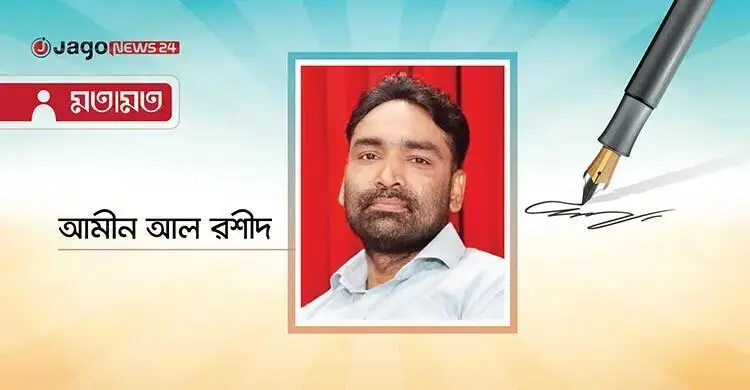

-699b8e6511dac.jpg)

