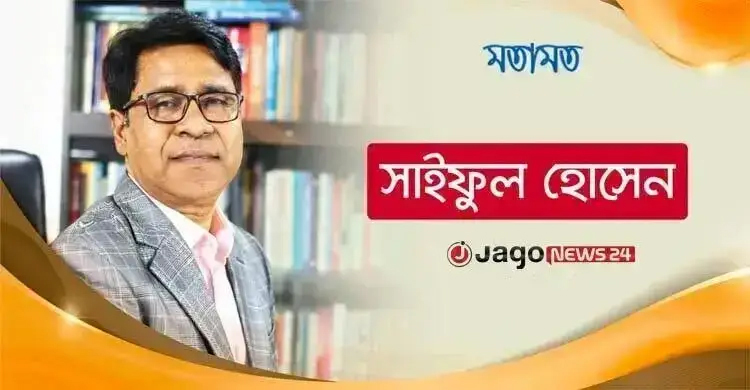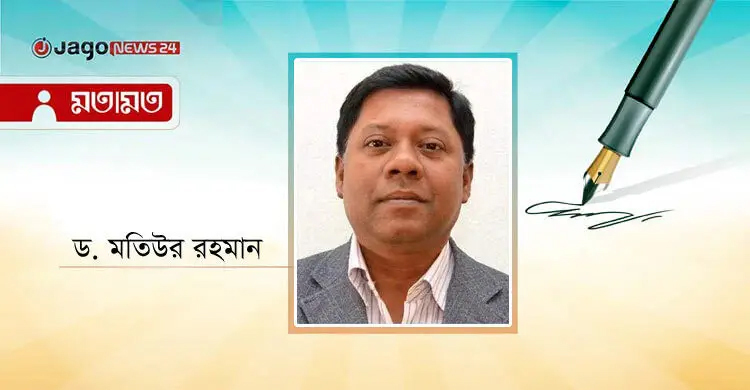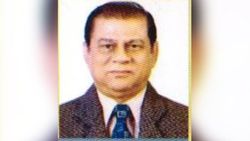মানবপাচার করিডোর: ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে দায় কার?
সীমান্তের ওপারে পৌঁছেই কারও পরিচয় হয় ‘কর্মী’, কারও ‘বস্তু’—সবাই পাচারের শিকার। ভারত–বাংলাদেশের ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ করিডোর, যেখানে নারী ও শিশুরা পাচারকারীদের প্রধান লক্ষ্য। জোরপূর্বক শ্রম থেকে বাণিজ্যিক যৌনশোষণ—এই সীমান্ত এখন অপরাধীদের জন্য একটি পথ।
ভারত এখানে উৎস, ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশ; বাংলাদেশ প্রধানত উৎস ও ট্রানজিট। সীমান্তের অনিরাপদ ভূগোল, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য এবং প্রশাসনের দুর্বলতা পাচারের জালকে দিন দিন আরও বিস্তৃত করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই অবৈধ বাণিজ্য থেকে প্রতি বছর আনুমানিক ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়—যা শুধু অর্থনৈতিক লাভ নয়, অসংখ্য মানুষের জীবনের মূল্যহ্রাসের নিষ্ঠুর চিত্র।
এই সমস্যার ঐতিহাসিক শিকড় ১৯৪৭ সালের দেশভাগে নিহিত। দেশভাগ কৃত্রিমভাবে সীমান্তরেখা তৈরি করে সীমান্ত সংলগ্ন অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে দেয়। ফলে, সরকার বা প্রশাসন সীমান্ত অতিক্রমকারীদের ‘স্বাভাবিক অভিবাসী’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি; বরং তাদের ‘অবৈধ অভিবাসী’ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় নগরীগুলোর যৌন বাজারের দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা এই বিভাজনের সঙ্গে মিলে সুসংগঠিত পাচার ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। ঊনবিংশ শতকে কলকাতায় শ্রমজীবী শ্রেণির বিস্তার এবং নগর অর্থনীতির চাহিদা এই বাজারকে আরও প্রসারিত করেছে। পুলিশ সীমান্তের সমতল ভূমি, বেড়াহীন ক্ষেত্র, গ্রামীণ পথ, কৃষিজমি ও মাছের ঘের কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা পাচারকারীদের জন্য সহজ পথ তৈরি করছে।
মানবপাচার বিষয়ক বিশ্লেষণে প্রায়শই ‘চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব’ ব্যবহৃত হয়। মূল চালিকা শক্তি হলো সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্বলতা। দারিদ্র্য ও বেকারত্বে জর্জরিত মানুষ প্রতারকদের দেওয়া ভুয়া কর্মসংস্থানের প্রলোভনে পড়ে যায়। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে, যা মানুষকে যেকোনো চাকরির প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করে। সামাজিক রোগব্যাধি এই দারিদ্র্যের প্রভাবকে আরও তীব্র করে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও লিঙ্গ বৈষম্য নারীদের ওপর নির্ভরশীলতা চাপিয়ে দেয়, ফলে তারা সহজ শিকার হয়ে পড়ে। এছাড়া, কিশোরী কুমারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্কে যৌনরোগ নিরাময়ের কুসংস্কার শিশুপাচারের চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে বিপজ্জনক অভিবাসনপথে ঠেলে দেয়।
পাচারকারীরা ক্রমাগত তাদের কৌশল পরিবর্তন করছে। ঐতিহ্যবাহী রুট এখনো সক্রিয়, যেমন যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে কলকাতাগামী পাচারের প্রায় ৫০ শতাংশ ঘটে।
তবে নতুন ধারাও দেখা দিচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, জোরপূর্বক শ্রম ও যৌনশোষণের পাশাপাশি মানুষকে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) শিল্পেও ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিও পাচারের নতুন হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ‘নীল পাখি’ নামের একটি ফেইসবুক আইডির মাধ্যমে স্কুলছাত্রীদের ভারতে নাচের প্রশিক্ষণের প্রলোভন দেখিয়ে মাসে ৫০,০০০ টাকা উপার্জনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল পাচারের ফাঁদ। সবচেয়ে ভয়াবহ বাস্তবতা হলো কক্সবাজারে অবস্থানরত রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্ব। তারা নাগরিকত্ব, মৌলিক অধিকার ও জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পাচারকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। তাদের হোটেল, শ্রমবাজার বা যৌনপল্লিতে বিক্রি করা হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের সদস্য নয়, তাই ধরা পড়া রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের আইনি সুরক্ষার পরিবর্তে প্রায়শই কারাগারে পাঠানো হয়।
এই অপরাধের মানবিক মূল্য ভয়াবহ। অভিবাসন ও মানবপাচার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান রামরু-এর মাঠপর্যায়ের তথ্য থেকেও এ ধরনের বহু ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য উঠে এসেছে। যেমন, ফারজানা নামে এক তরুণী সম্মানজনক চাকরির প্রলোভনে দিল্লিতে পাচার হন, কিন্তু অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে কলকাতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। চট্টগ্রামের সাবিনা গৃহকর্ম থেকে পশ্চিমবঙ্গের যৌনপল্লিতে বিক্রি হয়ে পাঁচ বছর বাধ্যতামূলক যৌনশ্রমে আবদ্ধ ছিলেন। রিমঝিম তার প্রেমিকের প্রতারণায় বিক্রি হন। এমনকি এক মায়ের শিশুকে বারান্দা থেকে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যৌনশোষণ করা হয়েছিল।
এসব ঘটনা পাচারকারীদের নির্মমতার গভীরতা তুলে ধরে। উদ্ধারের পরও ভুক্তভোগীদের জীবন সহজ হয় না; পুনর্বাসন একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তবে, যশোরের এক তরুণী পুনর্বাসনের পর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে ফিরে এসে দৃঢ়তার উদাহরণ স্থাপন করেছেন।
ভারত ও বাংলাদেশ মানবপাচার প্রতিরোধে আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। ভারতের সংবিধান, দণ্ডবিধি এবং বাংলাদেশের ২০১২ সালের ‘মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন’ উল্লেখযোগ্য। ২০১৫ সালের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও মানসম্মত কার্যপদ্ধতি (এসওপি) উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও তদন্তে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা স্থাপন করেছে। কিন্তু এগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফলাফল হতাশাজনক। বিচারহীনতা এখানে বড় ব্যর্থতা। ২০২৪ সালের সরকারি তথ্যমতে, ১,২৫০টি মানবপাচার মামলা খালাস হয়েছে, কিন্তু মাত্র ৫৫ জন বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পেয়েছেন, যার মধ্যে পাঁচজনের আজীবন কারাদণ্ড। সাক্ষী সুরক্ষার অভাব এবং ভুক্তভোগীদের আদালতে উপস্থিতির খরচ বহন করতে না পারা বিচারহীনতার প্রধান কারণ।