
নব্বই–পরবর্তী বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির মূল প্রবণতা হচ্ছে, এখানে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন শিক্ষার্থীদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের ওপর বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছিল। জোর করে মিছিলে যেতে বাধ্য করা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত গেস্টরুমে নিয়ে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন ছিল নিয়মিত ঘটনা।
ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ সুপিরিয়র হয়ে উঠেছিল। সরকারি দলের ভাড়াটে বা ঠ্যাঙারে বাহিনী হয়ে তারা শিক্ষার্থীদের দমন–পীড়ন চালাক।
ক্ষমতাসীন ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এই সম্পর্ককে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সামন্ত প্রভু-ভূমিদাস সম্পর্ক দিয়ে। বিগত বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের যেভাবে ছাত্রনেতাদের কুর্নিশ করতে দেখা যেত, সেটা এ ধরনের সামাজিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত নিজেদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে আপস করেই কায়দা করে বেঁচেবর্তে থাকতে হতো।
একমাত্র সেনানিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর বাদে এই চিত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। ক্ষমতা পরিবর্তনের আগে ও পরে যাঁদের হলে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা ভালো করেই জানেন যে সরকার বদলের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কীভাবে স্লোগান বদলে যায়। মজার বিষয় হলো, সামনের সারির কিছু মুখই এখানে বদলায়। নিপীড়ন কাঠামো বদলায় না। ফলে যৌন–সন্ত্রাস থেকে শুরু করে পিটিয়ে হত্যা—সব ধরনের সহিংসতা চালু থাকে ক্যাম্পাসে।
এ বাস্তবতায় গত ৩৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব বড় আন্দোলন হয়েছে, তার সিংহভাগই ধরনের দিক থেকে নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন।
জাহাঙ্গীরনগরে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশ ঢুকে ছাত্রী নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনাসদস্য কর্তৃক ছাত্র নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জরুরি শাসনবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে আবু বকর নিহত হওয়ার ঘটনায় গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনসহ অসংখ্য আন্দোলন হয়েছে, যা ধরনের দিক থেকে ছিল নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।
এ সময়টাতে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের মঞ্চ করে তুলেছিল। দীর্ঘ ৯ বছরের সংগ্রামে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের পতনের পর দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উল্টো যাত্রাটাই দেখা যায়। ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে ছাত্রদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।
এর কারণটা স্পষ্ট। সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে নব্বই পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলো খুব পরিকল্পিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা, এ দেশের ছাত্ররা খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাবিরোধী। সে কারণেই ছাত্ররাজনীতি বারবার করে জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে।
নব্বইয়ের পরে একদিকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন দিয়ে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার, মালি, দারোয়ান নিয়োগ—সবখানেই রাজনৈতিক আনুগত্যই একমাত্র বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বদলে ভোটার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অতিনিয়ন্ত্রিত রাজনীতিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় এমন এক দম বন্ধ করা পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের ন্যূনতম সুযোগটাও নেই।
- ট্যাগ:
- মতামত
- বিশ্ববিদ্যালয়
- রাজনৈতিক দল
- ক্ষমতা দখল



-698a648f3096f.jpg)
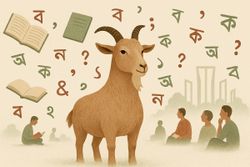

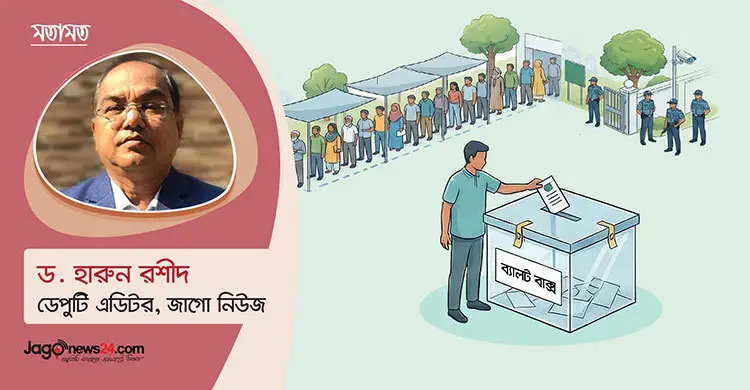

-698a65a64ca3e.jpg)
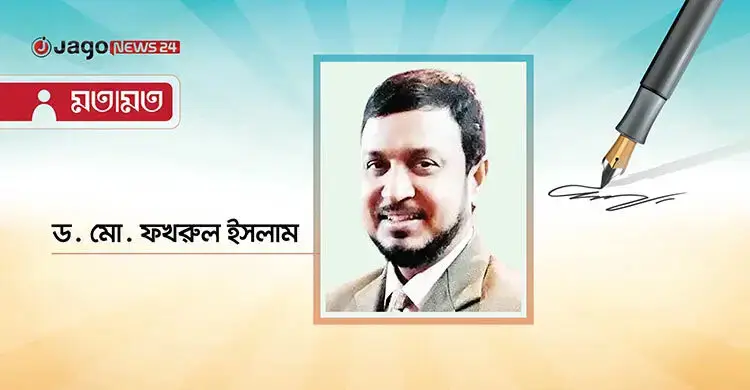
-698a65090f021.jpg)