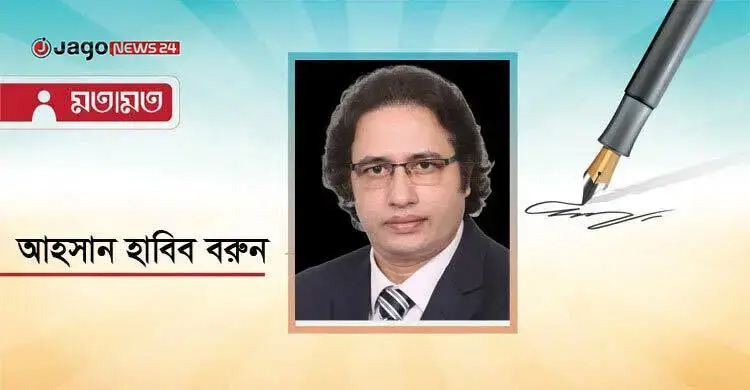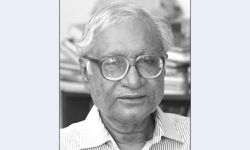বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের আকার এত বড় কেন?
জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশকে একটি স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির পথ রচনা করে দিয়েছে। মানুষ দেড় দশকের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেয়েছে। ১৬ কোটি মানুষ নতুন স্বপ্নে বিভোর। স্বপ্নটা একটি সুশাসনের বাংলাদেশের, একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার এবং সর্বোপরি একটি টেকসই অর্থনীতির। মূলত টেকসই অর্থনীতিই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে পড়লে রাষ্ট্রের কোনো তন্ত্র-মন্ত্রই আর কাজে আসে না, যার পকেটে টাকা থাকবে না সে ‘একমুঠো ভাত’র জন্য যখন চুরি কিংবা ঝাপটাবাজি করবে তখন তার অপরাধকে সে অপরাধ মনে করার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—জান বাঁচানো তখন তার জন্য ফরজ। অথবা সে বলে উঠতেই পারে, ‘ভাত দে হারামজাদা, তা-না হলে মানচিত্র খাব।’ অর্থাৎ দেশের মানুষের মৌলিক যত অধিকার দরকার, সবকিছুর ওপর অর্থনৈতিক তথা বেঁচে থাকার অধিকারটাই পায় অগ্রাধিকার।
জুলাই অভ্যুত্থানের আগের বছর ও পরের বছরের কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা যাক। রাজস্ব বছর ’২৪-এ (অভ্যুত্থানের আগের বছর) জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ, আর পরের বছর (অভ্যুত্থানের পরের বছর) তা নেমেছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে। ব্যাংকিং খাতে অভ্যুত্থানের আগের বছর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ দশমিক ১১ শতাংশ, যা পরের বছর বেড়ে হয়েছে ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য অভ্যুত্থানের আগের জুনে ছিল ১১৭ টাকা, যা পরের বছর বেড়ে হয়েছে ১২২ টাকা।
জিডিপি প্রবৃদ্ধিটা ব্যাংকিং খাতের অগ্রগতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। কারণ একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকিং খাত সুস্থ থাকলে জিডিপিতে সেটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকেই বুঝা যাচ্ছে দেশের ব্যাংকিং খাত সুস্থ নয়, তাই জিডিপি প্রবৃদ্ধিও ঋণাত্মক। ব্যাংকিং খাতের সুস্থতার ব্যারোমিটার হলো খেলাপি ঋণের পরিমাণ।
একটি দেশের সহনীয় খেলাপি ঋণের (এনপিএল) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হলো সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ। সবল আর্থিক সিস্টেমে তা সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ। আর আমাদের হলো ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। এর কারণ কী? এর অনেকগুলো কারণ। মূল কারণে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।
এটা সর্বজনবিদিত যে জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে পতিত সরকারের সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে মসজিদের ইমাম পর্যন্ত যারা সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুবিধাভোগী ছিলেন সবাই পালিয়ে গেছেন কিংবা আত্মগোপনে আছেন। তাদের মধ্যে যারা ট্রেডিং, কল-কারখানা, সেবা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকের মালিকানা এবং ব্যাংক-ঋণ সুবিধা গ্রহণের½সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের অবর্তমানে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান রাতারাতি অচল হয়ে পড়ে এবং শিল্প-কারখানাগুলো একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। একটি রফতানিমুখী কারখানার প্রধান ব্যক্তি যদি কর্মস্থলে না থাকেন ওই কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। উৎপাদন বন্ধ হলে কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে। আর ওই কারখানার মাধ্যমে প্রতি মাসে যে কয়েক লাখ ডলার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হতো তাও বন্ধ হয়ে যাবে। আয় বন্ধ হলে ওই কারখানার নামে শত কোটি টাকার যে ব্যাংক ঋণ ছিল, সে ঋণ পরিশোধ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সে ঋণ খেলাপি হয় পড়বে তিন মাসের মধ্যেই। আবার ওই কারখানার এলসির বিপরীতে ব্যাংকের ভবিষ্যৎ-পরিশোধতব্য স্বীকৃত বিল ছিল সে বিলগুলোও ব্যাংক ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে ডিউ-ডেটে পরিশোধ করতে বাধ্য। আর ফোর্সড লোন হলে তা ৩০ দিনের মধ্যে শ্রেণীকৃত হয়ে যাবে।
শত শত ব্যবসায়ী আত্মগোপনে চলে যাওয়ার কারণে একদিকে খেলাপি ঋণ হুরহুর করে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শত শত কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখ লাখ লোক বেকার হয়ে পড়েছে। আর অর্থনীতিতে পড়েছে সামগ্রিক নেতিবাচক প্রভাব। খেলাপি ঋণের লাগাম টেনে ধরা তাই অপরিহার্য। অভ্যুত্থানের কারণে হয়েছে, না কি মন্দার কারণে হয়েছে, তা-তো বিশ্ববাসী খতিয়ে দেখবে না। তারা দেখবে বাংলাদেশের অর্থনীতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। খেলাপি ঋণের প্রভাব যতটা অভ্যন্তরীণ খাতে পড়ে, তার চেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। যেমন এরই মধ্যে অনেক ব্যাংকের সঙ্গে বিদেশী ব্যাংকগুলো লেনদেন সংকুচিত করে ফেলেছে। এলসিতে অ্যাড-কনফার্মেশন না দেয়া, ডিসকাউন্টিং সুবিধা না দেয়া, এলসি অ্যাডভাইজ না করা, ডকুমেন্ট নেগোসিয়েট না করা, ডিপি এলসিতে অ্যাক্সেপ্টেন্স অ্যাডভাইজ কার্যকর না করা, গ্যারান্টি ইস্যু না করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিদেশী অনেক ব্যাংক ব্যবসা সংকুচিত করে ফেলেছে। অস্বাভাবিক খেলাপি ঋণ অভ্যন্তরীণ খাতে অনেক সূচকে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সক্ষমতা কমিয়ে দেয় বলে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ে, ব্যাংকের ঋণে ঝুঁকি বেড়ে যায়, মুনাফা কমে যায়, ব্যাংকের মুনাফা কমে যায় বলে শেয়ারহোল্ডাররা ডিভিডেন্ড থেকে বঞ্চিত হয় এবং পুঁজিবাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, গ্রাহকদের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয় বলে গ্রাহকরা আমানত তুলে ফেলে অনেকটা ব্যাংক-রানের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
শুধু তাই নয়, অর্থনীতির এ দুর্দশার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং ঋণাত্মক করে দিয়েছে, যার কারণে বিদেশী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ব্যবসা করতে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে। এছাড়া কোনো ব্যাংক যদি তার গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক এলসি ইস্যু করতে না পারে, গ্রাহক ওই ব্যাংকের ওপর আস্থা তো হারাবেই বরং তিনি সাপ্লায়ারের চাহিদা অনুযায়ী এলসি করতে না পারলে ওই গ্রাহকের ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যাবে। তার পণ্যটা যদি কারখানার কাঁচামাল হয়, তবে তো ওই কাঁচামালের অভাবে কারখানাটাই বন্ধ হয়ে যাবে—হচ্ছেও তা-ই।