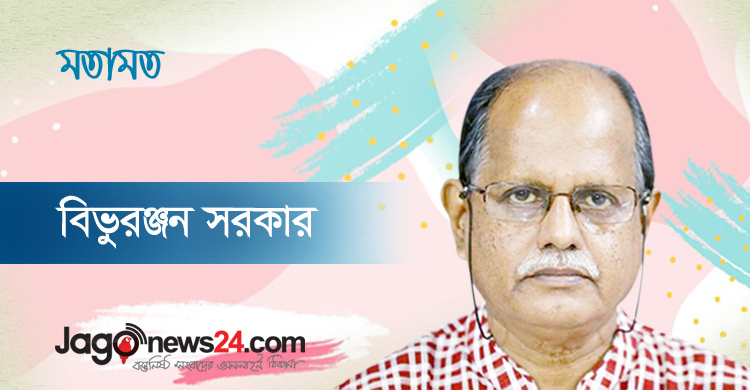
বিচারপতির বিচার : শীর্ষ এজলাস থেকে কাঠগড়ায়
একজন প্রধান বিচারপতি শুধু একটি আদালতের নন, তিনি একটি রাষ্ট্রের ন্যায়ের প্রতীক। কিন্তু সেই বিচারপতির রায়ই যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যদি তার সিদ্ধান্তই বিভাজন তৈরি করে রাষ্ট্রের ভেতরে, যদি তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন রাজনৈতিক নাটকের চরিত্র—তাহলে বিচারালয়ের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? এ প্রশ্ন আজ ঘুরেফিরে আসছে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের গ্রেফতারের পরে। এক সময় যিনি বসতেন সুপ্রিম কোর্টের শীর্ষ এজলাসে, আজ তিনি আলোচনা, সমালোচনা, এমনকি নিন্দার কেন্দ্রবিন্দুতে। গ্রেফতারবরণ করে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে কাঠগড়ায়। এটা এক বিরল ঘটনা। বাংলাদেশে আগে কখনো কোনো প্রধান বিচারপতি গ্রেফতার হননি। প্রশ্ন উঠছে, খায়রুল হকের আগে-পরে কোনো প্রধান বিচারপতি কি কোনো বিতর্কিত রায় দেননি?
বিএনপি, জামায়াতে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামসহ একাধিক রাজনৈতিক শক্তি খায়রুল হকের গ্রেফতারকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা এটিকে দেরিতে হলেও বিচারিক প্রক্রিয়ার বিজয় হিসেবে দেখছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘তিনি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন,’ আর জামায়াত আমির শফিকুর রহমান লিখেছেন—‘তিনি গুম-খুন-লুণ্ঠনের লাইসেন্স দিয়েছেন।’ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেছেন, ‘তার কারণে হাজারো মায়ের কোল খালি হয়েছে।’
অন্যদিকে, নিরপেক্ষ বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলছেন—খায়রুল হকের গ্রেফতার প্রক্রিয়া কতটা ন্যায়সংগত, আর কতটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ? তাকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো কি ঠিক কাজ হয়েছে? ৮০ বছর বয়সী একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি কাউকে হত্যার সঙ্গে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে জড়িত থাকা কি বিশ্বাসযোগ্য? তার রায় যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, তাহলে তার গ্রেফতার প্রক্রিয়াও রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের বাইরে নয়।

খায়রুল হকের রায়, ভূমিকা ও পরিণতি প্রশ্ন তুলেছে—বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচারপতিদের দায়বদ্ধতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাব নিয়ে। একজন প্রধান বিচারপতি যদি ষড়যন্ত্রে জড়িত হন, তবে সে দেশের বিচারব্যবস্থা কতটা বিশ্বাসযোগ্য থাকে? আবার, যদি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতে আদালত ব্যবহৃত হয়, তবে গণতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত থাকে?
এই দুই প্রশ্নের উত্তরই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ন্যায়বিচার ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন অনেক রায় রয়েছে, যা রাজনৈতিক প্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায়, যা এসেছিল প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ থেকে—তা ছিল এক যুগান্তকারী এবং একই সঙ্গে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। ২০১০ সালের ১০ মে, ১৩তম সংশোধনী বাতিলের রায় প্রদান করে আদালত জানায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং এটি ভবিষ্যতে আর কার্যকর হবে না। এই রায়ের পরপরই রাজনীতির মাঠে শুরু হয় উত্তেজনা, দ্বিধা এবং সন্দেহ। উচ্চ আদালত এমন রায় না দিলে শেখ হাসিনার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা হয়তো সহজ হতো না।
একটি সরকার ব্যবস্থার বিপরীতে রায় দেওয়া আদালতের এখতিয়ার, এ বিষয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু রায় প্রদানের পদ্ধতি, সময়চয়ন এবং ভাষা—এসবই হয়ে উঠেছিল প্রশ্নবিদ্ধ। খায়রুল হক নিজেই রায় লেখেন অবসরের পর, যেটি আইনি রীতি ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিপজ্জনক এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তিনি মাত্র নয় মাস ছিলেন প্রধান বিচারপতি। অবসরের পরে সম্পূর্ণ রায় লিখে তা প্রকাশ করেন। এই রায়ের একটি অংশে বলা হয়, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করে এবং এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিকৃতি।’ এই বক্তব্য শুধু একটি আইনগত ব্যাখ্যা নয়, বরং একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনও বটে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- বিচারপতি
- বিচার ব্যবস্থা







