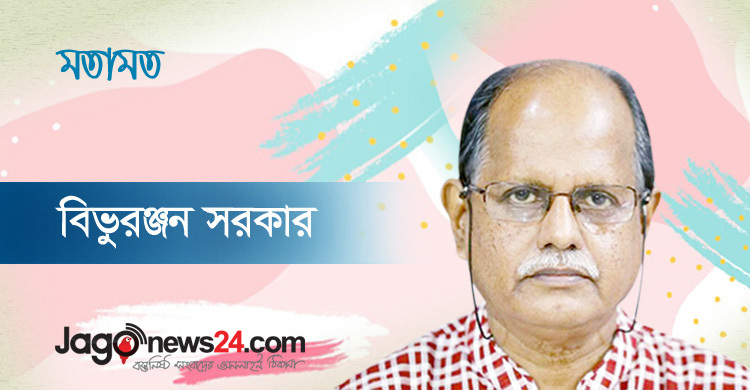
ড. ইউনূসের তিন শূন্য তত্ত্ব ও বাস্তবতা
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ক্ষুদ্রঋণের সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস আর জাতিসংঘের মিলনায়তনে নোবেল পদকের গর্বিত মুহূর্ত ভেসে ওঠে; একই সঙ্গে ভেসে ওঠে বিতর্ক, দোলাচল, প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহের টুকরো ছায়া। ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য আর ব্যর্থতার কাহিনি লতাপাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র গ্রামে—কিছু জায়গায় তা স্বনিযুক্তির আলো জ্বেলেছে, আবার কোথাও মানুষকে ফেলে দিয়েছে ঋণের দুষ্টচক্রে।
আজ, যখন তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মঞ্চে, তাঁর নতুন স্বপ্ন ‘থ্রি জিরো’—দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নির্গমনকে শূন্যে নামিয়ে আনা—দেশের নীতি ও আন্তর্জাতিক আলোচনামঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু এই বিপুল আকাঙ্ক্ষার অভীষ্টে পৌঁছাতে গেলে প্রশ্নগুলোও সমান জোরে ধাক্কা দেয়: এটা কি উদার মানবিকতার বাস্তব নকশা, নাকি এক ধরনের মধুর ইউটোপিয়া, যার নেপথ্যে রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা আর বৈশ্বিক ইমেজ পলিশের কৌশল লুকিয়ে আছে?
দারিদ্র্য শূন্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে সেই আশ্চর্য পরিসংখ্যান—বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ১৯৯০ থেকে ২০১৯ মাঝে চরম দারিদ্র্যের হার ৩৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ শতাংশে, যার পেছনে চীনের শিল্পায়ন ও দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমবাজার ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু একই গ্রাফে দেখা যায়, বৈষম্যের ফারাকটা একই সময়ে ফেঁপেছে—ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলে ধনী-দরিদ্রের আয়ের ব্যবধান এখনো ঊর্ধ্বমুখী। ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ মডেল গ্রামীণ নারীদের হাতে সীমিত পুঁজি তুলে দিলেও ঋণের সুদহার, প্রশিক্ষণের অভাব, বাজারসুবিধার সংকট অনেক ক্ষেত্রেই লাভকে খেয়ে ফেলেছে।

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ২০১০ সালে সুদের কিস্তি শোধে ব্যর্থ হয়ে ধারাবাহিক আত্মহত্যার ঘটনা বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল: ক্ষুদ্রঋণ কি দারিদ্র্য দূর করছে, নাকি নতুন ধার- দেনার দানব সৃষ্টি করছে? বাংলাদেশেও একাধিক এনজিও মাঠপর্যায়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে চাপে ফেলেছে—পূর্বশর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে দেনার দায়ে গবাদি পশু পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সুতরাং দারিদ্র্য শূন্যের সোনালি সোপান তৈরির আগে ঋণপ্রাপ্তির পাশাপাশি ন্যায্য বাজারদর, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা—এই সমন্বিত অবকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি; নইলে ‘শূন্য’ শব্দটা পোস্টারেই চকচক করবে, বাস্তবের মাটিতে বসন্ত নয়, বরং হতাশার ধূলিঝড়ই ছড়াবে।
তারপর আসে বেকারত্ব শূন্যের প্রশ্ন, যেখানে ইউনূসের পপুলার মন্ত্র—‘সবাই উদ্যোক্তা’—শুনতে যতই অনুপ্রেরণাময় হোক, বাস্তবে তা অনেকের কাছেই গোলাপি কাচের চশমা পরে ভবিষ্যৎ দেখার শামিল। গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস-এর তথ্য বলছে, কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে অন্তত ১৭ কোটি মানুষ স্থায়ী আয়হীন, ননফরমাল খাত-নির্ভর জীবিকা খুঁজছে; এর মধ্যে অনেকে মাঝবয়সী, প্রযুক্তি-অজ্ঞ বা স্বল্পশিক্ষিত—উদ্যোক্তা হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ তাদের কাছে পেটের ভাতের শেষ মুঠোটুকু বাজি ধরা। অ্যান্ট্রেপ্রেনারশিপ পরামর্শদাতা রবার্ট রাইখ সাবধান করেছেন: ‘প্রত্যেককে উদ্যোক্তা বানানোর স্বপ্নে যে ঝুঁকি-সন্তুলন লাগে, তা নেই উন্নয়নশীল দেশের সিংহভাগ মানুষের ঝুলিতে।’
ধরা যাক, বাংলাদেশে প্রতিবছর কর্মবাজারে যুক্ত হয় প্রায় ২২ লক্ষ তরুণ; তার মধ্যে কারিগরি তথা ভোকেশনাল শিক্ষা পায় সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ। অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ যদি স্বনিযুক্তি করতে চায়, তবে শুধু ক্ষুদ্রঋণ নয়, লাগবে আধুনিক সরঞ্জাম, মার্কেট লিংকেজ, বিপণন প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল স্কিল, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম—এগুলোর কোনোটিই এখনো গণহারে সহজলভ্য নয়। উপরন্তু, প্রযুক্তিগত অটোমেশন বিপুল হারে ‘রুটিন’ কাজ হারিয়ে দিচ্ছে—২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট বলছে, জেনারেটিভ এআই অন্তত ৮ কোটি চাকরি পুনর্গঠন বা বিলুপ্তির ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে। এই বাস্তবতায় ‘বেকারত্ব শূন্য’ উচ্চারণ করতে হলে রাষ্ট্রকে কেবল তত্ত্ব প্রচার নয়, শিল্প পুনর্গঠন, উচ্চ-মূল্যভিত্তিক কৃষি, গ্রিন-টেক, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে গণ- প্রশিক্ষণ—এই সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম দাঁড় করাতে হবে; না হলে উদ্যোক্তা- স্বপ্ন হবে নদীর বালুচরের ঘর—দৃষ্টিনন্দন হলেও প্রথম জোয়ারেই বিলীন।
- ট্যাগ:
- মতামত
- ক্ষুদ্রঋণ
- জীবিকা নির্বাহ







