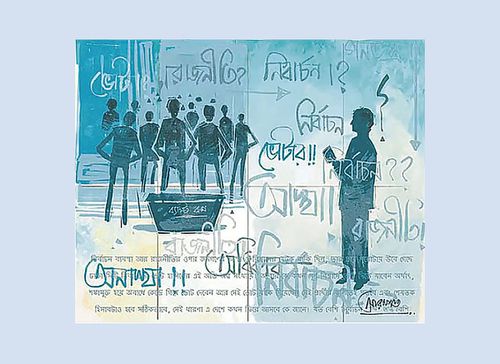
অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া ছাড়া ঐকমত্য কি টেকসই হবে
বর্তমানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের অংশীদারদের সঙ্গে একধরনের আলোচনা প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন সাংবিধানিক কাঠামো, প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক চুক্তি গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।
এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই আলোচনার পরিধি, কাঠামো ও অংশগ্রহণকারীদের বাছাই কতটা ন্যায়সংগত ও প্রতিনিধিত্বমূলক হচ্ছে?
বাংলাদেশ এখন একধরনের রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সরকার একের পর এক নির্বাচন ছিনতাই করেছে, বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করেছে, গুম-খুন চালিয়েছে।
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সরকারি বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের অনেক নেতা–কর্মী রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্র–জনতার ওপর সহিংস হামলা চালায়। যেভাবে এই হামলা চালানো হয়েছিল, তা ছিল মানবতাবিরোধী অপরাধ। গণ-অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন নয়।
এ রকম বাস্তবতার মধ্যেও আমরা যদি শুধু শাসক দলটির পতনকেই গণতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় ধরে নিই, তাহলে তা হবে একটি ‘অর্ধসত্য’। কারণ, কোনো ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা শুধু সরকার বা প্রশাসনই তৈরি করে না, তা একটি দীর্ঘমেয়াদি মানসিক কাঠামোও গড়ে তোলে।

এই কাঠামোর অংশ হয়ে যায় কিছু গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, এমনকি অনেক সাধারণ মানুষও—যারা হয়তো সরাসরি দমননীতি চালায়নি; কিন্তু চুপ থেকেছে, কিছু না দেখে থাকার ভান করেছে কিংবা নিরাপত্তা ও সুযোগের বিনিময়ে নির্যাতনকে বৈধতা দিয়েছে।
এই মানসিক কাঠামোর ভাঙন কেবল একজন শাসকের পতনেই শেষ হয় না; এটি সম্পূর্ণ হয়, যখন আমরা সাহস করে সেই মানুষদের কথাও বলি—যারা সরাসরি অন্যায় করেনি, কিন্তু চুপ থেকেছে বা নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে অন্যায় মেনে নিয়েছে।
এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কী করব? আমরা কি শুধু অপরাধীদের শাস্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব, নাকি একটি ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার কথা ভাবব?
একটি ‘সরল’ প্রশ্ন
২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন ছিল জালিয়াতি ও প্রহসনের নির্বাচন। এ কারণে এ নির্বাচনগুলোর ভোটের ফলাফল বিবেচনায় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
আমার প্রশ্ন একেবারে মৌলিক এবং সরল। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভোট পেয়েছিল। দেশের অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ভোটার একাধিকবার এই দলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।
এবার যখন একটি নতুন গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সূচনা হচ্ছে, তখন কি এই বিশাল জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অবস্থান, চিন্তা ও মতামত পুরোপুরি উপেক্ষা করা হবে—এই প্রশ্নটি হয়তো অনেকেই বিবেচনায় নিচ্ছেন না।
কেউ কেউ হয়তো ভয় পাচ্ছেন—যেন তাঁদের গায়ে ‘দোসর’ বা ‘দালাল’–জাতীয় কোনো ট্যাগ না লেগে যায়। এ এক নতুন ধরনের পরিস্থিতি, যেখানে সমালোচনার বদলে চলে প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ আর কণ্ঠ রুদ্ধ করার প্রতিযোগিতা!


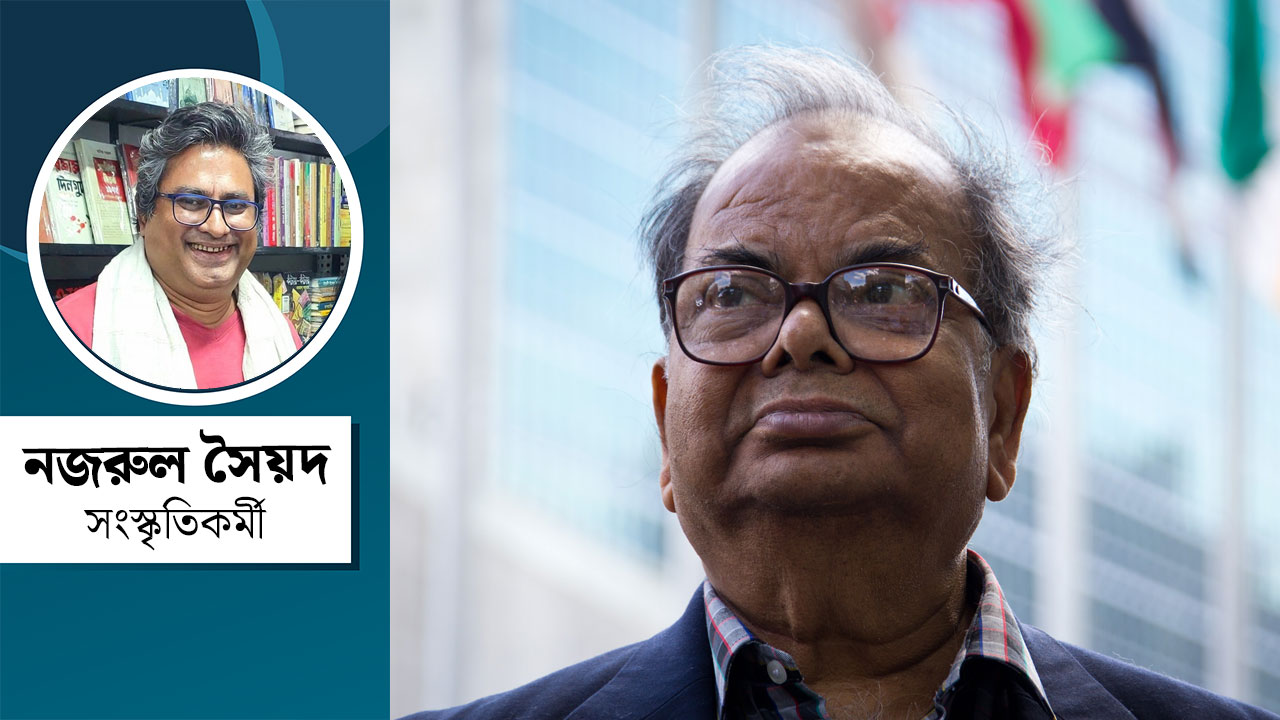
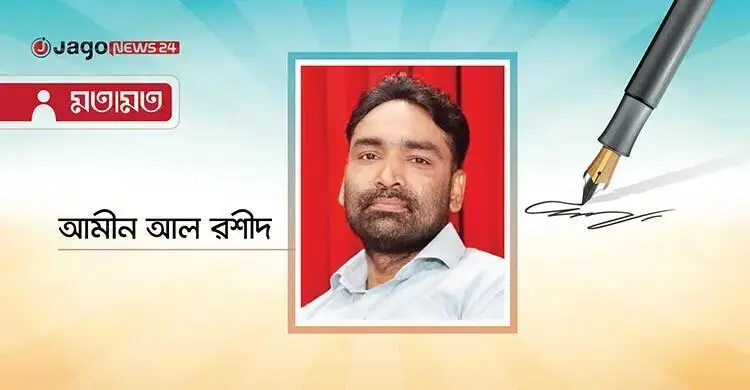

-699b8e6511dac.jpg)

