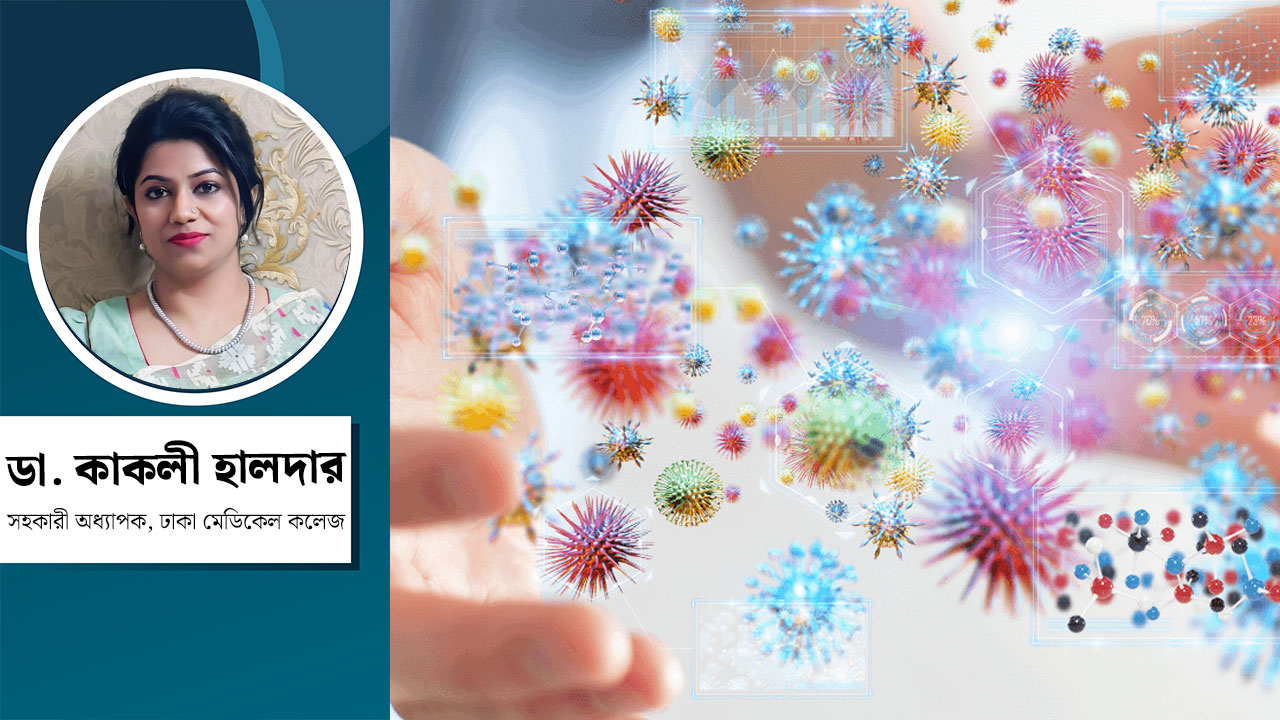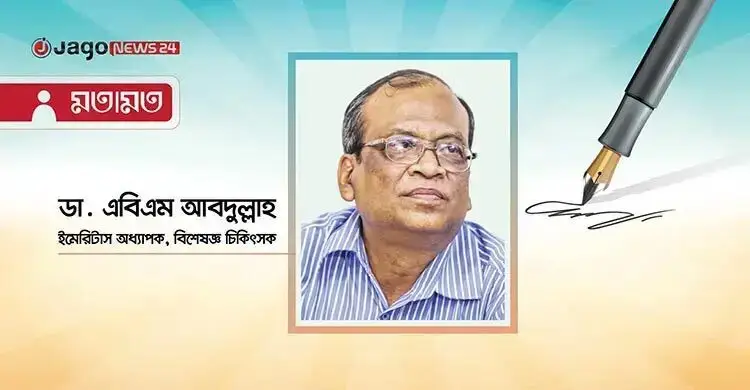গণ-অভ্যুত্থানউত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস একান্তভাবেই গণমানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন-দেশের প্রতিটি আন্দোলন ছিল ইতিহাসের একেকটি মোড় ঘোরানো ক্ষণ, যেখানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের। এ ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের ন্যায্যতা, সম্মান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন জনতার অভ্যুত্থানই হয়ে ওঠে পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রতিটি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ই সবচেয়ে সংকটময়, কারণ তখনই শুরু হয় পুরোনো কাঠামো ভাঙার এবং নতুন কাঠামো নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়া। বর্তমানের বাংলাদেশ সেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বৈরশাসনের পতনের পরও দেশে এখনো সুসংহত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর ছাপ সুস্পষ্ট নয়। এ অন্তর্বর্তী সরকারের কালপর্বে একদিকে যেমন পুরোনো শাসনযন্ত্রের ভাঙন, অন্যদিকে তেমনি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার অস্পষ্টতা-উভয়ের দ্বন্দ্বই জাতিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতি হিসাবে আমাদের প্রয়োজন গভীর আত্মবিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং ব্যাপক জনশিক্ষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।
একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি হলো একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য বিচারব্যবস্থা, যেখানে আইনের শাসন কেবল সাংবিধানিক ধারায় নয়, বরং নৈতিক ন্যায়ের বাস্তব রূপায়ণে প্রতিফলিত হয়। ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে বিচার হবে কেবল শাস্তির অনুশাসনে নয়, বরং তা হবে ন্যায়বোধ, মানবিকতা ও প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার সম্মিলন। ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আধুনিক বিশ্বের উদাহরণে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন এবং রুয়ান্ডার গ্যাকাকা আদালত, এ দুই বিশেষ উদ্যোগই ইতিহাসের ভয়াবহ সহিংসতা ও নিপীড়নের পর ন্যায় ও পুনর্মিলনের পথ উন্মোচনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছার শক্ত সাক্ষ্য। এগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ন্যায় কেবল একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরকার প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি নৈতিক ও জনগণসম্পৃক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশন কেবল একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি জনগণের আস্থা ও গণতন্ত্র চর্চার মূল স্তম্ভ। এর কার্যক্রম হতে হবে সর্বজনগ্রাহ্য, সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, যাতে কোনো ধরনের দলীয় প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ কিংবা অনিয়মের সুযোগ না থাকে। নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন, আর সে প্রক্রিয়ায় জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র রূপ নেয় একটি ফাঁপা খোলসে। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণে যেসব মডেল অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে চিলির গণভোট প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যেভাবে সেখানে একটি নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, তা আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এ উদাহরণ প্রমাণ করে, নির্বাচন তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা হয় সর্বস্তরের মানুষের আস্থাভাজন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ন্যায়ের চর্চার বহিঃপ্রকাশ।

ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে অর্থনৈতিক ইনসাফ বা ন্যায্যতা একটি অপরিহার্য ভিত্তি। এটি কেবল আয়-বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্য নয়, বরং তা সামগ্রিকভাবে সম্পদের উৎপাদন, মালিকানা ও বণ্টনে একটি ন্যায়সংগত ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিয়ে যায় একটি গভীর নৈতিক ও দার্শনিক আলোচনায়। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ‘ইনসাফ’-এর ধারণা খুব স্পষ্ট, সম্পদের ‘মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব মানবের; ভোগে নির্ধারিত সীমা অনুসরণ, বণ্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ।’ এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য হলেও তা সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কার্ল মার্কস একটি সুস্পষ্ট বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেখানে ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী’ সম্পদ বণ্টিত হবে। এটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং ন্যায্যতার একটি আদর্শিক ভিত্তি, যেখানে ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে এবং বিনিময়ে সমাজ তাদের প্রয়োজন মেটাবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতির লক্ষ্য হবে শুধু মুনাফা নয়, বরং মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায়, একদিকে অল্পকিছু মানুষের হাতে গচ্ছিত সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এ বৈষম্য কেবল একটি অর্থনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের নীতির সঙ্গে একটি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো কেবল করনীতির পুনর্বিন্যাস নয়; এটি একটি সমন্বিত জনকল্যাণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের দাবিদার, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে নাগরিকের অধিকার হিসাবে নিশ্চিত করা হয়; জনগণের প্রতি অনুগ্রহ হিসাবে নয়। এ কাঠামো গঠনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। এর জন্য জরুরি কর ব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কার, ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান, দুর্নীতির নির্মূল এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। কৃষক ও শ্রমিক, এ দুই প্রধান উৎপাদনশক্তিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
লাতিন আমেরিকার বলিভিয়া ‘বুয়েন ভিভির’ বা ‘ভালোভাবে বেঁচে থাকা’ নামক দর্শনের মাধ্যমে এক বিকল্প উন্নয়ন চিন্তার পথ দেখিয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রকৃতি, সম্প্রদায় ও আত্মমর্যাদার সহাবস্থান। এ দর্শন বলিষ্ঠভাবে প্রচলিত ভোগবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার বিপরীতে গিয়ে সামষ্টিক কল্যাণ, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে। এখানে মানুষকে প্রকৃতির শত্রু নয়, বরং সহযাত্রী ও রক্ষক হিসাবে কল্পনা করা হয়। বলিভিয়ার সংবিধানেও প্রকৃতিকে অধিকারসম্পন্ন সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের ওপর তার সংরক্ষণের নৈতিক ও আইনগত দায় আরোপ করে। এ চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক দর্শনের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামে বলা হয়, দুনিয়ায় সম্পদের ‘মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব মানবের’, অর্থাৎ মানুষ ভোগদখলের চূড়ান্ত অধিকারী নয়, বরং সে এক দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক (স্টুয়ার্ড)। তার প্রতি অর্পিত হয়েছে সম্পদের সুষম ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি নয়, বরং সমষ্টি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণকে উন্নয়নের মূল পরিমাপক হিসাবে গণ্য করে। তাই বলিভিয়ার ‘বুয়েন ভিভির’ এবং ইসলামি অর্থনীতির এ দায়বদ্ধতাভিত্তিক দর্শন আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় একটি ন্যায্যতাভিত্তিক, ইনসাফপূর্ণ বিকল্প কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- গণঅভ্যুত্থান
- সামাজিক ন্যায়বিচার