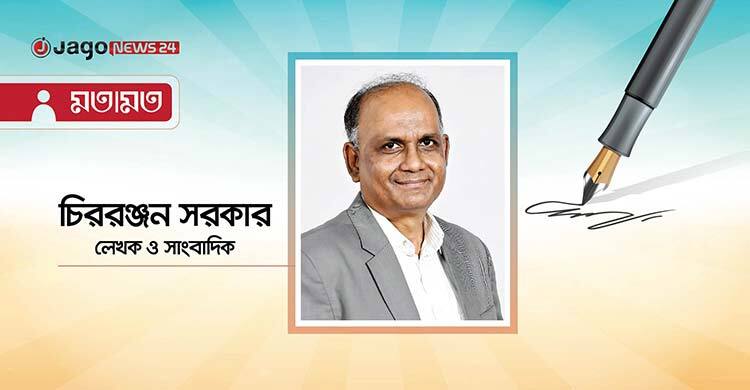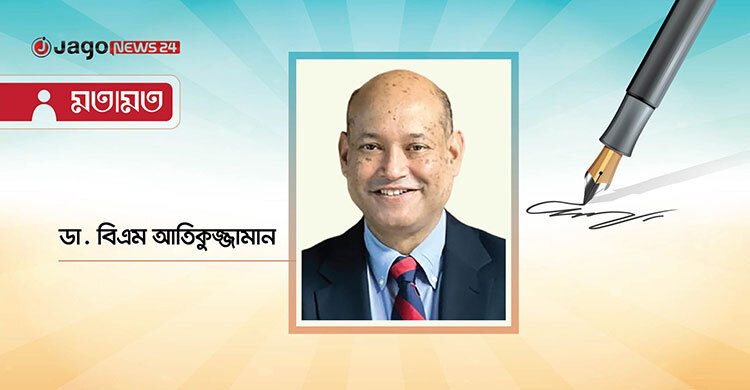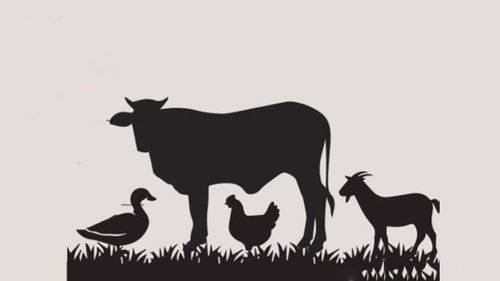
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে একটি ভিন্ন ভাবনা
বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১.৪ শতাংশ। জাতীয় জিডিপিতে এ খাতের অবদান অল্প হলেও জাতীয় শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ এ খাতে সরাসরি যুক্ত এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। তাই প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও উৎপাদনমুখী করতে পারলে জাতীয় অর্থনীতি বেগবান হবে।
প্রাণিসম্পদ খাত থেকে আমরা মূলত তিনটি প্রধান খাদ্য পেয়ে থাকি-দুধ, ডিম ও মাংস। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি দেশীয় খাত থেকে কীভাবে চাহিদার সবটুকু পূরণ করা সম্ভব। এটি দুভাবে করা যায় : ১. গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস এবং মুরগির সংখ্যা বাড়িয়ে-গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়তে থাকবে। ২. গৃহপালিত পশুপাখির মোট সংখ্যা না বাড়িয়ে প্রতিটি প্রাণীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বেশি লাভজনক ও টেকসই। কারণ, দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে; কিন্তু সেই তুলনায় কৃষিজমির পরিমাণ কমছে। তাই সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করাটা লাভজনক হবে।
ধরা যাক, প্রাপ্তবয়স্ক দেশি গরুর গড় ওজন ২০০ কেজি। আমরা চাই এ ওজন বৃদ্ধি করে ৫০০ কেজিতে উন্নীত করতে। এ উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে-জিনতত্ত্বের (জেনেটিকস) মূলনীতি প্রয়োগ করে ‘সিলেক্টিভ ব্রিডিংয়ের’ মাধ্যমে জাত উন্নয়ন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের ‘অ্যানিমেল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস’ বিভাগের গবেষকরা এ বিষয়ে নিবিড় গবেষণা করে থাকেন। সংক্ষেপে এখানে জাত উন্নয়নের একটি ধারণা দেওয়া যায়।

ধরা যাক, ময়মনসিংহ জেলায় গৃহপালিত গরুর সংখ্যা ২ লাখ এবং এদের গড় ওজন ২০০ কেজি। আমরা যদি প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি গরুর ওজন রেকর্ড করি, তাহলে দেখতে পাব, অধিকাংশ গরুর ওজন ২০০ কেজির কাছাকাছি, কিছু ২০০ কেজির বেশি আর কিছু ২০০ কেজির কম হবে। ‘কোয়ানটিটেটিভ জেনেটিকসের’ মূলনীতি অনুযায়ী, একটি গরু থেকে অন্য গরুর ওজনের ভিন্নতার একটি কারণ প্রতিটি গরুর জিনগত (জেনেটিক) গঠন।
যেহেতু গরুর দৈহিক ওজন জিনগত গঠনের কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়, এ বৈশিষ্ট্য বাবা-মা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও ছড়িয়ে যাবে। এটি একটি বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য। ‘সিলেক্টিভ ব্রিডিংয়ের’ ধারণা হচ্ছে ‘ভালো বাবা-মা’ (জেনেটিক্যালি সুপিরিওর প্যারেন্টস) নির্বাচন, যাদের গড় ওজন গরুর সমগ্র ‘পপুলেশনের’ গড় ওজন থেকে বেশি। ‘ভালো বাবা-মা’ নির্বাচন করতে পারলে পরবর্তী প্রজন্মের গড় ওজন বৃদ্ধি পাবে। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতি প্রজন্মে চলমান থাকলে ‘পপুলেশনের’ গড় ওজন ২০০ থেকে ৫০০ কেজি বা তারও অধিক বৃদ্ধি পাবে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কীভাবে ‘ভালো বাবা-মা’ নির্বাচন করতে পারি। দুটি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১০ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে ‘বাবা-মা’ নির্বাচন। অর্থাৎ যে প্রাণীর দৈহিক ওজন বেশি, তাকেই পরবর্তী প্রজন্মের ‘বাবা-মা’ নির্বাচন করা। একে বলে ‘ফেনোটাইপিক সিলেকশন’। এ পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদে ‘পপুলেশনের’ গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, কিন্তু বার্ষিক বৃদ্ধির হার কম হবে। ২. প্রতিটি প্রাণীর ‘ব্রিডিং ভ্যালু’ নির্ণয় করা এবং এ মানের ভিত্তিতে উচ্চ ব্রিডিং ভ্যালুসম্পন্ন প্রাণী নির্বাচন করা। এ পদ্ধতি অধিকতর সঠিক। এ পদ্ধতির জনক চার্লস রয় হেন্ডারসন। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রাণীর পূর্ব বংশ তথা ‘বাবা-মা’, ‘দাদা-দাদি’র তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি প্রাণীর নিজস্ব তথ্য ও তাদের পূর্ব বংশের তথ্য একসঙ্গে করে পরিসংখ্যানভিত্তিক ব্রিডিং ভ্যালু নির্ণয় করা যায়। এভাবে প্রতি প্রজন্মে ব্রিডিং ভ্যালু নির্ণয়ের মাধ্যমে ভালো ‘বাবা-মা’ নির্বাচন করা যাবে এবং যার ফলে ‘পপুলেশনের’ গড় উৎপাদন বেড়ে যাবে। তখন ‘পপুলেশনের’ সংখ্যা কম রেখেও আমরা অধিক উৎপাদনে যেতে পারব। যার ফলে কম সম্পদ ব্যবহার করে বৈশ্বিক ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ খাদ্যের চাহিদা মেটানো যাবে। ‘সিলেক্টিভ ব্রিডিংয়ের’ মাধ্যমে জাত উন্নয়ন একটি চিরস্থায়ী ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন পদ্ধতি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি
- প্রাণিসম্পদ