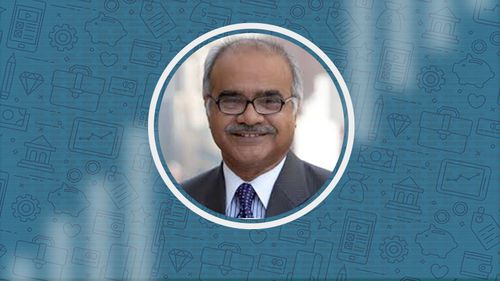
বাংলাদেশে আর্থিক খাত সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই
আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের কর্মদলটি কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই অবশেষে ঢাকা ছাড়লেন। না, বাংলাদেশকে দেয়া তাদের ঋণের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির টাকা অবমুক্তি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এ দুই কিস্তির মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি ডলার। দুই বছর আগে বাংলাদেশকে দেয় মোট ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের অংশ কিস্তি দুটি। মুদ্রাভাণ্ডারের সঙ্গে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কিস্তিতে পাওয়া গিয়েছিল ৪৮ কোটি ডলারের মতো, সে বছরেরই ডিসেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তিতে এসেছিল ৬৮ কোটি ডলার এবং ২০২৪ সালের জুনের তৃতীয় কিস্তিতে ১০১ কোটি ডলার। কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির টাকা অবমুক্তির ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার। আসলে এ অবমুক্তি অনুমোদিতও হয়নি, আবার এটাকে আটকেও দেয়া হয়নি। সত্যিকার অর্থে, পুরো ব্যাপারটি একটি অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে।
এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির অর্থ অবমুক্তি মুদ্রাভাণ্ডারের সম্প্রসারিত ঋণ সুবিধা এবং সংনম্যতা ও বজায় ক্ষমতা সুবিধার অধীনে কতগুলো প্রত্যাশিত সংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মুদ্রাভাণ্ডারের কর্মদল বলেছেন, যেহেতু আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের শর্তগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে, তাই চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির অর্থ অবমুক্তি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। আর্থিক খাতে যেসব অগ্রগতি হয়েছে তা স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে সময় বয়ে যাচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের ঋণ কিস্তি অবমুক্তি তখনই অনুমোদিত হয়, যখন প্রতিষ্ঠানটির কর্মী-সদস্য পর্যায়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়। ঋণ কিস্তি অবমুক্তিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য এ জাতীয় ঐকমত্য অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতিতে পুরো প্রক্রিয়াটিই আটকে যায়। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই কর্মী-সদস্যের মধ্যে সমঝোতা অর্জিত হয়। আশা করা হচ্ছে যে এপ্রিলে বিশ্বব্যাংক—আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের বসন্তকালীন সভার সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে। তৃতীয়ত, যেসব সংস্কার-সম্পৃক্ত বিষয় আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বাংলাদেশ সরকারের আলোচনার বিষয়বস্তু, চতুর্থত, বৈদেশিক মুদ্রাহার ব্যবস্থাপনা, কর কাঠামোর সংস্কার, ভর্তুকির যৌক্তিকতা এবং ব্যাংক খাতের সংস্কার। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা এখনো আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের শর্ত পূরণ করতে পারেনি।

বৈদেশিক মু্দ্রাহার নীতির ক্ষেত্রে বিষয়টি হচ্ছে, কী জাতীয় মুদ্রাহার কাঠামো বেছে নেয়া হবে—সম্পূর্ণ নমনীয় একটি হার নাকি উরোগামীবদ্ধ একটি হার। বাংলাদেশ উরোগামীবদ্ধ একটি হার অনুসরণ করছে এবং দুই-তিন বছর ধরেই বিষয়টি আলোচনায় আসছে বারবার। বাংলাদেশে পরিপূর্ণ নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রাহারের সপক্ষে তিনটি যুক্তি দেখানো হয়—রফতানি বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সুবিধা, বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ পুনঃপূরণ করা এবং বৈশ্বিক ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশ অর্থনীতির সংনম্যতা বাড়ানো। গত দুই বছরের ক্রমাগত হ্রাসের পর সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ স্থিতিশীল হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে সরকারি ও বেসরকারি হারের মধ্যের পার্থক্য ন্যূনতম। সুতরাং সম্পূর্ণ নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের পক্ষে দাবি জোরদার হবে।
নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রাহারের সপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি হচ্ছে যে এমন হার নিকটবর্তী সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু অন্যপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রাহার বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। বিগত দুই-তিন মাসে বাজারে শীতকালীন শাকসবজি ওঠায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতি বেশকিছুটা কমে এসেছিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য-বহির্ভূত জিনিসপত্রের দাম ছিল ক্রমাগতভাবে বাড়তির দিকে। অতিসম্প্রতি খাদ্যসামগ্রীর মূল্য আবারো বেড়ে যাচ্ছে বলে বাজারে এক ধরনের অস্বস্তি বিরাজমান। নিশ্চিতভাবে মূল্যস্ফীতি হ্রাস করার ব্যাপারে মুদ্রানীতির একটা ভূমিকা আছে এবং কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ বেশ রক্ষণশীল মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু সেটাই পর্যাপ্ত নয়। মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য কাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন।
কর কাঠামোর সংস্কার বিষয়টি বেশ দীর্ঘদিন ধরেই সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচনার বলয়ে আছে। ১০ বছর ধরে উন্নয়নশীল বিশ্বে কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত ১৫ শতাংশে স্থিত আছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট অনুপাতটি হচ্ছে ৭-৮ শতাংশের মধ্যে। এ জাতীয় অনুপাত উন্নয়ন ব্যয়সহ সামগ্রিক সরকারি ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণকে সীমিত করে দেয়। বলা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরামর্শ নির্বিশেষে বাংলাদেশকে তার কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত বাড়াতে হবে। এমনকি ভারত বা নেপালের মতো বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ দুটিতেও কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত যথাক্রমে ১২ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। বাংলাদেশে করারোপযোগ্য মানুষের মধ্যে ৬৮ শতাংশই কোনো আয়কর দেন না। মূল্য সংযোজন কর এবং আবগারি শুল্কের মতো নানা অপ্রত্যক্ষ করের ওপরই বাংলাদেশের সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া বেশি নির্ভরশীল।