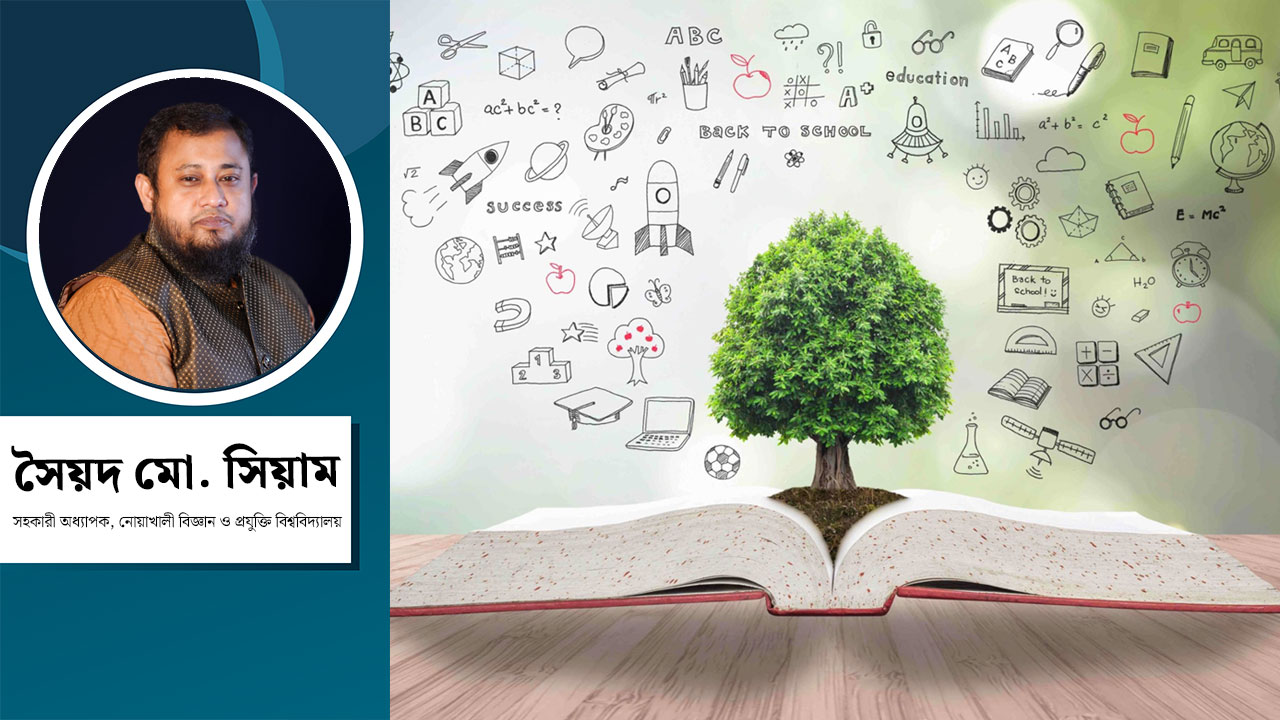কেমন আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা
পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে লিখতে বা বলতে গেলে অনেক কথা মনে পড়ে যায়। অনেকদিন আগে আমার বন্ধু, ওর বাবা বিখ্যাত সাহিত্যিক, হাসতে হাসতে একটা গল্প বলেছিল। ওর সঙ্গে ওর সহপাঠিনীর তখন চুটিয়ে প্রেম। কিছুদিন বাদে দুই বাড়িতেই জানাজানি হলো। সেরকম আপত্তি উঠল না কোনো বাড়িতেই। আমার বন্ধুর বাড়ি তো সবসময় খোলা হাওয়া। কিন্তু মেয়েটির বাড়িতেও ছেলেটির ব্যবহারে সবাই এমন মুগ্ধ যে তাকে অল্প সময়ের মধ্যেই আপন করে নিল। দিন যায়। বিয়ের দিনক্ষণ পাকা। এমন সময়ে মেয়ের মামা আড্ডা মারতে মারতে বলে বসলেন, ছেলেটিকে তো ভালোই ভাবতাম, এখন জানলাম ও মুসলমান।
বহু বছর আগের ঘটনা। এখন আমার বন্ধুর মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টি কোনোভাবে উঠলে বন্ধুটি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেও বুঝতে পারি ওর বুকের ভেতর অদৃশ্য কাঁটা খচখচ করে। ভোরবেলায় মালদা স্টেশনে নেমেছি। শীতকাল। সিনিয়র এক দাদার বাসায় যাব। আগে কখনো যাইনি। তাও ঠিকানা খুঁজে ঠিক বের করেছি। শুধু ঠিক বাড়িতেই এসেছি কি না নিশ্চিত হতে মর্নিং ওয়াকে ব্যস্ত এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি হাঁটা না থামিয়েই জানতে চাইলেন, ‘ভদ্রলোক কি মুসলমান বিয়ে করেছেন!’ সেই বিয়ের বয়স অন্তত কুড়ি বছরের বেশি। কিন্তু স্বনামখ্যাত স্কুলশিক্ষক পাড়ায় পরিচিত মুসলিম নারীর স্বামী হিসাবে। এসব না হয় পুরোনো গল্প। এ সেদিন আমার এক বন্ধুর আশি বছর বয়সি উচ্চশিক্ষিত বাবা আমাদের চেনা এক গাড়ির ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইছিলেন-তোরা কি বাসায় উর্দু বা হিন্দিতে কথা বলিস! বেচারা, ঘ্যাঁট চচ্চড়ি খাওয়া বঙ্গসন্তান ফ্যালফ্যাল করে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো ভাবছিল, উর্দু ঠিক কী রকম ভাষা!
আমাকে যদি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের মূল সমস্যা কী, আমি বলব, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে অপরিচয়ের সমস্যা। কেউ কাউকে সেভাবে চিনি না। চিনতে চাইও না। ভারতের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে বাঙালি মুসলমানের বাস গ্রামে। শহরে চাকরি করতে আসেন কেউ কেউ। ইদানীং সংখ্যা কিছু বাড়ছেও। সামান্যসংখ্যক মুসলিম হালে কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনছেন ঠিকই, তবে এর সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। এমন অনেক শহর আছে, যেখানে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া মুশকিল। কোনো কোনো এলাকায় তো মুসলমানের পক্ষে নাম-পরিচয় গোপন না করলে কাজ পাওয়া কঠিন। ফলে সল্ট লেক, লেক টাউনের মতো অভিজাত অঞ্চলে আমিনাকে সাজতে হয় মীনা, সফিকুল হয়ে যান স্বপন বা ফিরোজ হয়ে যায় রঞ্জিত।

১৯৪৭ সালের পর থেকে খোদ কলকাতা শহরের জনবিন্যাস বদলে গেছে। শুধু কলকাতা কেন, নদীয়ার দিকে গেলে জানতে পারবেন, ছোট ছোট মফস্বল শহরে এখন মুসলমানের অস্তিত্ব কম। নানা কারণে তারা গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দুর জমির ওপরই গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক নিউটাউন। কলকাতা শহরের জনবিন্যাস যে বদলে গেছে, তা আপনি হাঁটতে হাঁটতেই দেখতে পাবেন। শুধু একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। কলকাতা উত্তরে চিৎপুরে পাবেন সব থেকে প্রাচীন পাঠান স্থাপত্যের বশরি শা মসজিদ। শামবাজারে নিঃশব্দে থেকে গেছে ভাঙাচোরা এক মসজিদ। শেষ কবে সেখানে নামাজ পড়া হয়েছিল, কেউ বলতে পারবেন না। কিন্তু মসজিদ যখন আছে, আন্দাজ করা যায় একদিন সেখানে প্রাণের স্পন্দন ছিল। ছিল সংখ্যালঘু বসতি। কবে কোন রাতের অন্ধকারে তাদের পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল, তা গবেষণার বিষয়। ঢাকুরিয়া, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড সব একদিন ছিল মুসলিম জনবসতি। এখন যেতে যেতে অধিকাংশ জায়গায় চোখে পড়বে জীর্ণ মসজিদ।
১৯৪৭ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের জীবনযাপন বদলে দিয়েছে। যে এলিট ও মধ্যবিত্ত মুসলমানের দাপট ছিল কলকাতার বিস্তৃত এলাকায়, তারা দেশ ছেড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় মুসলিম সমাজে যে শূন্যতা নামে, তা আজও পূরণ হয়নি। শিল্পী, সাহিত্যিক, চাকরিজীবী, শিক্ষকরা চলে গেলেন ওপারে। মুসলিম সমাজের নিম্নবিত্ত, গরিবস্য গরিবরা রয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দেশবিভাগের দাবিতে সোচ্চার মুসলিম লীগ রাতারাতি মুছে গেল এ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসর থেকে। মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের দু-একজন, সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও একে হাসানুজ্জামান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক নেতা না থাকায় মুসলিম জনগোষ্ঠী আচমকা টের পেল তাদের পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। রাজ্যের নীতিনির্ধারণে তাদের কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। নানাভাবে তাদের কোণঠাসা করার চেষ্টা চলতে থাকল। সোহরাওয়ার্দী তখনো ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ মাত্র। ফলে মুসলিম জনগণের সামান্যসংখ্যক প্রভাবশালী অংশ মুসলিম লীগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশ হিন্দু আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ঈদ বা অন্যান্য উৎসবে তারা সংযত থাকলেন। গরু কুরবানি বা মসজিদ থেকে জোরে মাইকে আজান দেওয়া থেকেও তারা বিরত থাকলেন অশান্তি এড়াতে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- সাম্প্রদায়িক সহিংসতা


-69890d3d62cc6.jpg)