
ক্রাউড কন্ট্রোলের চেয়ে ক্রাউড ম্যানজমেন্ট শ্রেয়
বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, নার্সসহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে আন্দোলন করে চলেছেন। তাদের কিছু দাবিও রয়েছে। মাঝে মধ্যে তারা গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক, স্থান বা স্থাপনার সম্মুখে অবস্থান নেওয়ার ফলে প্রায়ই তাদের পুলিশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। একপর্যায়ে কখনো কখনো পুলিশ সদস্যরা আবেগপ্রবণ জনতার ওপর জলকামান, টিয়ার গ্যাস বা শক্তি প্রয়োগ করছে।
আবার জনতার পক্ষ থেকে পুলিশের ওপর পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিতভাবে আঘাতও করা হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি হচ্ছে, জনতা ও পুলিশ উভয়কেই কৌশলী, সহনশীল হতে হবে এবং পেশাদারত্বের সঙ্গে একত্রে কাজ ও সমঝোতা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
জনগণের সহায়তা ছাড়া অধিকাংশ পুলিশি কাজে সফলতা পাওয়া যায় না। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো কমিউনিটি পার্টনারশিপ। এখানে পার্টনারশিপ বা অংশীদারত্ব বলতে কমিউনিটি ও পুলিশ উভয়কেই সমাজের ভালো ও খারাপ দুটি দিকের সুফল ও দায় নেওয়াকে বোঝায়। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, পুলিশের বেশকিছু সদস্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে গায়েবি মামলা হচ্ছে। একজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, আবার একজন কর্মচারী বিগত ১৬ বছরের সিংহভাগ সময় ঢাকার বাইরে নন-অপারেশনাল পদে পদায়ন থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানায় দুটি এজাহার করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ নিজ দ্বন্দ্বের ঘটনায় পুলিশকে বাদী করে মামলা দিতে চাপ প্রয়োগ করছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে পেন্ডিং মামলায় ‘শ্যোন অ্যারেস্ট’ দেখাতে অনেক শক্তিশালী পক্ষ চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এগুলো মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং এর দায় সমাজকে নিতে হবে। এসব কারণে সাধারণত মামলার প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিরাজমান ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের মাধ্যমে শাস্তি হলে সেটা টেকসই হয় মর্মে বিজ্ঞজনরা মতামত প্রদান করেন।

এখন আসা যাক ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ‘লি বোন’ ক্রাউডকে পরিকল্পনা মোতাবেক ব্যবহার করা যায় উল্লেখ করে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে ‘মব সাইকোলজি’ ও ‘ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট’ নিয়ে কাজ করার সুবাদে প্রাপ্ত উপলব্ধি দিয়ে আমাদের ‘ক্রাউড ম্যানেজ’ করতে হবে। যাহোক ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের কৌশল সম্পর্কে একটু বলার চেষ্টা করছি।
সমাবেশ বা মিছিলের আগে যোগাযোগ : পুলিশ কর্মকর্তাদের অবশ্যই সমন্বয়ের মাধ্যমে, ইন্টিলিজেন্সের মাধ্যমে কারা ও কোন ধরনের ব্যক্তিরা মিছিল, র্যালি ও সমাবেশ করবে, তা আগেই জানতে হবে এবং তাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়তা ও যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
ইন্টিলিজেন্স সংগ্রহ : আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? কারণ কী? কী তার সমাধান? আন্দোলনকারীদের কি কোনো নাশকতামূলক কাজ করার পরিকল্পনা আছে, তাদের নেতা কে অথবা তারা কার কথা শোনে ইত্যাদি জানতে হবে। জনতার আন্দোলনের কারণ, তার উৎস এবং সম্ভাব্য প্রতিকারগুলো নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। জনতা শান্ত, আবেগপ্রবণ এবং অনেক সময় অত্যন্ত অশান্ত হয়ে থাকে। সেজন্য আবেগপ্রবণ জনতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলো যাচাই করতে হবে।
ঝুঁকি নিরূপণ ও গুজব প্রশমন : ইভেন্টে কী ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, তা নিরূপণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু অসাধু স্বার্থান্বেষী মহল অনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র, শ্রমিক বা অন্যদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গুজবের সৃষ্টি করে থাকে এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা করে জনতার মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সে সুযোগে কিছু খারাপ মানুষ নিরীহ মানুষকে ভুল বোঝাতে পারে এবং তাদের বিপথে পরিচালিত করতে পারে। আর প্রকৃত ঘটনা পরিষ্কার করতে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে, যা ওই পরিস্থিতির মাত্রা কমাতে বা প্রশমন করতে সহায়ক হয়ে থাকে।
পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি : আন্দোলনকারীরা কী প্রকৃতির, সংখ্যায় কতজন, কোন বয়সের, কোন উদ্দেশ্যে জমায়েত হচ্ছে ইত্যাদি জানতে হবে এবং সেগুলো গবেষণা করে খুঁজে বের করতে হবে। ইভেন্টের ঝুঁকি মোতাবেক পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করতে হবে। এছাড়া সব ফোর্স ও অফিসারকে যথাযথভাবে ব্রিফ করতে হবে। আন্দোলনকারীদের আগেই পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হবে এবং মোতায়েন করতে হবে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- নিয়ন্ত্রণ
- পরিস্থিতি
- মিছিল-সমাবেশ



-698a648f3096f.jpg)
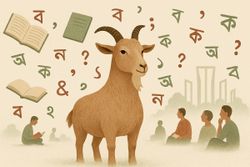

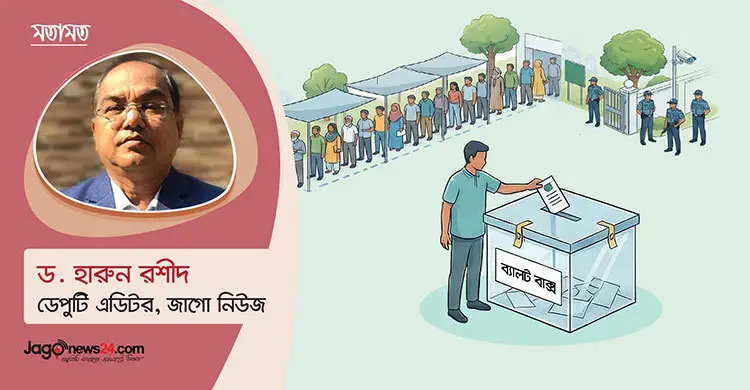

-698a65a64ca3e.jpg)
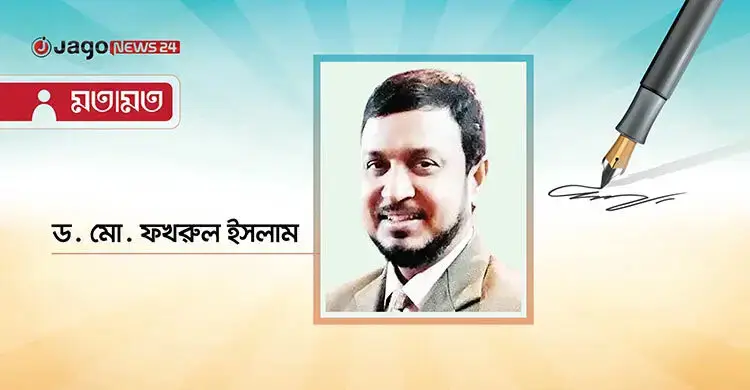
-698a65090f021.jpg)