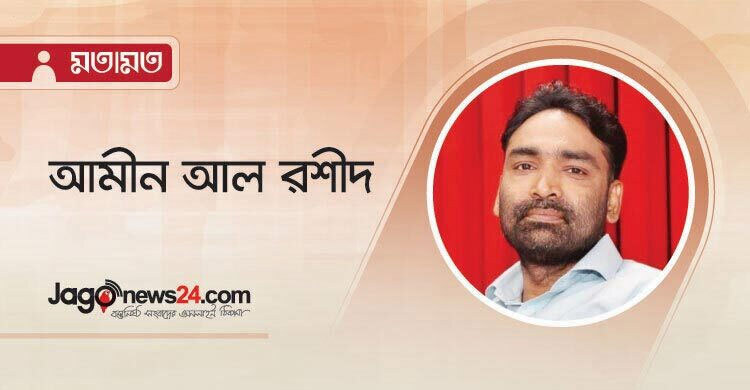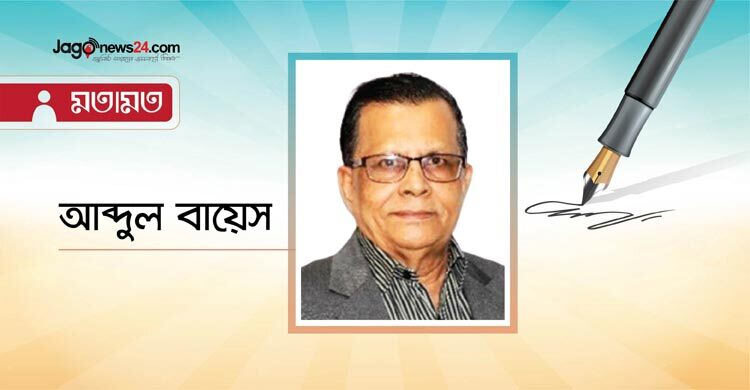দাবি মানেই কি সড়ক–রেল অবরোধ?
গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা শহরের মানুষ একটি জিম্মি অবস্থায় ছিল। তারা জিম্মি হয়ে ছিল একটি দাবির কাছে। দাবিটি হচ্ছে, একটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করে দিতে হবে। কলেজটি আর ছয়টি কলেজের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। কিন্তু জোর দাবি উঠেছিল, এই সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভুক্তি থেকে বের করে নিয়ে এসে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আনা হোক।
বাংলাদেশে আর দশটি দাবির মতো এ দাবিও মেনে হওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি ওই কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের নবতম দাবি, তাঁদের কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করে দেওয়া হোক। শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য অনশন করেছেন, কলেজের সামনের পথ ও রেললাইন অবরোধ করেছেন, যানবাহন ও ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের দাবি ন্যায়সংগত কি না, এর নৈতিক বা প্রায়োগিক কোনো আলোচনায় আমি যাচ্ছি না, আমি শুধু কয়েকটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই।
প্রথমত, দাবি আদায়ের জন্য পথ অবরোধ ও যানবাহন চলাচল বন্ধের জন্য শহরে যে যানজট সৃষ্টি হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। এমনিতেই সপ্তাহান্ত শুরু আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় বিচ্ছিরি যানজট সৃষ্টি হয়, কিন্তু ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার তা কয়েক গুণ বেশি জটিল হয়েছিল। এ পুরো যানজট ছাড়াতে অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক সময় লেগেছে। ফলে কী হয়েছে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকজনকে রাস্তায় থাকতে হয়েছে। অফিসফেরতা এবং শহরের বাইরে বাড়িমুখী মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পরে বাড়ির দরজায় টোকা দিতে পেরেছেন। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে অথবা জিনিসপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে যানবাহন থেকে নেমে দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন অনেকে। বাস-ট্রেনের যাত্রীরা তাঁদের বাস-ট্রেন ধরতে পারেননি। রিকশা ও বেবিট্যাক্সির চালকেরা এই অস্বাভাবিক যানজটে আটকে পড়ায় আয় হারিয়েছেন। আমরা কি জানি, অসুস্থ রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স শেষ পর্যন্ত সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে পেরেছিল কি না?

এক কথায়, ‘একটি দাবির প্রগলভতার’ পরিপ্রেক্ষিতে শহরের সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছিল এবং তাদের দুর্গতি ও ভোগান্তি ছিল সীমাহীন। প্রশ্ন হচ্ছে, দাবি আমাদের থাকতেই পারে, দাবি আদায়ের নানা পন্থা আমরা অনুসরণ করতে পারি, কিন্তু তার জন্য আমরা জনগণকে জিম্মি করতে পারি কি না এবং সেই সঙ্গে তাদের অশেষ দুর্গতি ও ভোগান্তির মধ্যে ফেলে দিতে পারি কি না? আমাদের দাবি আদায়ের জন্য আমরা তাদের যাপিত জীবনকে বিঘ্নিত করতে পারি কি না? এটা শুধু নৈতিকতা কিংবা অধিকারের প্রশ্ন নয়, এটা একটা প্রায়োগিক বাস্তবতার প্রশ্নও বটে।
দ্বিতীয়ত, যাঁরা দাবি আদায়ের আন্দোলন করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, তাঁদের দাবি আদায়ের কর্মকাণ্ডে জনগণকে দুর্গতি ও ভোগান্তির মধ্যে ফেলা হয়েছে। যদি তাঁরা বলেন, তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য গৃহীত পন্থার ফলে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি হবে, তা তাঁরা জানতেন। কিন্তু এতে তাঁদের কিছু যায়–আসে না; কারণ, তাঁদের কার্যসিদ্ধি হলেই হলো। আমি জানি, এমন ভাবনা তাঁদের নেই। কিন্তু যদি তা থেকে থাকে, তবে সেটা হবে নিতান্তই স্বার্থপরতা। যদি তাঁরা বলেন, তাঁদের কাজের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে, তা তাঁরা জানতেন না, তাহলে তা হবে অবিবেচনাপ্রসূত। তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করেননি, তাঁদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কিছু করতে পারবেন—এই যেমন তাঁদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা কিংবা তাঁদের দাবি পূরণ করেন। আন্দোলনকারীরা যদি মনে করে থাকেন যে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা যাবে, সে আশার যৌক্তিকতা নিতান্তই কম। কারণ, সরকারের কেউকেটারা এসব প্রক্রিয়া থেকে অনেক দূরে—পথরোধ কিংবা যানবাহন চলাচল বন্ধ তাঁদের ছুঁতে পারে না।
এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য আরও কোনো সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর কর্মপন্থা কি তাঁদের হাতে ছিল না? তাঁদের দাবির সমর্থনে তাঁরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করতে পারতেন, শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের দাবি জানাতে পারতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গেও বৈঠক করতে পারতেন। তাঁদের দাবি মেটানোর ক্ষমতা এসব ব্যক্তির আছে, সাধারণ মানুষের নেই। তাই তাঁদের দাবির সমর্থনে তাঁদের গৃহীত কর্মপন্থার কারণে জনগণের দুর্গতিই বাড়বে, আর কিছুই অর্জিত হবে না।
- ট্যাগ:
- মতামত
- সড়ক-রেলপথ অবরোধ